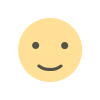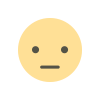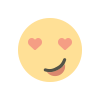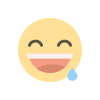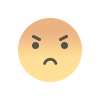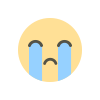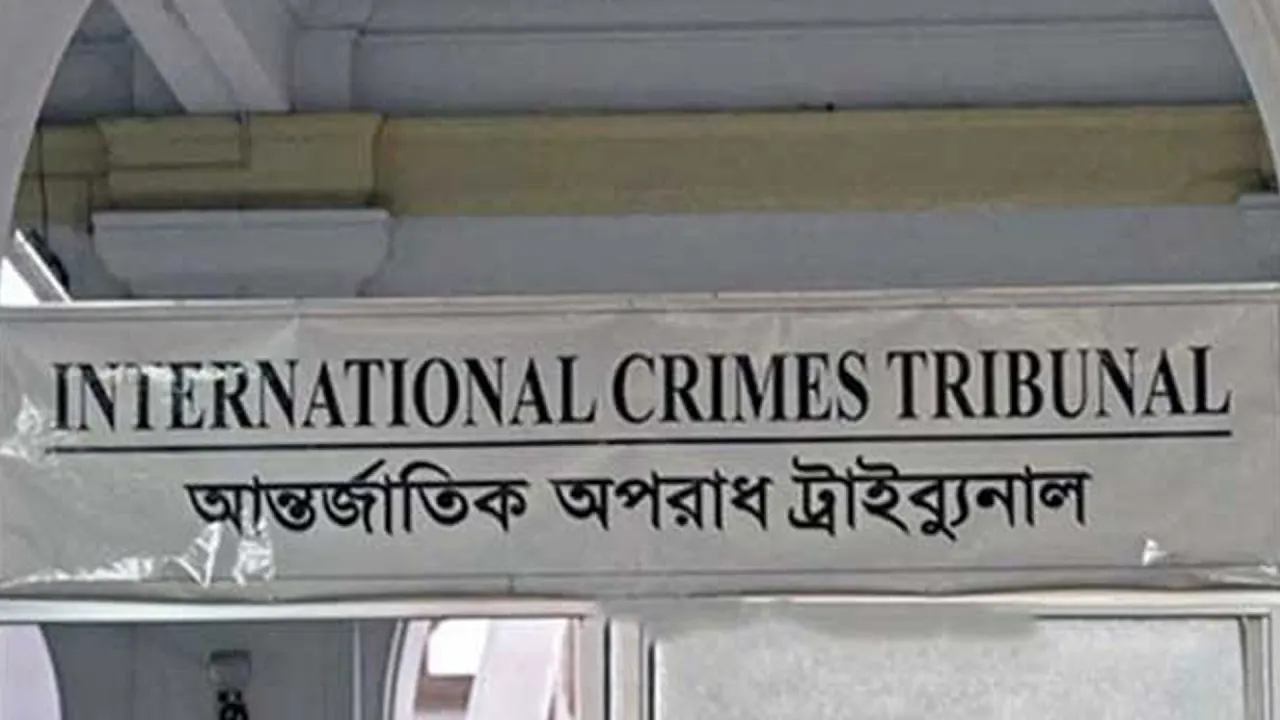চীন না আমেরিকা: কে হবে নতুন গ্রেট গেমের দাবার গুটি?
দুই শতাব্দী আগের সেই ‘গ্রেট গেম’ এর ভূরাজনৈতিক ছায়া আবারও মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে ভাসছে। ব্রিটিশ–রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেই পুরোনো লড়াই আজ নতুন রূপ পেয়েছে আমেরিকা ও চীনের সামরিক প্রতিযোগিতার ফলে। কাবুল থেকে ইয়াঙ্গুন, পামির থেকে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলজুড়ে অস্থিরতা, কৌশলগত পুনর্বিন্যাস এবং শক্তির নতুন বিন্যাস স্পষ্ট হয়ে উঠছে এখন। প্রশ্ন আজ একটাই—চীন ও আমেরিকার এই প্রতিযোগিতায় কে হবে নিয়ন্ত্রক, আর কোন দেশগুলো পরিণত হবে বড় শক্তির নতুন দাবার গুটিতে? আফগানিস্তান: নতুন গেমের পুরোনো কেন্দ্র আফগানিস্তান আজও ভূরাজনীতির সবচেয়ে সংবেদনশীল কেন্দ্র। ২০০১ সালে তালেবানকে সরিয়ে আমেরিকা নতুন এক আধিপত্যের সামরিক হস্তক্ষেপ অধ্যায় শুরু করেছিল। গত দুই দশক পর ২০২১ এ মার্কিন বাহিনীর অপমানজনকভাবে সমপর্ণ, সেই অধ্যায়ে হঠাৎ সমাপ্ত হয়। আমেরিকা রেখে যায় অস্ত্রভাণ্ডার, অর্ধসমাপ্ত শাসন কাঠামো এবং নাজুক নিরাপত্তা পরিস্থিতি। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি দখল করবে বলে দাবি জানিয়েছে। তালেবান সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, আমেরিকার পুনঃপ্রবেশের আর কোনো সুযোগ নেই। এই শূন্যতার সুযোগে চীন নরম কূটনীতি ব্যবহার করে

দুই শতাব্দী আগের সেই ‘গ্রেট গেম’ এর ভূরাজনৈতিক ছায়া আবারও মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে ভাসছে। ব্রিটিশ–রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেই পুরোনো লড়াই আজ নতুন রূপ পেয়েছে আমেরিকা ও চীনের সামরিক প্রতিযোগিতার ফলে। কাবুল থেকে ইয়াঙ্গুন, পামির থেকে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলজুড়ে অস্থিরতা, কৌশলগত পুনর্বিন্যাস এবং শক্তির নতুন বিন্যাস স্পষ্ট হয়ে উঠছে এখন। প্রশ্ন আজ একটাই—চীন ও আমেরিকার এই প্রতিযোগিতায় কে হবে নিয়ন্ত্রক, আর কোন দেশগুলো পরিণত হবে বড় শক্তির নতুন দাবার গুটিতে?
আফগানিস্তান: নতুন গেমের পুরোনো কেন্দ্র
আফগানিস্তান আজও ভূরাজনীতির সবচেয়ে সংবেদনশীল কেন্দ্র। ২০০১ সালে তালেবানকে সরিয়ে আমেরিকা নতুন এক আধিপত্যের সামরিক হস্তক্ষেপ অধ্যায় শুরু করেছিল। গত দুই দশক পর ২০২১ এ মার্কিন বাহিনীর অপমানজনকভাবে সমপর্ণ, সেই অধ্যায়ে হঠাৎ সমাপ্ত হয়। আমেরিকা রেখে যায় অস্ত্রভাণ্ডার, অর্ধসমাপ্ত শাসন কাঠামো এবং নাজুক নিরাপত্তা পরিস্থিতি। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি দখল করবে বলে দাবি জানিয়েছে। তালেবান সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, আমেরিকার পুনঃপ্রবেশের আর কোনো সুযোগ নেই।
এই শূন্যতার সুযোগে চীন নরম কূটনীতি ব্যবহার করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। আফগানিস্তানকে ব্রিকস, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য নেটওয়ার্কে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বেইজিংয়ের স্বার্থ তিনটি—নিরাপত্তা, খনিজ সম্পদ ও পশ্চিমাঞ্চলীয় বাণিজ্যের নতুন পথ। রাশিয়া রাজনৈতিক সহায়তা দিচ্ছে, ভারতও উন্নয়ন প্রকল্পে সক্রিয়। ফলে কাবুল আজ বৃহত্তর ‘পূর্ব অক্ষ’-এর মধ্যবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
ওয়াশিংটনের কাছে এই অবস্থান স্পষ্ট। আফগানিস্তান চীনের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক বলয়ে ঢুকে গেলে মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত আমেরিকার বহু–বছরের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই উদ্বেগ থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এখন আঞ্চলিক সামরিক উপস্থিতি ও গোয়েন্দা জোটকে নতুনভাবে সাজাচ্ছে।
মিয়ানমার: আরেকটি ‘গ্রেট গেম’
আফগানিস্তান যেখানে এশিয়ার পশ্চিম দরজা, ঠিক সেভাবেই মিয়ানমার পূর্ব দরজা। সেনা অভ্যুত্থানের পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় মিয়ানমারকে চীনের দিকে আরও ধাবিত করেছে। চীনের জন্য দেশটি শুধু একটি প্রতিবেশী নয়, বরং বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এর অন্যতম কৌশলগত উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কুনমিং থেকে মিয়ানমারের কিয়াখপু বন্দর পর্যন্ত চীনের রয়েছে তেল ও গ্যাসের পাইপলাইন। ‘মালাক্কা ডিলেমা’ মাধ্যমে তারা এটি সমাধানের চেষ্টা করছে। এটা ঠিক দক্ষিণ চীন সাগরের ঝুঁকিপূর্ণ জলপথ এড়িয়ে সরাসরি বঙ্গোপসাগর হয়ে জ্বালানি আনতে পারলে বেইজিং তার নিরাপত্তা ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারবে। তাই মিয়ানমারের সামরিক নেতৃত্ব যতই অজনপ্রিয় হোক, চীনের কাছে তারা অপরিহার্য। তারা এখন আরো বেশি মিয়ানমারের সামরিক উপস্থিতি কাছে পেতে চাইছে।
অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র এখন বঙ্গোপসাগর অঞ্চলকে নতুনভাবে বিবেচনা করছে। আফগানিস্তানে প্রভাব হারানোর পর ওয়াশিংটনের আগ্রহ বেড়েছে দক্ষিণ এশিয়া ও আন্দামান–নিকোবরের সামুদ্রিক ত্রিভুজের মধ্যে। মার্কিন নিরাপত্তা জোট যেমন: কোয়াড, অকাস সমুদ্রপথে চীনের প্রভাব ঠেকাতে সক্রিয়। ফলে মিয়ানমার কার্যত এক নতুন ছায়াযুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে চীনের মদদে মায়ানমারের জান্তা সমর্থন বনাম আমেরিকার আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামো সরাসরি চ্যালেঞ্জ এর মধ্যে রয়েছে।
আফগানিস্তান ও মিয়ানমার আর শুধু আঞ্চলিক সংকট নয়; তারা চীন–আমেরিকার বৈশ্বিক লড়াইয়ের পরীক্ষাগার। যে-কোনো মুহূর্তে এখান থেকেই নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি হতে পারে। নতুন গ্রেট গেমের এই প্রতিযোগিতায় বড় শক্তির লক্ষ্য স্পষ্ট তা হলো নিয়ন্ত্রণ। আর দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর বাস্তবতা আরও স্পষ্ট তা হলো তারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে টিকে থাকতে চাইলে কৌশলগত ভারসাম্যই হবে একমাত্র পথ।
ভারতের কঠিন বাস্তবতা
চীন–আমেরিকা প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে জটিল অবস্থানে রয়েছে ভারত। একদিকে ব্রিকসের সদস্য হিসেবে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার। অন্যদিকে আমেরিকার সাথে প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য সম্পর্কে ভারত–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কৌশল অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্র এখন বঙ্গোপসাগর অঞ্চলকে নতুনভাবে বিবেচনা করছে। আফগানিস্তানে প্রভাব হারানোর পর ওয়াশিংটনের আগ্রহ বেড়েছে দক্ষিণ এশিয়া ও আন্দামান–নিকোবরের সামুদ্রিক ত্রিভুজ বলয়ের মধ্যে। মার্কিন নিরাপত্তা জোট—কোয়াড, অকাস সমুদ্রপথে চীনের প্রভাব ঠেকাতে সক্রিয়। ফলে মিয়ানমার কার্যত এখন এক নতুন ছায়াযুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে চীনের জান্তা সমর্থন সরকার বনাম আমেরিকার আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামো জড়িয়ে আছে।
ভারতের কঠিন বাস্তবতা
চীন–আমেরিকা প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে জটিল অবস্থানে রয়েছে ভারত। একদিকে ব্রিকসের সদস্য হিসেবে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা। অন্যদিকে আমেরিকার সাথে প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য সম্পর্কে ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে কাছে রাখা। মিয়ানমারের সাথে ভারতের যোগাযোগ অবকাঠামো যেমন ত্রিপুরা-মনিপুরের ওপর নির্ভরশীল করছে ভারতের উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন প্রকল্পগুলো। কিন্তু চীন সমর্থিত সামরিক বাহিনী এবং পশ্চিমা সমর্থনপ্রাপ্ত বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব যত বাড়ছে, ভারতের কৌশলগত হিসাব তত জটিল হচ্ছে। দিল্লির আরেক উদ্বেগ চীনা প্রভাব বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাকিস্তান–আফগানিস্তান–চীন ত্রিভুজের সামরিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র। এটি ভারতের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তাকে নতুন করে চ্যালেঞ্জে ফেলতে পারে।
বৃহত্তর কাঠামো: নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা
২১ শতকের ভূরাজনীতির মূল গল্প হলো শক্তির পূর্বমুখী স্থানান্তর। চীন শুধু অর্থনৈতিক শক্তি নয়; একই সঙ্গে প্রযুক্তি, সামরিক শক্তি, বাণিজ্য নেটওয়ার্ক এবং জ্বালানি নিরাপত্তার মাধ্যমে বহুমাত্রিক ক্ষমতা গড়ে তুলেছে। ডলার নির্ভর আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর বিকল্প হিসেবে ইউয়ান ভিত্তিক বাণিজ্য, ব্রিকস ব্যাংক ও সুইফটের বিকল্প পেমেন্ট সিস্টেম গড়ে ওঠা আমেরিকাকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।
হেনরি কিসিঞ্জারের পর্যবেক্ষণ ছিল, আমেরিকা যখন সোভিয়েত প্রতিরোধে চীনকে উত্থানে সহায়তা করেছিল, তখন তারা ভাবেনি, এই চীনই একসময়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে। সেই আশঙ্কা আজ বাস্তব হলো। তবে চীন ও আমেরিকার প্রতিযোগিতার কেন্দ্র শুধু নিরাপত্তা নয়; এর সাথে যুক্ত জ্বালানি, প্রযুক্তি, সাইবার ক্ষমতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এবং বৈশ্বিক পরিবহন নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ। এই প্রতিযোগিতা যত বিস্তৃত হচ্ছে, ততই আফগানিস্তান ও মিয়ানমার হয়ে উঠছে দুই শক্তির পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র।
চীনের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা
চীনের অর্থনৈতিক পরিধি যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় দ্রুত বিস্তৃত হলেও তাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
– প্রথমত, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকোচন, স্থানীয় সরকারের ঋণ এবং ডেমোগ্রাফিক হ্রাস দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি তৈরি করছে।
– দ্বিতীয়ত, প্রতিরক্ষা জোটে চীন এখনো বিচ্ছিন্ন; তাদের কোনো শক্তিশালী বহুপাক্ষিক নিরাপত্তা জোট নেই।
– তৃতীয়ত, দক্ষিণ চীন সাগরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিরোধ চীনের আঞ্চলিক গ্রহণযোগ্যতাকে কমাচ্ছে।
তবুও চীন তার অর্থনৈতিক সহায়তা এবং অবকাঠামো বিনিয়োগ দিয়ে বহু উন্নয়নশীল দেশকে প্রভাববলয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও সংকট
যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশ্বব্যবস্থার মূল সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি। ন্যাটো, কোয়াড, অকাস—সবই তাদের ভূরাজনৈতিক অর্জন। তবে তাদেরও চাপ রয়েছে।
যেমন:
-দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্তি।
– অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন।
– অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা।
মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে সংঘাত। এসব মিলিয়ে আমেরিকার ‘গ্লোবাল নেতৃত্ব’ এখন চাপের মুখে।
এজন্যই যুক্তরাষ্ট্র এখন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে কৌশলগত শক্তি আরও জোরদার করছে। চীনের প্রভাব ঠেকাতে প্রযুক্তি নিষেধাজ্ঞা, সামরিক চুক্তি এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোটকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
গ্রেট গেমের পরবর্তী ধাপ: কে নিয়ন্ত্রণ করবে?
কাবুল থেকে ইয়াঙ্গুনকে ঘিরে উদীয়মান নতুন ‘গ্রেট গেম’-এ মূল লড়াই ভৌগোলিক নয়; বরং প্রভাব বলয়, বাণিজ্য পথ, জ্বালানি নিরাপত্তা, এবং প্রযুক্তিগত শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে।
এ প্রতিযোগিতার পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট:
১. চীন অর্থনৈতিক বিনিয়োগ দিয়ে অঞ্চল দখল করছে।
২. আমেরিকা সামরিক–নিরাপত্তা জোট দিয়ে প্রতিরোধ তৈরির চেষ্টা করছে।
৩. ভারত আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে দুই পক্ষের মাঝখানে সতর্ক ভারসাম্য খুঁজছে।
৪. রাশিয়া রাজনৈতিক সমর্থন ও নিরাপত্তা কাঠামো দিয়ে চীনের সহায়ক ভূমিকায়।
৫. দক্ষিণ এশিয়ার ভঙ্গুর রাষ্ট্রগুলো বড় শক্তির প্রতিযোগিতায় ক্রমশ গুটি হয়ে পড়ছে।
বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য বার্তা:
চীন ও আমেরিকা প্রতিযোগিতায় বঙ্গোপসাগর হলো নতুন কেন্দ্র। চীনের কৌশল বিনিয়োগ ও বন্দরনির্ভর প্রভাব। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল সমুদ্র নিরাপত্তা ও সামরিক অংশীদারত্ব।
বাংলাদেশের জন্য বাস্তবতা হলো:
অতিরিক্ত নির্ভরতা কোনো এক পক্ষের ওপর ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
সামুদ্রিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য পথ, এবং আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্পে ভারসাম্য রক্ষাই ভবিষ্যতে টিকে থাকার কৌশল।
বৈশ্বিক ‘পূর্ব–পশ্চিম’ প্রতিযোগিতার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার ছোট দেশগুলোকেই সবচেয়ে বেশি সাবধানী হতে হবে।
নতুন ‘গ্রেট গেম’-এ কে প্রভাবশালী শক্তি হবে তা নির্ধারিত হয় দুইভাবে। কোন দেশ এই অঞ্চলকে স্থিতিশীলতা দিতে পারে এবং কোন দেশ দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। চীনের অর্থনৈতিক শক্তি ও বিনিয়োগ তাদের এগিয়ে রাখছে। অন্যদিকে আমেরিকার সামরিক শক্তি ও বৈশ্বিক নেতৃত্ব তাদের প্রতিযোগিতায় ধরে রেখেছে। ফলে নির্দিষ্ট জয়ী বা পরাজিত এখনো নেই। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত তা হলো আফগানিস্তান ও মিয়ানমার আর শুধু আঞ্চলিক সংকট নয়; তারা চীন–আমেরিকার বৈশ্বিক লড়াইয়ের পরীক্ষাগার। যে-কোনো মুহূর্তে এখান থেকেই নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি হতে পারে। নতুন গ্রেট গেমের এই প্রতিযোগিতায় বড় শক্তির লক্ষ্য স্পষ্ট তা হলো নিয়ন্ত্রণ। আর দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর বাস্তবতা আরও স্পষ্ট তা হলো তারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে টিকে থাকতে চাইলে কৌশলগত ভারসাম্যই হবে একমাত্র পথ।
লেখক : গণমাধ্যম শিক্ষক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক।
[email protected]
এইচআর/জেআইএম
What's Your Reaction?