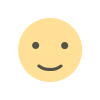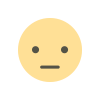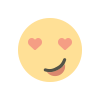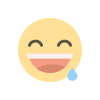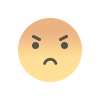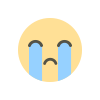দক্ষতার সংকটে আমাদের শ্রমবাজার : এখনই নজর দিন
এই মুহূর্তে বাংলাদেশের শ্রমবাজার বহুবিদ চ্যালেঞ্জের মুখে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ‘দক্ষতার সংকট’। এই দক্ষতার অভাবটিই দেশে-বিদেশে প্রকট আকার ধারণ করেছে। দেশে প্রতিবছর লাখ লাখ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এদের একটি বড় অংশই আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মক্ষেত্রে কাজের উপযোগী নয়। ফলে একদিকে বেকারত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে দক্ষ জনবলের অভাবে শিল্পকারখানায় উৎপাদনশীলতা কমছে। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ থেকে ২৫ লাখ মানুষ নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই আধুনিক শিল্প, সেবা বা প্রযুক্তি খাতে কাজে দক্ষ। সিংহভাগেরই কারিগরি দক্ষতা, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান, ভাষা ও পেশাগত আচরণের অভাব সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। জরিপ বলছে, বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ শ্রমিক অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ; তাদের মধ্যে অনেকেই কৃষি বা নিম্নআয়ের সেবা খাতে কাজ করেন। অথচ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে (বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া বা ইউরোপে) দক্ষ কর্মীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আমাদের দেশে দ্রুত বাড়ছে তৈরি পোশাক, আইটি, নির্মাণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা ও হসপিটালিটি খাতে দক্ষ
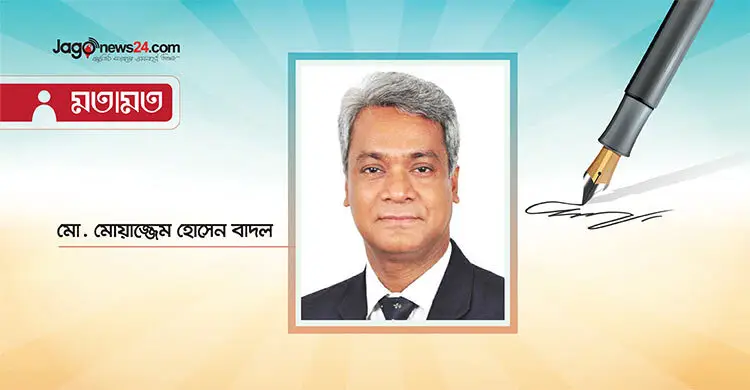
এই মুহূর্তে বাংলাদেশের শ্রমবাজার বহুবিদ চ্যালেঞ্জের মুখে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ‘দক্ষতার সংকট’। এই দক্ষতার অভাবটিই দেশে-বিদেশে প্রকট আকার ধারণ করেছে। দেশে প্রতিবছর লাখ লাখ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এদের একটি বড় অংশই আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মক্ষেত্রে কাজের উপযোগী নয়। ফলে একদিকে বেকারত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে দক্ষ জনবলের অভাবে শিল্পকারখানায় উৎপাদনশীলতা কমছে।
পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ থেকে ২৫ লাখ মানুষ নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই আধুনিক শিল্প, সেবা বা প্রযুক্তি খাতে কাজে দক্ষ। সিংহভাগেরই কারিগরি দক্ষতা, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান, ভাষা ও পেশাগত আচরণের অভাব সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। জরিপ বলছে, বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ শ্রমিক অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ; তাদের মধ্যে অনেকেই কৃষি বা নিম্নআয়ের সেবা খাতে কাজ করেন। অথচ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে (বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া বা ইউরোপে) দক্ষ কর্মীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।
আমাদের দেশে দ্রুত বাড়ছে তৈরি পোশাক, আইটি, নির্মাণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা ও হসপিটালিটি খাতে দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তা। অথচ এসব খাতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বিদেশ থেকে উচ্চ বেতনে প্রশিক্ষিত শ্রমিক এনে অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার চেষ্টা করছে- যা অর্থনীতির জন্য বড় প্রতিবন্ধকতাই বটে।
দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও শ্রমবাজারের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও বড় অংশে তাত্ত্বিক শিক্ষা দেয়; হাতে-কলমে শেখা, প্র্যাকটিক্যাল স্কিল বা ‘ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ’ প্রায় নেই বললেই চলে। যেসব শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের পর কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায়, তাদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এখনও পর্যাপ্ত নয়। দেশে প্রায় ১৫ হাজারের বেশি স্কুল ও কলেজ থাকলেও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এগুলোর অধিকাংশেই আধুনিক সরঞ্জাম, প্রশিক্ষক ও মানসম্পন্ন কোর্সের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতির কারণে, শ্রমবাজারে যে দক্ষতার চাহিদা তৈরি হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের তরুণরা প্রস্তুত নয়।
রেমিট্যান্স আয় আমাদের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। কিন্তু দুঃখজনক হলও সত্য যে, যারা বিদেশে যাচ্ছেন, তাদের ৭০ শতাংশই অদক্ষ শ্রমিক। ফলে তারা কম বেতন পান, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হন। বিদেশে প্রতিযোগিতামূলক শ্রম শিল্পে টিকতে পারেন না। অন্যদিকে, ফিলিপাইন, ভারত, ভিয়েতনাম, নেপাল বা ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো দক্ষশ্রমিক তৈরি করেন শ্রমবাজারমুখী। তারা এই দক্ষশ্রমিক বিদেশে পাঠিয়ে বেশি রেমিট্যান্স অর্জন করছে। বাংলাদেশ যদি এই দিকটি গুরুত্ব দিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাড়ায়, তবে অল্প সময়েই বিদেশে উচ্চ বেতনের কাজ পাওয়া সম্ভব হবে। এতে একদিকে আমাদের রেমিট্যান্স বাড়বে, অন্যদিকে কমবে বেকারত্ব।
আরেকটা বিষয় এখানে স্পষ্ট যে, নারীদের অংশগ্রহণও এখন এই খাতে সীমিত হয়ে যাচ্ছে। শ্রমশক্তিতে তাদের অংশ এখন মাত্র ৩৬ শতাংশের মতো। অনেক নারী গার্মেন্টস খাতে কর্মরত থাকলেও তাদের নতুন শিল্প ও সেবা খাতে প্রবেশের সুযোগ কম। তাই ডিজিটাল স্কিল, ফ্রিল্যান্সিং, হেলথকেয়ার, ফুড প্রসেসিং বা কুটির শিল্পে নারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা বাড়াতে হবে। আমি মনে করি, দক্ষ নারীশক্তি গড়ে তুলতে পারলে শুধু কর্মসংস্থানই বাড়বে না, বরং পরিবার ও সমাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে।
একবিংশ শতাব্দীতে যে দেশ তার তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক দক্ষতায় সজ্জিত করতে পারবে, সেই দেশই হবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ দেশ। বাংলাদেশের সামনে সেই সুযোগ এখন অনেকটাই উন্মুক্ত। এখন প্রয়োজন কেবল রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সমন্বিত পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী বাস্তবায়ন। যদি আমরা দক্ষতা উন্নয়নের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারি, তাহলে অদক্ষতার অভিশাপ নয়, দক্ষতার বাংলাদেশ হবে আগামীর গর্ব।
চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এখন আমাদের দেশের জন্য অতীব বাস্তব। এই বাস্তবতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, ডেটা অ্যানালিটিক্স, বন্টকচেইন, ইন্টারনেট অব থিংস- এসব প্রযুক্তি ইতোমধ্যে শিল্পখাতে কাজের ধরন পাল্টে দিচ্ছে। এই পরিবর্তনে অচিরেই অনেক পুরোনো পেশা হারিয়ে যাবে, আবার নতুন পেশার সৃষ্টি হবে। তাই ডেটা অ্যানালিস্ট, সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট, ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার, ড্রোন অপারেটর বা ই-কমার্স ম্যানেজারের মতো কাজগুলো আগামী দশকে বড় চাহিদাসম্পন্ন পেশা হবে।
সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের শ্রমবাজার আজ এক গভীর রূপান্তরের মুখে দাঁড়িয়ে। এতে একদিকে যেমন আমাদের তরুণ জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস ও অটোমেশন বিশ্ব শ্রমবাজারে নতুন বাস্তবতা তৈরি করছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের শ্রমবাজারে ‘দক্ষতার সংকট’ এখন একটি গুরুতর জাতীয় ইস্যু। বেসরকারি খাত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ না হলে, এই বিশাল জনসংখ্যাগত সম্পদই একদিন বোঝায় পরিণত হতে পারে।
আমি আগেই উল্লেখ করেছি, রেমিট্যান্সের বড় অংশ আসে শ্রমিকদের হাত ধরে। যার বেশির ভাগই অদক্ষ শ্রমিকদের ঘামঝরা পরিশ্রম থেকে। তাদের আয় কম, ঝুঁকি বেশি। অথচ বিশ্ববাজারে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ফিলিপাইন, ভারত ও ভিয়েতনামের মতো দেশগুলো তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরি নিশ্চিত করছে। বাংলাদেশ যদি এই দিকটি গুরুত্ব না দেয়, তবে ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের শ্রমিকদের টিকে থাকা কঠিন হবে। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণও এখনও সীমিত। প্রায় ৩৬ শতাংশ। গার্মেন্টস খাতের বাইরে নারীদের নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ খুবই কম। অথচ ডিজিটাল মার্কেটিং, স্বাস্থ্যসেবা, অনলাইন ব্যবসা বা ফুড প্রসেসিংয়ে নারীরা বড় ভূমিকা রাখতে পারেন, যদি তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।
মানতে হবে, বিশ্ব শ্রমবাজারে এক নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, অটোমেশন ও তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারে অনেক পুরোনো পেশা বিলুপ্ত হচ্ছে, আবার নতুন পেশা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, ডেটা অ্যানালিস্ট, ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। বাংলাদেশের তরুণদের যদি এখন থেকেই এসব দক্ষতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তবে ভবিষ্যতের শ্রমবাজারে আমরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারব।
আমার বিবেচনায় বিদ্যমান সংকট মোকাবেলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো এখনই জরুরি। তাই এই ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমশক্তি বৃদ্ধিতে যা করা যেতে পারে-
১. শিক্ষা সংস্কার: মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই কারিগরি ও স্কিলভিত্তিক কারিকুলাম চালু করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইন্ডাস্ট্রি ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক করা হোক।
২. সরকার-বেসরকারি অংশীদারিত্ব: প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে সরকার, শিল্পখাত ও এনজিওর যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা যেতে পারে।
৩. ডিজিটাল প্রশিক্ষণ: অনলাইন কোর্স, ভার্চুয়াল ক্লাস ও ইউটিউবভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা দরকার।
৪. বিদেশগামী শ্রমিকদের প্রি-ডিপারচার ট্রেনিং: ভাষা, সংস্কৃতি, আইন ও পেশাগত দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৫. নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: তাদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হোক।
৬. দক্ষতা সার্টিফিকেশন: যারা অনানুষ্ঠানিকভাবে দক্ষতা অর্জন করেছেন, তাদের জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।
আমরা মনে করি, ফিলিপাইন বা ভারতের মতো একটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করে প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রম এক ছাতার নিচে আনা যেতে পারে। পাশাপাশি ‘ন্যাশনাল লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম’ গড়ে তুলে কোন খাতে কত জনবলের চাহিদা আছে- সেই তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব। দক্ষতার অভাব কেবল অর্থনৈতিক নয়; এটি সামাজিক সংকটও। কারণ অদক্ষ তরুণ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে অনিরাপদ হলে সমাজে হতাশা, অপরাধ ও অস্থিরতা বাড়ে। বাংলাদেশের সামনে জনসংখ্যাগত সুযোগ এখনও শেষ হয়নি। যদি এখনই আমরা দক্ষতা বিপ্লবের পথে হাঁটতে পারি, তাহলে ‘অতিরিক্ত জনসংখ্যা’ নয়, ‘দক্ষ জনসম্পদ’ হবে আমাদের আসল শক্তি। সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পখাত ও সমাজ- সব পক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টায়ই এই সংকট কাটিয়ে উঠা সম্ভব। দক্ষতা উন্নয়নের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, অর্থায়ন ও পরিচালনা। সরকারের পক্ষে একা এ দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব নয়, বেসরকারি শিল্পখাত, ব্যবসায়ী সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এর সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।
আসলে শ্রমখাতে দক্ষতার সংকট কেবল শ্রমবাজারেরই সমস্যা নয়; এটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকও। একবিংশ শতাব্দীতে যে দেশ তার তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক দক্ষতায় সজ্জিত করতে পারবে, সেই দেশই হবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ দেশ। বাংলাদেশের সামনে সেই সুযোগ এখন অনেকটাই উন্মুক্ত। এখন প্রয়োজন কেবল রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সমন্বিত পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী বাস্তবায়ন। যদি আমরা দক্ষতা উন্নয়নের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারি, তাহলে অদক্ষতার অভিশাপ নয়, দক্ষতার বাংলাদেশ হবে আগামীর গর্ব। মনে রাখতে হবে, একবিংশ শতাব্দীতে প্রতিযোগিতা হচ্ছে জ্ঞানে, প্রযুক্তিতে ও দক্ষতায়। আমি মনে করি, অদক্ষতা নয়, দক্ষতাই হওয়া উচিত আমাদের আগামীর উন্নয়নের ভিত্তি। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোকে এখনই নজর দেওয়া উচিত।
লেখক : কলাম লেখক ও শিল্প-উদ্যোক্তা।
এইচআর/এমএস
What's Your Reaction?