ড. ফোরকান আলী
এ দেশের বেশিরভাগ মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। কৃষি হলো দেশের প্রাণ। ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অপরদিকে অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের পাশাপাশি ভূমিদখল, নদীভাঙন, আবাসন ও অবকাঠামো নির্মাণের কারণে প্রতিনিয়তই কৃষিজমি কমছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি হুমকির মুখে পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন। এমনিতেই খরা, বন্যা, জোয়ার-ভাটা, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও অতি শিলাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল উৎপাদনে সমস্যা হচ্ছে। এর প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙনসহ বাংলাদেশে নানা রকম প্রাকৃৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেই কৃষক জমিতে ফসল ফলানোর চেষ্টা করেন প্রতিনিয়ত। ফলে কৃষি ও কৃষকের অবস্থা দিন দিন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। দেশের বিপুল পরিমাণ জমি চলে যাচ্ছে অকৃষি খাতে। এভাবে চললে একদিন হয়তো চাষাবাদের জন্য জমি ফুরিয়ে যাবে; এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।
পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ এখনো কৃষিনির্ভর। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো নির্ধারিত হয়ে থাকে কৃষির উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর। কিন্তু দিন দিন দেশের কৃষিজমি চলে যাচ্ছে অকৃষি খাতে। নতুন বসতভিটা, রাস্তাঘাট-অবকাঠামো নির্মাণ, ইটভাটা, কলকারখানা, নগরায়ণে অধিগ্রহণেই ভূমির অবক্ষয় হচ্ছে বেশি। বর্তমান হারে ভূমি অবক্ষয় চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে কোনো কৃষিজমি থাকবে না। অপরদিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা আর অস্থিরতার মধ্যেও দেশকে অনেকটা স্বাভাবিক রাখছে কৃষি। সংগত কারণেই কৃষিজমির সুরক্ষা জরুরি। তাই জমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও নীতিমালা জরুরি। কৃষিজমি অকৃষি কাজে ব্যবহারের প্রবণতা কঠোরভাবে রুখতে হবে।
কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষিজমির সুরক্ষা ব্যর্থ হলে টিকে থাকা কঠিন হবে। দেশে কৃষিজমির পরিমাণ কমছেই। স্বাধীনতার পর থেকে কৃষিজমির পরিমাণ অর্ধেকে নেমে এসেছে। এ সময়ে জনসংখ্যা বেড়েছে আড়াই গুণেরও বেশি। ৫৪ বছর আগেও বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতির দেশগুলোর একটি। জনসংখ্যা আড়াই গুণ বেড়ে যাওয়ায় বর্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজনে ঘর-বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ব্যাপকহারে কৃষিজমি। রাস্তাঘাট, বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত তৈরিতেও কৃষিজমির ব্যবহার এড়ানো যাচ্ছে না। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্যও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষিজমি।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কৃষিশুমারিতেও নিশ্চিত করা হয়েছে কৃষিজমি কমার তথ্য। জরিপ অনুযায়ী, ১১ বছরে আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে ৪ লাখ ১৬ হাজার একর। ২০০৮ সালে আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৯০ লাখ ৯৭ হাজার একর। ২০১৯ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮৬ লাখ ৮১ হাজার একরে। মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ‘বাংলাদেশের কৃষিজমি বিলুপ্তির প্রবণতা’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে প্রতি বছর ৬৯ হাজার ৭৬০ হেক্টর আবাদি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। শুধু অবকাঠামো নির্মাণকাজের কারণে প্রতি বছর ৩ হাজার হেক্টর জমি হারিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০১০ এবং কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি জোনিং আইন-২০১০ অনুসারে কৃষিজমি কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু বিকল্প জমি না থাকায় কৃষিজমি ভরাট করে বাড়িঘর, শিল্পকারখানা, ইটভাটা বা অন্য কোনো অকৃষি স্থাপনা হচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য বিশেষত খাদ্য উৎপাদনে কৃষিজমি সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্থাপনা কলকারখানা না বানালেও চলবে না। এ সমস্যার মোকাবিলায় গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিতে হবে। কম জমিতে বহুতল ভবন গড়ে তুলে ঘরবাড়ি বানানোর জন্য কৃষিজমির যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা দরকার। সাগরপ্রান্ত থেকে জমি উদ্ধারের বিষয়েও ভাবতে হবে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশের আবাদি জমি, বনভূমি, নদী, লেক ও বনাঞ্চল সব মিলিয়ে মোট জমির পরিমাণ ১ কোটি ৪৭ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে দেশের কৃষিজমির পরিমাণ ৮৫ লাখ ২০ হাজার হেক্টর। উল্লেখ্য, ইক্যুইটি বিডির এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও নদীভাঙনের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৮৯ হাজার হেক্টর অকৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট জমির ৫০ শতাংশই চলে যাবে শুধু বসতি স্থাপনের জন্য। বিশেষ করে ১৯৬০ সালে মাত্র ১০ শতাংশ পরিবার দেশের ৩৭ শতাংশ জমির মালিক ছিল। বর্তমানে ৭০ শতাংশ পরিবার মাত্র ১৫ শতাংশ কৃষি জমির মালিক। তথাপি ১৯৬০ সালে দেশের ১৯ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন ছিল।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ২৫ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন। এ ছাড়া দেশের ২৬ শতাংশ মানুষ নিয়মিতভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার হচ্ছে। অর্থাৎ এরা বেশিরভাগ সময় ক্ষুধার্ত থাকে। বিশেষত ২০০৮ সালে খাদ্য সংকটের সময় বিদেশ থেকে খাদ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডলার থাকা সত্ত্বেও সে সময় ন্যায্যমূল্যে খাদ্য ক্রয় করা যায়নি। অর্থাৎ ভারত, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম চাল ও গমের দাম ১০০ থেকে ৩০০ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই ভবিষ্যতে ডলার থাকলেও যে বিশ্ববাজার থেকে খাদ্য ক্রয় করা সম্ভব হবে, এ নিয়ে কিন্তু বেশ সংশয় থেকেই যায়। আমরা খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নিয়ে যে গর্ব করছি; কিন্তু তা মিলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। কারণ এমনিতেই প্রতিবেশী দেশ ভারতের বৈরী পানিনীতির ফলে নদ-নদীর নাব্য কমে যাওয়া এবং উপকূলে লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে। ফলে কৃষক ঠিকমতো ফসল ফলাতে পারছেন না।
আরও পড়ুন
মানিকগঞ্জে আমনের ফলন নিয়ে দুশ্চিন্তায় চাষিরা
টাঙ্গাইলে ৫৮ কোটি টাকার হলুদ বিক্রির সম্ভাবনা
এ ছাড়া বিদ্যমান জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষিজমিতে আশানুরূপ ফসল তেমন হচ্ছে না। এ থেকে উত্তরণের জন্য অতিসত্বর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। নতুবা এ বিপুলসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে আর খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে বলে অনেকে ধারণা করছে। এর সঙ্গে বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যদিকে দেশে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাবে। ফলে কৃষিজমি হারিয়ে অনেকে ভিন্ন পেশা বেছে নিতে বাধ্য হবে। কৃষিজমি সুরক্ষা আইন না থাকায় যে যেভাবে পারছেন, জমি বিনষ্ট করে চলেছেন। এ ক্ষেত্রে ভূমি রক্ষায় রাষ্ট্রের সমন্বিত কোনো পরিকল্পনাও নেই, যদিও ২০১৭ সাল নাগাদ ভূমি জোনিংয়ের লক্ষ্য ঠিক করছিল সরকার। কিন্তু কৃষিজমির অপব্যবহার কতটা দ্রুত বন্ধ করা সম্ভব, তা নিয়ে সরকারের সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই বলে সুশীল সমাজ মনে করছে।
একসময় দেশের জমির সিংহভাগই ছিল দেশের খাদ্য জোগানের মূল উৎস। দুঃখের বিষয়, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও আবাসনের কারণে দিন দিন যে হারে জমি কমছে, তাতে কৃষিজমি সুরক্ষা করা জরুরি বলে দেশের আমজনতা মনে করছে। যোগাযোগমাধ্যমে আমরা অনেক কথা বলি যে, ভেনিস ও অন্যান্য দেশের অন্যান্য শহর অনেক সুন্দর। তবে সেখানে যে খাল-নদী রয়েছে, সেখানকার সরকার ও জনগণ মিলে সেগুলো প্রাকৃতিকভাবে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছে। আর আমরা সারাদেশের খাল ও জলাশয় ধ্বংস করছি। আগে ঢাকা শহরে জলাশয়ের সংখ্যা ছিল ৭০টি। আমাদের অপরাধের কারণে তা কমতে কমতে ২০ থেকে ২৫টিতে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দেশের কৃষিজমির পরিমাণ না বাড়িয়ে তৈরি জমি ব্যবহার করা আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড ছাড়া কিছুই নয়।
বিশ্বের অনেক দেশেই কৃষিজমি সুরক্ষিত করে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন করা হচ্ছে। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ায় খাল কেটে মরুভূমিতে ফসল ফলানো হচ্ছে। এ ছাড়া ভিয়েতনামে এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতে জমির ওপর দিয়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ করে কৃষিজমি রক্ষা করা হচ্ছে। এর বিপরীতে প্রকৃতিগতভাবে আমাদের দেশে কোনো ধরনের চাষ ছাড়াই বীজ ফেলে রাখলে সহজেই গাছ জন্মে যায়। অথচ বছরের পর বছর প্রকৃতির এ অপার দান স্বেচ্ছায় ধ্বংস করা হচ্ছে। এমন উবর্র দেশ পৃথিবীর আর কোথাও তেমন দেখা যায় না। যেখানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি উদ্বৃত্ত ফসল রপ্তানি করার অপার সুযোগ রয়েছে, সেখানে কৃষিজমি ধ্বংসের এ প্রক্রিয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
বাংলাদেশে ভূমি অনুযায়ী লোকসংখ্যা অনেক বেশি। তাই প্রতি বছর প্রায় ২৫ লাখ মানুষ বাড়লেও কৃষিজমি এক শতাংশ বাড়ছে না। বরং আয়তনের এক শতাংশ জমি কমে যাচ্ছে। তবে মাঝেমধ্যে সমুদ্রে দ্বীপ ও নদীতে চর জেগে ওঠার কথা শোনা যায়। কিন্তু সেগুলো কবে চাষযোগ্য হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। ফলে আমাদের বিদ্যমান কৃষিজমির দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। আর এসব জমি যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে সংকট যে তীব্র হয়ে উঠবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কারণে অবিলম্বে কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষি খাসজমি ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বন্দোবস্ত করতে হবে। অকৃষি খাসজমিকে কোনো ধরনের অকৃষি কাজে ব্যবহারে বন্দোবস্ত করা যাবে না। এ বিধান প্রবর্তন করে কার্যকর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অকৃষি খাসজমিকে কেবল উন্নয়ন কাজেই বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান করতে হবে; অন্যদিকে দখলদারদের গ্রাস থেকে কৃষিজমি বাঁচাতে হবে আর কৃষিজমি রক্ষায় সচেতনতার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।
বসতি স্থাপনের জন্য আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের মোট আবাদি ভূমি অর্ধেকে নেমে আসার আশঙ্কা থেকে যায়। এ ছাড়া কৃষিজমির স্বল্পতার কারণে যেমন কৃষক তুলনামূলকভাবে ফসল উৎপাদন করতে পারছেন না; অন্যদিকে টাকা বা ডলার হাতে থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়া যাবে না বলে সুশীল সমাজ আশঙ্কা করছে। অর্থাৎ বিক্রি করার মতো উদ্বৃত্ত খাদ্যই হয়তো পাওয়া যাবে না। তাই কৃষিজমি রক্ষা করে পরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন করতে হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় এক শ্রেণির অসাধু ইটভাটার মালিকরা সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে সোনা ফলানোর জমি থেকে গণহারে মাটি কাটছে প্রতিনিয়তই। এখনই যদি মাটি কাটার মতো অপকর্ম বন্ধ না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে খাদ্য সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এ ছাড়া দেশের কৃষিজমির ক্ষতি করে কতিপয় বিতর্কিত আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তি মাছের প্রজেক্ট ও রিসোর্ট তৈরি করছে। এদের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সঙ্গে সরকারকে সুনির্দিষ্ট আইন দ্রুত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে কৃষিজমি রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
দেশের অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, আবাসন ও অবকাঠামো নির্মাণের রাশ টেনে ধরতে হবে। কৃষিজমি বাঁচিয়ে পরিকল্পিতভাবে এসব কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে হবে। যে জমি থেকে মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়, সে জমি যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ দেশের যে জমিতে মানুষের খাদ্য সংস্থান হয়, সে জমি রক্ষায় সরকারকে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অনেক সভ্যতাই মানুষের হঠকারিতার শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই আমাদের শিক্ষা নেওয়ার চেতনা না জাগলে একই পরিণতি আমাদেরও বরণ করতে হবে। আবাসন চাহিদা মেটাতে বহুতল ভবন নির্মাণ করে কৃষিজমির ওপর চাপ কমানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিকল্পিত গ্রাম-নগরায়ণ ও গৃহায়ন-প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষিজমিকে রক্ষা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান গতিময় উন্নয়নশীলতার ধারায় আমাদের দরকার পরিকল্পিত গ্রাম।
লেখক: গবেষক ও সাবেক অধ্যক্ষ।
এসইউ/জেআইএম

 2 hours ago
1
2 hours ago
1


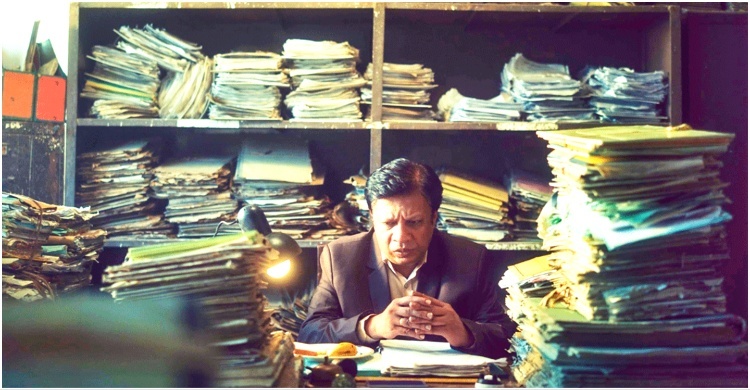





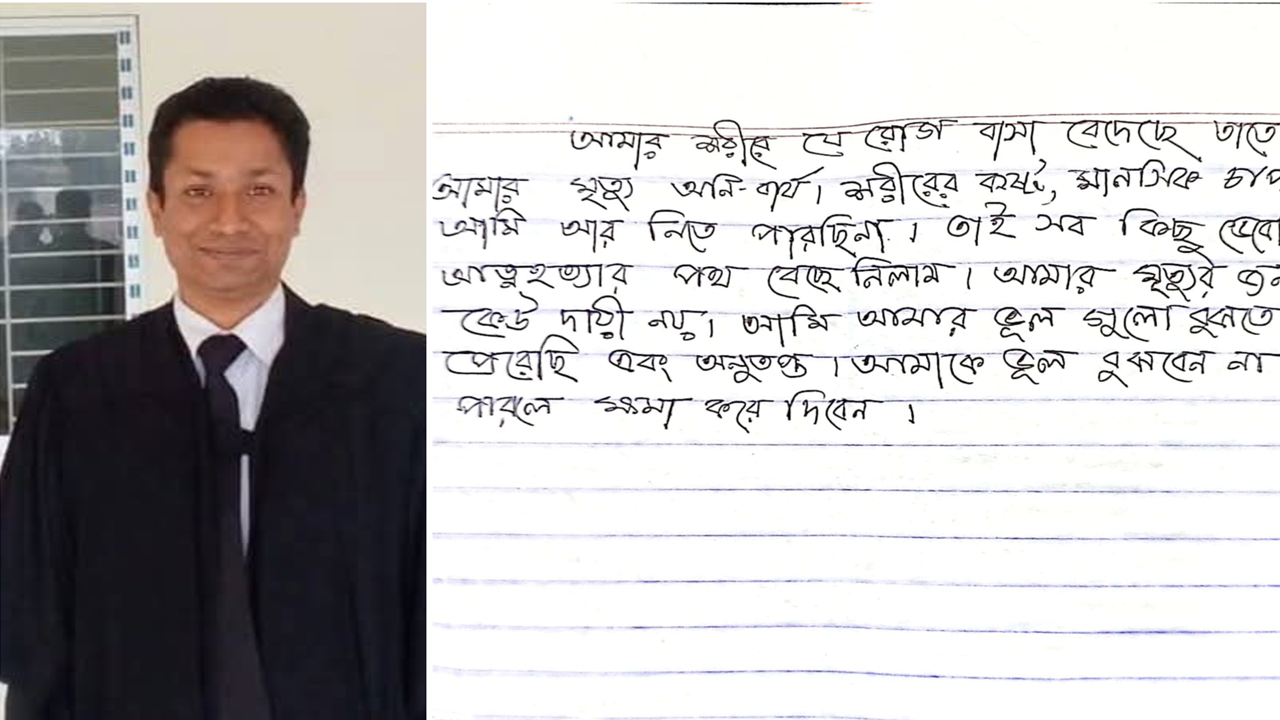
 English (US) ·
English (US) ·