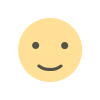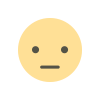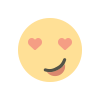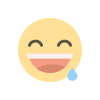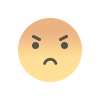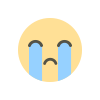উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকার ভবনগুলো তীব্র ঝুঁকিতে
হাসান জাহিদ সমস্ত দেশের বোঝা ঢাকা শহরের কাঁধে। জলবায়ু উদ্বাস্তু, নদীভাঙনের শিকার আর রুজি-রোজগারের সন্ধানে সারা বাংলাদেশ থেকে লোকজন উপচে পড়ছে ঢাকা শহরে। নাজুক ভৌগোলিক অবস্থানের এই ছোট দেশটি নিত্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তথা ঝড়-ঝঞ্জা, বন্যা, পরিবেশ দূষণ ও সর্বোপরি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার এই দেশ। ঢাকা শহর বিশ্বের অন্যতম দূষিত শহর হিসেবে প্রায়ই বিশ্বের বিভিন্ন জরিপে উঠে আসে। ঢাকা মহানগরকে অপরিকল্পিত নগর বলা যায়। যানজট, মানুষের ভিড় যেখানে নিত্যসঙ্গী। বিভাগভিত্তিক জনসংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সবচেয়ে বড় বিভাগ ঢাকার গণনাকৃত জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪২ লাখ ১৫ হাজার ১০৭ জন, সমন্বয়কৃত জনসংখ্যা হলো ৪ কোটি ৫৬ লাখ ৪৩ হাজার ৯১৫ জন, যা দেশের মোট সমন্বয়কৃত জনসংখ্যার ২৬.৬৮ শতাংশ। সবচেয়ে কম জনসংখ্যা বরিশাল বিভাগে, মোট সমন্বয়কৃত জনসংখ্যার ৫.৪৯ শতাংশ। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পিইসি (পোস্ট ইনিউমারেশন চেক) জরিপের আলোকে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর সমন্বয়কৃত জনসংখ্যা প্রকাশ করে পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। এসব প্রসঙ্গ এ কারণে যে, যে কোনো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে একটা দেশের সার
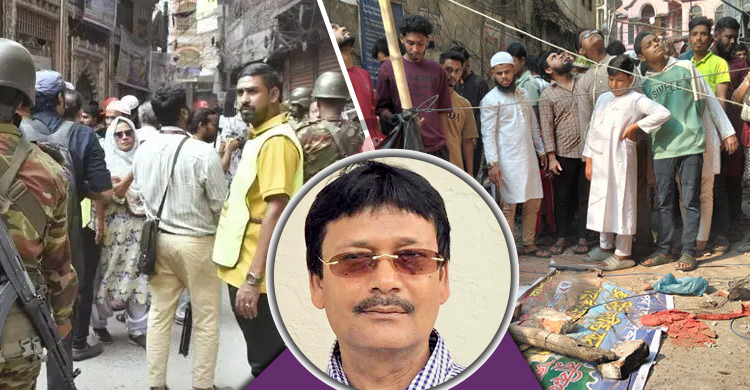
হাসান জাহিদ
সমস্ত দেশের বোঝা ঢাকা শহরের কাঁধে। জলবায়ু উদ্বাস্তু, নদীভাঙনের শিকার আর রুজি-রোজগারের সন্ধানে সারা বাংলাদেশ থেকে লোকজন উপচে পড়ছে ঢাকা শহরে। নাজুক ভৌগোলিক অবস্থানের এই ছোট দেশটি নিত্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তথা ঝড়-ঝঞ্জা, বন্যা, পরিবেশ দূষণ ও সর্বোপরি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার এই দেশ। ঢাকা শহর বিশ্বের অন্যতম দূষিত শহর হিসেবে প্রায়ই বিশ্বের বিভিন্ন জরিপে উঠে আসে। ঢাকা মহানগরকে অপরিকল্পিত নগর বলা যায়। যানজট, মানুষের ভিড় যেখানে নিত্যসঙ্গী।
বিভাগভিত্তিক জনসংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সবচেয়ে বড় বিভাগ ঢাকার গণনাকৃত জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪২ লাখ ১৫ হাজার ১০৭ জন, সমন্বয়কৃত জনসংখ্যা হলো ৪ কোটি ৫৬ লাখ ৪৩ হাজার ৯১৫ জন, যা দেশের মোট সমন্বয়কৃত জনসংখ্যার ২৬.৬৮ শতাংশ। সবচেয়ে কম জনসংখ্যা বরিশাল বিভাগে, মোট সমন্বয়কৃত জনসংখ্যার ৫.৪৯ শতাংশ। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পিইসি (পোস্ট ইনিউমারেশন চেক) জরিপের আলোকে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর সমন্বয়কৃত জনসংখ্যা প্রকাশ করে পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। এসব প্রসঙ্গ এ কারণে যে, যে কোনো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে একটা দেশের সার্বিক ভারসাম্য থাকার প্রয়োজন, যার কোনোটাই নেই বাংলাদেশে। বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকা, বিশেষত পুরান ঢাকা ও অন্যান্য জেলা শহরের প্রবল ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এদিকে জলবায়ু পরিবর্তন চক্ষু রাঙাচ্ছে।
বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে, তাতে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীত হয়ে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ক্ষতির শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। উষ্ণতা বৃদ্ধি মানবসৃষ্ট, প্রাকৃতিক কারসাজি নয়—এটি বিশ্বে আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। আর এই অমোঘ সত্যটাকে বহু বছর যাবত ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টায় রত ছিল বিশ্বের শিল্পোন্নত কতিপয় দেশ। শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উন্নত ও শিল্পায়িত বিশ্বের লাগামহীন কার্বন নিঃসরণের শিকার এখন গোটা বিশ্ব; কেননা উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে বরফ গলছে আর তা স্ফীত করে তুলছে সাগর-মহাসাগরকে। যার কুফলে অধিক ভুগবে বিশ্বের দ্বীপরাষ্ট্রসহ নিম্নাঞ্চলীয় নাজুক ভৌগোলিক অবস্থানের দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশ।
এরকম ঘনবসতির শহরে অনেক ভবনই ভূমিকম্পে ঝুঁকিপূর্ণ। ঠাসাঠাসি ভবন গড়ে উঠছে আর খোলা জায়গা নেই বললেই চলে। ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলে কোনো মাঠে বা খোলা জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার কোনো উপায় নেই। ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পে পুরানো ঢাকার বংশালে ছাদের রেলিং ধসে নিহত হয়েছেন তিনজন। শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে হওয়া এ ভূমিকম্প ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে অনুভূত হয়েছে। এতে তীব্র ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। এতে রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সূত্রমতে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদীতে। উৎপত্তিস্থলে রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। এটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প। এই পর্যন্ত ১০ জন নিহত ও কয়েকশ’ মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশের নরসিংদী থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে। উৎপত্তিস্থলে রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫। এবারের এপিসেন্টার ছিল দেশের অভ্যন্তরেই। বিগত কয়েক বছরই বাংলাদেশে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়ে আসছে। ভূমিকম্পের মাত্রা আরও বাড়লে, ৬ বা ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে এদেশের অনেক ভবন ধসে পড়ার আশংকা রয়েছে। সূত্রমতে, ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে ধসে পড়বে ঢাকার ৪০% ভবন। বিল্ডিং কোড না মানা, অনুমোদিত প্ল্যান ছাড়া বাড়ি তৈরি বা প্ল্যান থাকলেও সেটার পরিবর্তন করে অনেক ভবন নির্মিত হচ্ছে। ঢাকার ভবনগুলোর একটা বড় অংশ ভূমিকম্পপ্রতিরোধক নয়। সস্তা ও নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কারণে ভূমিকম্পে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এসব ভবন।
টপসয়েল ক্ষয়ে যাচ্ছে মাটি উত্তোলন ও খোঁড়াখুঁড়িতে। মাটির নিচে জমা হচ্ছে কোটি কোটি প্লাস্টিক ব্যাগ, যা ২০০ বছরেও বায়োডিগ্রেডেবল নয়। প্লাস্টিক ব্যাগ জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে। খাল-বিল, নদী-নালা ও বিভিন্ন জলাশয় ভরে যাচ্ছে প্লাস্টিক ব্যাগে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ইকোসিস্টেম প্লাস্টিকের আধিক্যে ভারসাম্য হারাচ্ছে। ঢাকার চারপাশে, বিশেষভাবে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীকে মৃতপ্রায় বলা যায়। বুড়িগঙ্গা নদী আজ সম্পূর্ণ মৃত মানববর্জ্যে, হাজারীবাগ ট্যানারির ক্রোমিয়াম, অবৈধ দখলদারিত্ব ও ময়লা-আবর্জনার কারণে। এর তলদেশে জমা হয়েছে লক্ষ-কোটি পলিথিন ব্যাগ।
এতসব সমস্যা নিয়ে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বাংলাদেশে বড় কোনো ভূমিকম্পের ফলাফল হবে ভয়াল। দেশে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। এই ভূমিকম্প হয়েছিল টাঙ্গাইলের মধুপুরের ভূগর্ভস্থ চ্যুতি বা ফাটল রেখায় (ফল্ট)। এরপর ১৪০ বছর হতে চললেও এত বড় ভূমিকম্প ওই ফাটল রেখায় আর হয়নি। মধুপুরের ওই ফাটল রেখায় যদি রিখটার স্কেলে (ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপক) এখন ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্পও হয়, তাহলে ঢাকায় কমপক্ষে ৮ লাখ ৬৪ হাজার ভবন ধসে পড়বে, যা ঢাকার মোট ভবনের ৪০ শতাংশ।
সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ, ওই মাত্রার ভূমিকম্প দিনে হলে কমপক্ষে ২ লাখ ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হবে। আর রাতে হলে কমপক্ষে ৩ লাখ ২০ হাজার মানুষ মারা যাবে। এবার কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গ, গুয়াহাটি এবং বাংলাদেশের ঢাকাসহ বহু জায়গায় অনুভূত হলো ভূমিকম্প। আজ ভারতীয় সময় সকাল ১০টা ১০ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। বাংলাদেশের নরসিংদী থেকে ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের এপিসেন্টার। এদিন সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই জানিয়েছেন ভূমিকম্প অনুভব করার বিষয়টি। ঢাকা, উত্তরবঙ্গ, উত্তরপূর্বের বেশ কিছু স্থানেও এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মধ্য বাংলাদেশে। ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে এই ভূমিকম্প হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎস ছিল। জানা যায়, কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫.২ ছিল। এদিকে ভূমিকম্পের জেরে বাংলাদেশ বনাম আয়ারল্যান্ডের ম্যাচটি বিলম্বিত হয়। ভূমিকম্প অনুভব করায় ক্রিকেটাররা ড্রেসিংরুম থেকে মাঠে নেমে এসেছিলেন। এদিকে মাঠে থাকা দর্শকরাও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও এর ৫ মিনিট পরেই ফের খেলা শুরু হয়ে যায়।
কলকাতা শহরে ভূমিকম্পের সময়ে আতঙ্কে অনেকেই বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন বলেও শোনা গেছে। অনেকের বাড়িতেই দেওয়ালে টানানো ছবি বা সিলিং ফ্যান দুলতে থাকে। বিশেষ করে বহুতলের বাসিন্দাদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক দেখা গিয়েছিল। ফলে বহু বাড়ি থেকেই মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। এই ভূমিকম্পের ফলে কলকাতায় ক্ষয়ক্ষতির তেমন খবর পাওয়া যায়নি। কলকাতা ছাড়া রাজ্যের অন্য কোনো অংশেও কোনো সমস্যা হয়েছে বলে শোনা যায়নি।
অনেক কারণেই ভূমিকম্প হতে পারে। এসব কারণের বেশিরভাগই প্রাকৃতিক। তবে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে ও জানমালের রক্ষায় পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়নের বিকল্প নেই। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়নের বিষয়ে সেমিনার ও আলোচনাই হয়। ভূমিকম্প রোধে শর্ট টার্ম বা লংটার্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যত কোনো পদক্ষেপেই এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি ও দারিদ্র্য গ্রাস করে রেখেছে দেশটিকে বিগত কয়েক দশক ধরে। শহর, উপশহর ও হাউজিংয়ের ব্যবসা রমরমা। চাষের জমি ও জলাভূমি দখল করে চলছে হাউজিং ব্যবসা। প্রকৃতি হারিয়ে যাচ্ছে যত্রতত্র ইটের ভাটায়, গাছপালা–বৃক্ষ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মোচ্ছব চলছে। শিক্ষাবিদ ও প্রকৌশলী শামীমুজ্জামান বসুনিয়ার মতে, ‘ঢাকার প্রায় সব ভবনই ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে। ওয়ারস্ট ভালনারেবল হচ্ছে বুয়েটের লাল বিল্ডিংগুলো। বুয়েটের যে লাল রেসিডেনশিয়াল বিল্ডিংগুলো আছে, সেগুলো হলো মোস্ট ভালনারেবল। আহসানউল্লাহ হলের বয়স হচ্ছে এখন ৭০-৭৫ বছর। ইটের ওপরে তৈরি।’
এ বছর ১ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। ৬০০ জন মারা গেছেন। আরও অনেকের খোঁজ নেই। ভূ-অভ্যন্তরে শিলায় পীড়নের জন্য যে শক্তির সঞ্চয় ঘটে, সে শক্তি হঠাৎ মুক্তি পেলে ভূপৃষ্ঠ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে এবং ভূ-ত্বকের কিছু অংশ আন্দোলিত হয়; এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বছরে লাখ লাখ ভূমিকম্প হয়। এর অনেকগুলো হয়তো বোঝাই যায় না। এগুলোর বেশিরভাগই মৃদু, যেগুলো আমরা টের পাই না। সাধারণত তিন ধরনের ভূমিকম্প হয়ে থাকে—প্রচণ্ড, মাঝারি ও মৃদু। বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় গড়ে ১৩৮ বার ভূমিকম্প হয়। এশিয়া ও জাপানে প্রায় প্রতিদিনই ভূমিকম্প হয়।
সাধারণ জ্ঞানে ভূমিকম্প শব্দটি দ্বারা যে কোনো প্রকার ভূকম্পনজনিত ঘটনাকে বোঝায়। সেটা প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট যাই হোক না কেন। বেশিরভাগ ভূমিকম্পের কারণ হলো ভূগর্ভে ফাটল ও স্তরচ্যুতি হওয়া; কিন্তু সেটা অন্যান্য কারণেও; যেমন: অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, খনিতে বিস্ফোরণ বা ভূগর্ভস্থে নিউক্লিয়ার গবেষণায় ঘটানো আণবিক পরীক্ষা থেকেও হয়ে থাকতে পারে। ভূগর্ভে ভূমিকম্পের প্রাথমিক ফাটলকে বলে কেন্দ্র (ফোকাস) বা অধোকেন্দ্র (হাইপোসেন্টার) এবং অধোকেন্দ্র থেকে উল্লম্ব বরাবর ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কেন্দ্রটিকে উপকেন্দ্র (এপিসেন্টার) বলে।
প্লেট টেকটোনিক জনিত
অনেক আগে পৃথিবীর সব স্থলভাগ একত্রে ছিল। পৃথিবীর উপরিভাগে কতগুলো অনমনীয় প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত বলে ধীরে ধীরে তারা আলাদা হয়ে গেছে। এই প্লেটগুলোকেই বিজ্ঞানীরা বলেন টেকটোনিক প্লেট। আমাদের ভূপৃষ্ঠ অনেকগুলো প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত। টেকটোনিক প্লেটগুলো একে অপরের সঙ্গে পাশাপাশি লেগে থাকে। কোনো কারণে এগুলোর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হলেই তৈরি হয় শক্তি। এই শক্তি সিসমিক তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। যদি তরঙ্গ শক্তিশালী হয়, তাহলে সেটি পৃথিবীর উপরিতলে এসে পৌঁছায়। তখনো যদি যথেষ্ট শক্তি থাকে, তাহলে সেটা ভূত্বককে কাঁপিয়ে তোলে। এই কাঁপুনিই মূলত ভূমিকম্প। কখনো কখনো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।
ভূমিকম্পে করণীয়
> ঢাকা মহানগরীসহ দেশের জেলা শহর ও বন্দরগুলোকে পরিকল্পিতভাবে ও দীর্ঘমেয়াদে পরিবর্ধন ও সংস্কার করা।
> ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পরিকল্পিত নগরী, প্রশস্ত সড়ক, মাঠ ও ফাঁকা জায়গা তৈরি করা প্রধান শর্ত।
> ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরোনো বিল্ডিং শনাক্ত করে ভেঙে ফেলা।
> নতুন উপশহর, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন ও হাউজিং গড়ে তুলতে হবে পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ-এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট) প্রয়োগ করে, ভবন নির্মাণ নীতিমালা অনুসরণ, উপযুক্ত সয়েল টেস্ট ও উন্নত কারিগরী প্রয়োগ করে।
> নতুন ভবন নির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, শক্তিশালী ও টেকসই কাঁচামাল ব্যবহার করা। দক্ষ প্রকৌশলী ও স্থপতির তত্ত্বাবধানে ভবন নির্মাণ।
> জনসচেতনতা তৈরি করা ও আপদকালীন করণীয় সম্পর্কে যথাযথ ট্রেইনিং প্রদান করা।
মনে রাখতে হবে, ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা যাবে না। মানিয়ে নেওয়া ও ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠতে পরিকল্পিত নগরী তৈরি করে টিকে থাকতে হবে প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে।
সূত্র: উইকিপিডিয়া ও গণমাধ্যম।
লেখক: কলামিস্ট।
এসইউ/জেআইএম
What's Your Reaction?