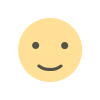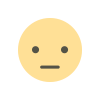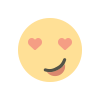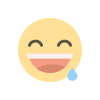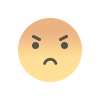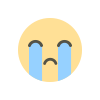এই শহর ছেড়ে আমি পালাবো কোথায়…
শুক্রবারের ভূমিকম্প আতঙ্কের পর থেকে আমার স্ত্রী বলছে, চলো বাড়ি চলে যাই। কিন্তু সে যেখানে যেতে চায়, সেটিও কি নিরাপদ বা ভূমিকম্প হলে আমরা কি সুরক্ষিত থাকবো? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কেননা, ভূমিকম্পের তীব্রতা ও ভয়াবহতা নির্ভর করে সেটির উৎপত্তিস্থল কোথায় এবং এর গভীরতা কতটুকু। কিন্তু তারপরও ঢাকা শহর যে বাংলাদেশের যে-কোনো শহর ও গ্রামের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ কম। গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে সিলেট। তারপরে চট্টগ্রাম। কিন্তু যে মাত্রার ভূমিকম্প হলে সিলেট বা চট্টগ্রামে একশো মানুষের প্রাণহানি এবং গোটা দশেক ভবন ভেঙে পড়বে, সেই একই মাত্রার ভূমিকম্প ঢাকায় হলে প্রাণহানি হবে কয়েক হাজার এবং ভেঙে পড়া ভবনের সংখ্যা হবে কয়েকশো। কেননা ঢাকা এমন একটি শহর, যেখানে প্রায় তিন কোটি মানুষের বাস এবং এখানের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনগুলো গড়ে তোলা হয়েছে গায়ে গা লাগিয়ে। পরিকল্পিত নগরায়ণ বলতে যা বুঝায়, এই মহানগরীতে সেটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শুক্রবারের ভূমিকম্পের রেশ না কাটতেই পরদিন শনিবার এক মিনিটের মধ্যে দুবার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানী ঢাকা। শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে ভ
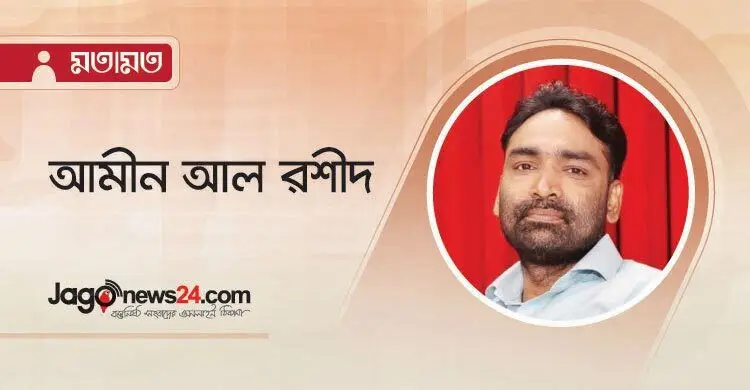
শুক্রবারের ভূমিকম্প আতঙ্কের পর থেকে আমার স্ত্রী বলছে, চলো বাড়ি চলে যাই। কিন্তু সে যেখানে যেতে চায়, সেটিও কি নিরাপদ বা ভূমিকম্প হলে আমরা কি সুরক্ষিত থাকবো? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কেননা, ভূমিকম্পের তীব্রতা ও ভয়াবহতা নির্ভর করে সেটির উৎপত্তিস্থল কোথায় এবং এর গভীরতা কতটুকু। কিন্তু তারপরও ঢাকা শহর যে বাংলাদেশের যে-কোনো শহর ও গ্রামের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ কম।
গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে সিলেট। তারপরে চট্টগ্রাম। কিন্তু যে মাত্রার ভূমিকম্প হলে সিলেট বা চট্টগ্রামে একশো মানুষের প্রাণহানি এবং গোটা দশেক ভবন ভেঙে পড়বে, সেই একই মাত্রার ভূমিকম্প ঢাকায় হলে প্রাণহানি হবে কয়েক হাজার এবং ভেঙে পড়া ভবনের সংখ্যা হবে কয়েকশো। কেননা ঢাকা এমন একটি শহর, যেখানে প্রায় তিন কোটি মানুষের বাস এবং এখানের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনগুলো গড়ে তোলা হয়েছে গায়ে গা লাগিয়ে। পরিকল্পিত নগরায়ণ বলতে যা বুঝায়, এই মহানগরীতে সেটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।
শুক্রবারের ভূমিকম্পের রেশ না কাটতেই পরদিন শনিবার এক মিনিটের মধ্যে দুবার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানী ঢাকা। শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটাল স্কেলে এর মাত্রা ছিলো ৩ দশমিক ৭। এরপরই আরেকটি কম্পন। রিখটাল স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩। উৎপত্তিস্থল খোদ রাজধানীর বাড্ডা এলাকা। এর আগে শনিবার সকাল ১০টা ৪২ মিনিটে দেশকে কিছুটা নাড়া দেয় ভূমিকম্প। এবারও এর উৎপত্তিস্থল নরসিংদী। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিলো ৩ দশমিক ৩। যে কারণে কোনো প্রাণহানির খবর মেলেনি।
প্রশ্ন হলো বাংলাদেশ কি সত্যিই বড় ধরনের ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইন্ডিয়ান, ইউরেশিয়ান ও বার্মা—এ তিনটি প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান এবং বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে বড় বড় ফল্ট আছে। বাংলাদেশ, মিয়ানমার, চীন, ভারত, নেপালের অবস্থান ওই তিন ফল্ট লাইনের আশেপাশে। তাই, মিয়ানমারের ৫ মাত্রার ভূমিকম্প আমরা অনুভব করি। আর যদি সেখানে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়, তখন আমাদের ওপর সেই প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে। আর ভারত বা নেপালে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে ওই সম্ভাবনা আরও বেশি। (সমকাল, ২১ নভেম্বর ২০২৫)।
শুক্রবারের ভূমিকম্পের পরে অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, এ যাত্রা বেঁচে গেছি। বাস্তবতা হলো, ঘনবসতি, দূষণ, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অভাব আর নিরাপত্তাহীনতার বিচারে ঢাকাকে বরাবরই পৃথিবীর বসবাস অযোগ্য শহরের তালিকার প্রথম দিকে রাখা হয়। কিন্তু নানা দুর্যোগ-দুর্বিপাকেও যে এই নগরী অত্যন্ত ঝুঁকিতে রয়েছে, সেটি আমরা মাঝে মধ্যে ভূমিকম্প নাড়া দিয়ে গেলে টের পাই।
খোলা জায়গা বা ওপেন স্পেস ক্রমশই চলে যাচ্ছে বহুতল ভবনের পেটে। সুতরাং প্রতিটি এলাকায় মধ্যম আকারের কিছু খোলা জায়গা বা ওপেন স্পেস তৈরি করা যায় কি না, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কী হয়েছে, তা দেশবাসী জানে। বাস্তবতা হলো, এই শহরে কেউ এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে নারাজ। অথচ মৃত্যুর পরে তার জন্য সাড়ে তিন হাত মাটি ছাড়া আর কিছুই বরাদ্দ থাকে না।
ঝড়-বন্যার মতো আগাম সতর্ক সংকেতের ব্যবস্থা নেই ভূমিকম্পে। অনেকদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে কাজ করছেন। তবে এখনও সেই অর্থে আশার বাণী শোনানো সম্ভব হয়নি। ফলে ভূমিকম্পের মতো সর্বব্যাপী দুর্যোগ নিয়ে আপাতত ভয়ে থাকা এবং ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতা নিয়েই আমাদের চিন্তা-ভাবনা।
ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ঢাকার আশেপাশের কোথাও যদি ৬ মাত্রাও ভূমিকম্পেরও উৎপত্তিস্থল হয়, তাহলে বছরের পর বছর ধরে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা এই নগরীতে কত হাজার মানুষের প্রাণহানি হলো, তা লিপিবদ্ধ করার মতো মানুষও হয়তো এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই আশঙ্কার কারণ মানুষের লোভ, সংকীর্ণতা, দুর্নীতি, অসচেতনতা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রে সুশাসন ও জবাবদিহির সংকট।
বছরের পর বছর ধরে যে-সব বহুতল ভবন গড়ে উঠেছে এই মহানগরীতে, তার কত শতাংশ ভূমিকম্প ঝুঁকি মেনে, অর্থাৎ একটু বাড়তি রড ও নকশায় সঠিক প্রকৌশল জ্ঞান কাজে লাগানো হয়েছে, তার নির্মোহ অনুসন্ধান করা হলে হতাশাজনক চিত্রই বেরিয়ে আসবে।
ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা নানা সময়েই বলেছেন এবং এখনও বলে থাকেন যে, একটি ভবন নির্মাণে যে পয়সা খরচ হয়, সেখাকে অল্প কিছু বাড়তি খরচ করলেই ভবনটিকে ভূমিকম্প সহনীয় করে গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু তারপরও বড় ভূমিকম্পে সেইসব ভবন টিকে থাকবে কি না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে ঝুঁকি অনেকটা কমবে।
ঢাকার সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তৈরি করেছেন এক শ্রেণির লোভী ও অসাধু আবাসন ব্যবসায়ী, যারা বালু দিয়ে জলাশয় ভরাট করে প্রয়োজনীয় পাইলিং এবং বহুতল ভবন নির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপেক্ষা করে রাতারাতি গড়ে তুলেছেন শত শত ভবন। উপরন্তু এসব বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনের নির্মাণ সামগ্রীও কতটা মানসম্মত, প্রশ্ন আছে তা নিয়েও। বলা হয়, যেহেতু আবাসন ব্যবসায়ীরা নিজেরা ওইসব থাকেন না, ফলে তারা ভবন খাড়া করে ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিতে পারলেই বেঁচে যান। কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে।
ভূমিকম্পে ঢাকার আরেকটি বড় ঝুঁকি তৈরি করেছে এই নগরীর অপ্রশস্ত আর অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, গ্যাস ও পানির লাইনের সমন্বয়হীনতা। বড় ভূমিকম্পের পরে প্রথমেই ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস লাইন ফেটে আগুন ধরে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, তা মোকাবিলা করার মতো সক্ষমতা ফায়ার সার্ভিসের আছে কি না, সেটি আরেকটি বড় প্রশ্ন। তাছাড়া সরু রাস্তার ওপর অপিরকিল্পত ভবনগুলোর কংক্রিট এমনভাবে স্তূপ হয়ে পড়ে থাকবে যে, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঘটনাস্থলে যেতেই পারবে না। ফলে ঢাকার আশেপাশে বড় ভূমিকম্পের অর্থই হলো তিলোত্তমা এই নগরী হবে মৃত্যুপুরী।
ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা যে ধরনের নিয়ম মেনে ভবন তৈরির পরামর্শ দিয়ে আসছেন, তা ভবন মালিকরা মানছেন কি না, তা তদারকিতে নির্মোহ ও সততার পরিচয় দিতে হবে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তাদের। যারা মানছেন না তাদের নিয়ম মানতে বাধ্য করতে হবে। পয়সা খেয়ে ভবনের নকশা অনুমোদন দেওয়ার ভয়ানক অসুখ সারাতে হবে। সেক্ষেত্রে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-রাজউকের দুর্নীতির রাশ টানার কোনো বিকল্প নেই।
বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে তিতাসের গ্যাস লাইন আর ওয়াসার পানির লাইনগুলো আধুনিক করে গড়ে তোলা এবং যত দ্রুত সম্ভব এগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করা জরুরি। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো সংস্কারে মালিকদের বাধ্য করা এবং সেখানে যাতে কেউ না থাকেন, সে বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি বাড়াতে হবে।
ঢাকা শহরে বড় খোলা জায়গা বলতে দু তিনটি স্টেডিয়াম আর কিছু খেলার মাঠ ছাড়া আর কিছু নেই। উপরন্তু খেলার মাঠগুলো বিভিন্ন ক্লাবের দখলে। সেসব মাঠের গেট অনেক সময়ই বন্ধ থাকে। রাতের বেলায় ভূমিকম্প হলে মানুষ দৌড়ে গিয়ে যদি কোনো খোলা জায়গায় দাঁড়াতে চায়, সেরকম খোলা প্রান্তর এই শহরে কতটি আছে তা যেমন প্রশ্ন, তেমনি যে-সব মাঠ আছে, বিপদের সময় সেসব মাঠেও বিপন্ন মানুষ গিয়ে দাঁড়াতে পারবে কি না, এই প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।
তাছাড়া এরকম খোলা জায়গা বা ওপেন স্পেস ক্রমশই চলে যাচ্ছে বহুতল ভবনের পেটে। সুতরাং প্রতিটি এলাকায় মধ্যম আকারের কিছু খোলা জায়গা বা ওপেন স্পেস তৈরি করা যায় কি না, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কী হয়েছে, তা দেশবাসী জানে। বাস্তবতা হলো, এই শহরে কেউ এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে নারাজ। অথচ মৃত্যুর পরে তার জন্য সাড়ে তিন হাত মাটি ছাড়া আর কিছুই বরাদ্দ থাকে না।
লেখক : সাংবাদিক ও লেখক।
এইচআর/জেআইএম
What's Your Reaction?