মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো সহজে কিছু পেলে কঠিনে না যাওয়া কিংবা এড়িয়ে চলে। করের ক্ষেত্রেও কথাটি যেন আরো বেশি সত্য। কেনাকাটা থেকে সহজে পাওয়া ভ্যাট এখন আমাদের রাজস্ব সংগ্রহের সবচেয়ে বড় উৎস। পরোক্ষ এই করের বোঝা বেড়েই চলেছে। আরো আছে আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক। পরোক্ষভাবে এর যোগানও দেন জনগণ। বিপরীতে প্রত্যক্ষ কর আদায়ে অগ্রগতি কম। বিপুল সম্পত্তির মালিক কিংবা শিল্পপতিদের পকেটে হাত দিতে সাহস করে না কেউ। অনেক সময় আদালতে মামলা করে তারা পেয়ে যান কর অব্যাহতিও।
২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর আদায়ের লক্ষ্য ৪৮ হাজার কোটি টাকা। যেখানে ভ্যাট থেকে আসবে ৩৮.১ শতাংশ, আমদানি শুল্ক ১০.৩ শতাংশ এবং সম্পূরক শুল্ক ১৩.৪ শতাংশ। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সবস্তরের জনগণ যোগান দিবে প্রায় ৬২ শতাংশ কর। অন্যদিকে করযোগ্য জনগণের একটি অংশ আয়কর বাবাদ যোগান দিবেন ৩৬.৬ শতাংশ।
১০ শতাংশের উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে জীবনযাপন ব্যয় বাড়লেও গেল দুই অর্থবছর ধরেই করমুক্ত ব্যক্তি আয়সীমা সাড়ে ৩ লাখ টাকায় আটকে রাখা হয়েছে। নতুন বাজেটে মাত্র ২৫ হাজার টাকা বাড়ানোর কথা শোনা যাচ্ছে। অথচ প্রতিবেশি ভারতে ৩ লাখ রুপি থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ রুপি করা হয়েছে। বেতনভোগী চাকুরিজীবীদের জন্য ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। (সূত্র: ইকনোমিক টাইমস)
রুপি টাকা বিনিময়হার ১ টাকা ৪৩ পয়সা ধরলে ৪ লাখ রুপির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ লাখ ৭২ হাজার টাকা, আর ১২ লাখ রুপি সমান ১৭ লাখ টাকার বেশি। তাহলে আমাদের করমুক্ত আয় সীমা কত হ্ওয়া উচিত? বিভিন্ন পক্ষ থেকে এই সীমা নতুন অর্থবছরের (২০২৫-২৬) জন্য ৫ লাখ টাকা করার দাবি এসেছে। যারা আয়কর দেন তাদের বড় অংশই চাকুরিজীবী। আবার যারা আয়কর দেয়ার যোগ্য তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম আয়ের করদাতাদের ওপর চাপ বাড়িয়েছি আমরা।
ভারত করেছে তার উল্টোটা। ৪ লাখের বেশি থেকে ৮ লাখ রুপি পর্যন্ত আয়কর ৫ শতাংশ। বাংলাদেশের সাড়ে ৩ লাখের বেশি থেকে সাড়ে ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত ৫ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতে দুই স্তরের ব্যবধান ৪ লাখ রুপি, বিপরীতে আমাদের মাত্র ১ লাখ টাকা। অথচ যারা কর ফাঁকি দিচ্ছে, ব্যাংক ঋণের টাকা পরিশোধ করছে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অক্ষমতা দেখিয়ে আসছে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর।
অপ্রত্যক্ষ করের দিকে তাকালে বৈষম্যের করুণ চিত্র চোখে পড়বে। একজন ভিক্ষুক বাজার থেকে পণ্য কিনে যে পরিমাণ ভ্যাট দিচ্ছেন, কোটি টাকার গাড়ির মালিক্ও একই ভ্যাট দিচ্ছেন। এর পাশাপাশি আছে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক। এসব শুল্ক যোগ করেই একটি পণ্যের দাম নির্ধারণ হয়। ক্রেতা যখন কোন পণ্য কিনেন তখন সমুদয় খরচ তার পকেট থেকেই যায়। এর উদাহরণ-বাজারে পাওয়া বিভিন্ন বিদেশি ফল।
ফল আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক, ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক, ৩০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক, ৫ শতাংশ অগ্রিম কর, ১৫ শতাংশ ভ্যাট, ৫ শতাংশ আগাম কর আছে। সব মিলিয়ে শুল্ক-করভার ১৩৬ শতাংশ। অর্থাৎ ১০০ টাকার ফল আমদানি করলে ১৩৬ টাকা কর দিতে হতো। অগ্রিম কর কমানোয় এখন করভার কিছুটা কমেছে। (সূত্র: প্রথম আলো)
তার মানে ১০০ টাকার ফল বন্দর থেকে বের হওয়ার পর দাম দাঁড়াচ্ছে ২৩৬ টাকা। এর সঙ্গে আরো দুটি স্তর (পাইকারি ও খুচরা) ও তাদের মুনাফা যোগ করে ভোক্তা পর্যায়ে দাম হতে পারে ৩০০ টাকা। এই পুরো টাকাটাই তো একজন ভোক্তা ফল কেনা বাবদ দিয়ে থাকেন। তাই এসব শুল্কও ভোক্তার জন্য পরোক্ষ কর। এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আমরা কত কর দিচ্ছি?
এক বিদেশি ফলেই দিচ্ছি কমবেশি ১৩৬ শতাংশ। মোবাইল ফোন ব্যবহারে দিচ্ছি ৩৯ শতাংশ। আবার নতুন সিম কিনলে ৩০০ টাকা অতিরিক্ত কর। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর করপোরেট কর সাড়ে ৩৭ থেকে ৪০ শতাংশ। মোবাইল অপারেটর গুলোর এই হার ৪৫ শতাংশ। সকল কর দিন শেষে ভোক্তা বা ব্যবহারকারী হিসেবে আমরা পরিশোধ করছি। এর বাইরে কর যোগ্য আয় থাকলে আয়করতো দিচ্ছিই। তাহলে উন্নত দেশের তুলনায় সব মিলিয়ে আমাদের করভার নেহায়েত কম নয়।
অথচ নাগরিক হিসেবে বার বার শুনতে হয়ে আমরা কর দিই না। যে কারণে প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় কর-ডিজিপি অনুপাতও আমাদের সবচেয়ে কম। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ২০২১ তথ্য অনুযায়ী ২০১৬-২০২০ সালে বাংলাদেশে গড় কর-জিডিপি অনুপাত ছিল ৯.৯ শতাংশ। বিপরীতে ভারতে এই হার ১৯.৬৭ শতাংশ, নেপালে ২১.৫ শতাংশ পাকিস্তানে ১৪.৮৮ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কায় ১২.৭৪ শতাংশ (সূত্র: ঢাকা ট্রিবিউন)।
স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে এত কর যায় কোথায়? উত্তরে, নাসিরউদ্দিন হোজ্জার বিড়ালের গল্পটি তুলনীয়। হোজ্জা বাজার থেকে ২ কেজি গরুর মাংস কিনে স্ত্রীকে রান্না করতে বলে বাইরে চলে গেলেন। স্ত্রী রান্না করতে গিয়ে মাংসের সুস্বাদু গন্ধে লোভ সামলাতে পারলেন না। নিজে ও ছেলে মিলে চেখে দেখতে গিয়ে পুরোটাই শেষ করে ফেললেন। হোজ্জা বাড়ি ফিরে মাংস খেতে চাইলে বউ-ছেলে পোষা বিড়ালটা ধরে এনে জানালো; এ সব খেলে ফেলেছে।
হোজ্জা ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। দাড়িপাল্লা আনতে বললেন। পাল্লায় মেপে দেখেন বিড়ালের ওজন ২ কেজির সামান্য বেশি। বউ-ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, বিড়াল যদি ২ কেজি মাংস খায় (যা এখনো হজম হয়নি) তাহলে এর ওজন চার কেজি হওয়ার কথা। তাহলে মাংস গেল কোথায়? আর এটা বিড়াল না হয়ে যদি মাংস হয়, তাহলে বিড়াল গেল কোথায়?
আমাদের পরিস্থিতিও তাই। মাঠের হিসেব বলছে আমরা নাগরিক হিসেবে পরোক্ষা ভাবে বহু কর দিই। অথচ কর জিডিপি হিসাব বলে আমরা কম দিই। তাহলে আমাদের কর যায় কোথায়? এর উত্তর লুকিয়ে আছে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির হিসেবে। অন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর যে শ্বেতপত্র কমিটি গঠন করেছিল, তার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিগত সরকারের সময় জিডিপি বেশি দেখানো হয়েছে। এই সংখ্যাকে বলা হয়েছে অলীক।
বিগত সরকার জিডিপির পরিমাণ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় দেখিয়েছিল। এতে বাজেটের আকার বাড়িয়ে উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা গেছে। এরপর হয়েছে সীমাহীন লুটপাট, যা পারমাণবিক বালিশ কিংবা লাখ টাকার পর্দা নামে গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। যেহেতু কর্মসংস্থান না বাড়িয়ে শুধু জিডিপি বড় করা হয়েছিল, ফলে আমরা বেশি কর দেয়ার পরও কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ছে না।
অনুপাত না বাড়লেও প্রতি বছরই রাজস্ব বোর্ডকে বড় লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়। সেটি পূরণ করতে গিয়ে যারা নিয়মিত কর দেন, তাদের উপর চেপেছে বোঝা। বাড়ানো হয়েছে পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা। অথচ করের বিষয়টি সংসদে আলোচনা হওয়ার কথা। দু:খজনক হলেও সত্য, আমাদের সংসদে কর সংক্রান্ত তেমন কোন আলোচনা হয় না। অথচ উন্নত দেশগুলোতে ঘন্টার পর ঘন্টা এই ইস্যুতে বিতর্ক হয়।
কর আদায়ের আইনী ভিত্তি তৈরি হয় বাজেটের সময় সংসদে পাশ হওয়া অর্থবিলের মাধ্যমে। অথচ এ নিয়ে সেখানে চুলচেরা বিশ্লেষণ না হওয়ায় আমলারা যে বাজেট তৈরি করে দেন সেটাই সংসদে পাশ হয়। অন্যদিকে রাজস্ব বোর্ড লক্ষ্যমাত্রা পূরণে থাকে মরিয়া। এই দুইয়ের মিশেলে কর ন্যায্যতা অনুপস্থিত। অন্তর্বর্তী সরকার চাইলে এই ন্যায্যতা ফিরিয়ে আনার সূচনা করতে পারে। সেই সুযোগ তাদের সামনে আছে।
এরই অংশ হিসেবে হয়তো রাজস্ব বোর্ড বিলুপ্ত করে নীতি ও বাস্তবায়ন বিভাগ আলাদা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে আপত্তির মুখে ৩১ জুলাইয়ের পর্যন্ত তা স্থগিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার আশ্বাস দিয়েছে অর্থমন্ত্রণালয়। যদিও টেকসই সংস্কারের পক্ষে রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও। তবে সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই তা বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছেন তারা। সেই আলোচনা চাইলে শুরু করা যেতে পারে। তবে নাগরিকদের দাবি এই দপ্তরের সেবা সম্পর্কে যেসব অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ আসে তা যেন আগামীতে দূর হয়।
গণমাধ্যমকর্মী ও সাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, ইআরএফ
এইচআর/জিকেএস

 3 months ago
6
3 months ago
6


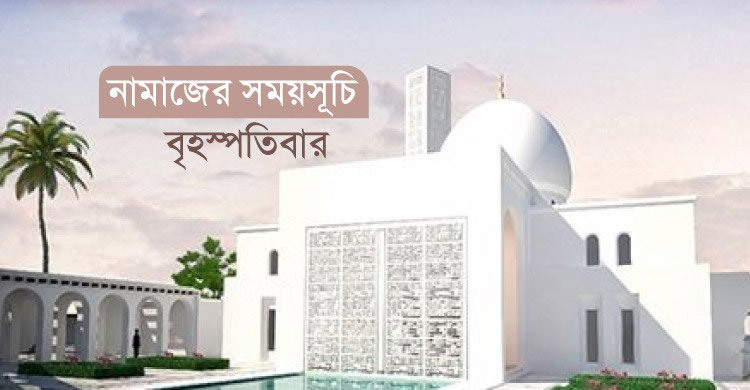


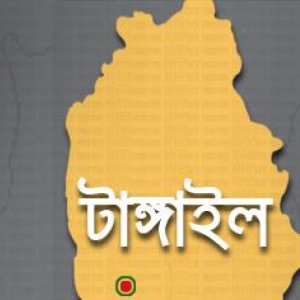



 English (US) ·
English (US) ·