নজরুল ইসলাম সাজু
বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু কবি রয়েছেন, যাঁদের রচনায় নিখাদ দেশপ্রেম, মানবতা ও মাটির গন্ধ মিলে এক অপূর্ব আবেগ সৃষ্টি করেছে। পল্লীকবি জসীম উদ্দীন তেমনই এক সাহিত্যিক, যিনি তাঁর কাব্যজগৎকে কেন্দ্র করেই নির্মাণ করেছেন এক অনন্য পল্লীজীবনভিত্তিক সাহিত্যভুবন। বাংলা কবিতার ধারায় তিনি এমন এক শক্তিমান নাম, যাঁর কলমে পল্লিবাংলার চিত্র এঁকেছেন প্রাণবন্ত রূপে। ‘নকশী কাঁথার মাঠ’, ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’, ‘ধানের গান’ ইত্যাদি তাঁর কালজয়ী কাব্যকর্ম। যা গ্রামীণ জীবন, সম্পর্ক ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।
জীবন ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট
পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের জন্ম ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে। তাঁর বাবা আনসারউদ্দীন মোল্লা ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক এবং ধর্মভীরু মানুষ। মা আমিনা খাতুনের কাছ থেকেই শুনেছিলেন গ্রামীণ লোককথা, গান আর বর্ণনা, যা পরবর্তীতে তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছিল। ছোটবেলা থেকেই জসীম উদ্দীনের মাঝে ছিল এক গভীর অনুভবশক্তি। গ্রামীণ দৃশ্য, কৃষকের মুখের গান, নদীর ঢেউ, মাঠের আল—এসব দৃশ্য তাঁর কিশোর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। তাঁর শৈশব কেটেছে পল্লির কোলে, যা তাকে ভবিষ্যতের ‘পল্লীকবি’ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পরিবারে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ থাকায় তিনি ছিলেন সংযত কিন্তু চিন্তায় উদার এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবতাবাদী।
শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনের ধারা
পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের জীবনপথে শিক্ষাজীবনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁর শৈশবের পল্লিজীবনের সরলতা ও অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর সাহিত্যচর্চায় ভিত্তি স্থাপন করেছে; তেমনই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিক জগতকে প্রসারিত করেছে এবং আধুনিক সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি গঠনে সহায়ক হয়েছে।
প্রাথমিক শিক্ষা
জসীম উদ্দীনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। তারপর তিনি ভর্তি হন ফরিদপুর জেলা স্কুলে। ছোটবেলা থেকেই তাঁর লেখা ও সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল। তিনি কবিতা লিখতেন এবং শিক্ষকদের সামনে তা পাঠ করতেন। তাঁর প্রতিভা খুব দ্রুতই স্কুলের পাঠক্রম ছাড়িয়ে সমাজে বিস্তৃতি লাভ করে।
ফরিদপুর কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর তিনি ভর্তি হন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে। এখানেই তাঁর সাহিত্যচর্চা আরেকটি মোড় নেয়। কলেজের সাহিত্যসভা, সংস্কৃতিচর্চা এবং পারিপার্শ্বিক পল্লিজীবনের অনুরণন তাঁকে আরও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি স্নাতক এবং পরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর স্নাতকোত্তর গবেষণার বিষয় ছিল ‘বাংলার লোকসাহিত্য’, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—তিনি শুধু কবি ছিলেন না, ছিলেন এক নিখাদ গবেষকও।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বীকৃতি
জসীম উদ্দীনের জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক আসে; যখন তাঁর লেখা ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কবিতাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পরীক্ষার সময় জমা দেন। কবিতাটি পড়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুগ্ধ হন এবং তাকে ‘পল্লীকবি’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এটি শুধু একটি স্বীকৃতিই নয়, বাংলা সাহিত্যধারায় পল্লির জীবনের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার দুঃসাহসিক পদক্ষেপ।
পল্লিজীবন ও লোকসাহিত্যে আগ্রহ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি বাংলার লোকগীতি, গ্রামীণ উপাখ্যান, লোককথা ও কৃষকজীবনের মৌখিক সাহিত্যে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি অনেক গ্রামে ঘুরে ঘুরে বয়স্ক মানুষদের মুখ থেকে লোককবিতা ও লোকগান সংগ্রহ করতেন, যা তিনি পরবর্তীকালে সংকলন ও বিশ্লেষণ করেন। এ গবেষণার ফলেই তাঁর সাহিত্য হয়ে ওঠে অধিকতর বাস্তব, প্রামাণ্য ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
শিক্ষাজীবনের সাহিত্যিক ফসল
জসীম উদ্দীনের শিক্ষাজীবন শুধু ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যম ছিল না বরং এটি ছিল তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র। তাঁর লেখা ছড়িয়ে পড়তে থাকে পত্রিকায়—‘কল্লোল’, ‘প্রবাসী’, ‘মাসিক মোহাম্মদী’ ইত্যাদিতে। এ পর্বে তাঁর রচিত বহু কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যা পাঠকমনে গভীর আলোড়ন তোলে।
পল্লিবাংলা ও লোকজ জীবনের প্রভাব
পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের সাহিত্যজগৎ নির্মিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতার ভিত্তিতে—বাংলার গ্রামীণ জীবন। তাঁর কলমে যে গ্রাম উঠে এসেছে, তা নিছক একটি স্থান নয়; বরং এক প্রাণময়, আত্মবিশ্বাসী, ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা। তিনি গ্রামকে শুধু প্রেমের আবেগ দিয়ে দেখেননি; দেখেছেন জীবনবোধ, সংস্কৃতি ও মানুষের সংগ্রামের বাস্তবতায়। এ অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করবো—কীভাবে পল্লীজীবন ও লোকজ ঐতিহ্য তাঁর সাহিত্যকে রূপ, রস ও দার্শনিকতা দিয়েছে।
১. পল্লিজীবনের বাস্তবতা ও জীবনের চলমানতা
জসীম উদ্দীনের জন্ম ও শৈশব কেটেছে বাংলার একটি ছোট গ্রামে, তাম্বুলখানায়। এই পল্লিজীবন ছিল তাঁর প্রথম পাঠশালা। কৃষকের হালচাষ, রাখালের বাঁশি, গরুর গাড়ি, বৈশাখের ঝড়, শ্রাবণের বৃষ্টি, নদীর ঢেউ, মেলা, পয়লা বৈশাখ, পুঁথি পাঠ—এসব ছিল তাঁর জীবন-ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা।
তাঁর কবিতায় আমরা দেখি, তিনি শহরের জটিলতা কিংবা জীবনবিচ্ছেদের বিষাদ নয়, তুলে ধরেন এক নির্মল অথচ সংবেদনশীল গ্রামীণ জীবনধারা: ‘আমি যাহা গাই, তাহা সত্য হইতে গেয়েছে/ আমি তো দেখি নাই কভু মিথ্যার গীত’। এই পল্লিজীবনের মাধুর্যই তাঁকে দিয়েছে আলাদা পরিচিতি।
২. লোকসংস্কৃতি ও লোককথার প্রভাব
জসীম উদ্দীন বাংলা লোকসাহিত্যের একজন সংগ্রাহকও ছিলেন। তিনি গ্রামের পল্লি নর-নারীদের মুখে শোনা গান, উপাখ্যান, লোককাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর লেখায় ধরা পড়ে—বউ কথা কও, পল্লিগান, নিমন্ত্রণ পর্ব, মেলামেশার রীতি, কৃষিভিত্তিক জীবনচক্র, পল্লিনারীর আত্মত্যাগ এবং বিচ্ছেদের বেদনাবোধ। তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ একধরনের পল্লিকাব্য, যেখানে একজন নারী তার জীবনযাপন, বঞ্চনা ও স্মৃতিকে সূচের আঁচরে ফুটিয়ে তোলে—এটি লোকজ ঐতিহ্যের এক অনন্য নিদর্শন।
৩. প্রকৃতি ও ঋতুবৈচিত্র্য
বাংলার প্রকৃতি জসীম উদ্দীনের কাব্যে প্রাণ ধারণ করেছে। তার কবিতায় আমরা পাই—বর্ষার বৃষ্টিস্নাত মাঠ, শরতের কাশফুল, শীতের কুয়াশাঘেরা নদীপাড়, বসন্তের নতুন পাতা ও কোকিলের ডাক। এই প্রকৃতি শুধু পটভূমি নয়, চরিত্র হয়ে কথা বলে। তাঁর কাব্যপ্রকৃতি রূপ পেয়েছে শস্যক্ষেত, নদী, গোধূলি, চাঁদনি রাতে।
৪. গ্রামীণ প্রেম ও সম্পর্কের নিটোল রূপ
জসীম উদ্দীনের প্রেমের কবিতা বা কাব্যনাট্যে প্রেম কখনো শহুরে আদলে নয়—তা সরল, কিন্তু গভীর। ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’- এ সোজন ও দুলালীর প্রেম গ্রামীণ সমাজের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সম্পর্কের এক নিখুঁত উদাহরণ। সেখানে ধর্মীয় বিভাজন, সামাজিক সংকট কিন্তু তার চেয়েও বড় হয়ে ওঠে মানবতা ও ভালোবাসা।
৫. পল্লিজীবনে ধর্ম, উৎসব ও রীতি
তাঁর সাহিত্যে উঠে আসে ঈদের গান, পীর-আউলিয়ার মাহফিল, নবান্ন উৎসব, গায়ে-হলুদ, রাখালদের গীত, চৈত্রসংক্রান্তির নাচ-গান। এসব রীতিনীতির মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সংস্কৃতিকে নতুন করে মূল্যায়ন করেছেন। এসব বিষয়ের ব্যবহারে তিনি সাহিত্যিকের চেয়ে একজন পল্লিচিত্রশিল্পীর মতো হয়ে ওঠেন।
৬. ভাষা ও ছন্দে পল্লির প্রকাশ
জসীম উদ্দীনের ভাষা সরল, অন্তরঙ্গ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিকতা-বহুল। তিনি শহুরে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বা কঠিন রূপক এড়িয়ে সহজ শব্দে গভীর কথা বলেন। যেমন: ‘তুই বিদেশ যাইবি, ভাই/ আমি থাকি গাঁয়ে রে।/ বলিস ভাই রে, ভুইলা যাইস না/ মোরে এই মায়ে রে!’ এ ধরনের ভাষা বাংলার গ্রামের অন্তর থেকে উঠে এসেছে।
>> প্রথম দিককার সাহিত্যচর্চা ও ‘নকশী কাঁথার মাঠ’
পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়েছিল এক অসাধারণ প্রতিভা ও মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়ে। তাঁর প্রথম দিককার সাহিত্যকর্মে যেমন বাংলার নিখাদ গ্রামীণ জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে; তেমনই চিত্রিত হয়েছে তার সহজ-সরল ভাবভাষা, মানবিক আবেদন এবং দারুণ কাব্যগুণ। এ অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করবো—কীভাবে তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু, সেই সূত্রে ‘নকশী কাঁথার মাঠ’-এর আবির্ভাব এবং তা বাংলা সাহিত্যে এক ঐতিহাসিক মোড় এনে দিয়েছিল।
১. সাহিত্যচর্চার সূচনালগ্ন
জসীম উদ্দীনের কাব্যপ্রতিভা বিকশিত হয় তাঁর শৈশবে, যখন তিনি গ্রামের পরিবেশ, মানুষের মুখে শোনা গান, লোককাহিনি ও সামাজিক দৃশ্যাবলির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। ছাত্রজীবনেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন এবং তার কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে বিভিন্ন পত্রিকায়। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পড়ার সময়ে তিনি স্থানীয় সাহিত্যসভা ও কবিতা পাঠে অংশ নিতেন। এ সময়ে তাঁর লেখা কবিতাগুলো ছিল সংবেদনশীল, ভাবগম্ভীর এবং গ্রামীণ জীবনকে ঘিরে আবর্তিত।
২. নকশী কাঁথার মাঠ: জন্ম ও পটভূমি
১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পড়ার সময় তাঁর সাহিত্য শিক্ষক ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অনুরোধে একটি ‘লোককাহিনিভিত্তিক’ কাব্য রচনা করেন। ফলাফল: ‘নকশী কাঁথার মাঠ’। কাব্যটি রচনার পেছনে ছিল একটি সত্য ঘটনা। গল্পটি এক গ্রামের মেয়ে রূপাই ও সাজু—তাদের প্রেম, ভুল বোঝাবুঝি, বিচ্ছেদ এবং সেই বেদনার অভিব্যক্তি হিসেবে সাজুর তৈরি করা কাঁথার উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে। ‘এক বুক কথা, এক নদী কান্না আর এক মুঠো অভিমান’— এ ভাবেই তিনি প্রেম ও বেদনার কাহিনি বুনে চলেন কবিতার ছন্দে।
৩. কাব্যের সারাংশ ও ভাব
‘নকশী কাঁথার মাঠ’ একটি পল্লিকাব্য, যেখানে কাহিনি রূপ পেয়েছে পদ্যে। এটি একটি গীতিনাট্যের আকারে নির্মিত শোকগাঁথা, যেখানে: প্রেম ও বিচ্ছেদ, বঞ্চনা ও প্রতীক্ষা, নারীর আত্মত্যাগ, সমাজের জটিলতা প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাজু প্রেমিক রূপাইয়ের প্রতি ভালোবাসার স্মৃতিকে ধরে রাখতে তার জীবনের নানা ঘটনার প্রতিচ্ছবি এঁকে একখানা কাঁথা তৈরি করে—এই কাঁথাই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু।
৪. কবিতার ভাষা, ছন্দ ও শৈলী
এ কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত সহজ, গ্রামীণ এবং হৃদয়গ্রাহী। আঞ্চলিক শব্দ, উপমা ও ভাবের সংমিশ্রণে এটি হয়ে উঠেছে এক অনবদ্য শিল্পকর্ম। উদাহরণস্বরূপ: ‘সাজু কাঁথা ফেলে রেখে মরে,/ মাঠে পড়ে রহিল ধূলায় পড়ে...’ এ পঙ্ক্তিগুলোর শব্দচয়নে দেখা যায় সরলতা ও আবেগের সংমিশ্রণ। এখানে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বাংলা লোককবিতার ধারায় প্রভাব বিস্তার করে।
৫. পাঠক ও সমালোচকের প্রতিক্রিয়া
‘নকশী কাঁথার মাঠ’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সমকালীন সমালোচক, লেখক ও কবিরা একে ‘বাংলা সাহিত্যের এক নতুন ধারার সূচনা’ বলে আখ্যায়িত করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটি পড়ে অভিভূত হন এবং বলেন—‘ইনি পল্লীর হৃদয়কে যেভাবে ধরেছেন, তা অতুলনীয়।’ তাঁর এ কাব্যই তাঁকে ‘পল্লীকবি’ অভিধায় ভূষিত করে।
৬. সাহিত্যে নতুন ধারা
‘নকশী কাঁথার মাঠ’-এর মাধ্যমে বাংলা কাব্যজগতে একটি নতুন ধারার সূচনা হয়, যাকে আমরা বলি—পল্লীকাব্য। এখানে কাব্যিকতা, কাহিনি, আবেগ, সামাজিক বাস্তবতা এবং লোকজ জীবন একত্রে মিশে যায়। ধারাটি পরে বহু কবি ও নাট্যকার অনুসরণ করেন। তবে জসীম উদ্দীনের মতো গভীরতায় আর কেউ পৌঁছাতে পারেননি।
>> সোজন বাদিয়ার ঘাট ও গ্রামীণ প্রেম
বাংলা সাহিত্যে প্রেম বহুবার চিত্রিত হয়েছে—কখনো তা নাগরিক পটভূমিতে, কখনোবা ঐতিহাসিক আখ্যানের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু পল্লীকবি জসীম উদ্দীন প্রেমকে তুলে ধরেন বাংলার শস্যশ্যামলা পল্লিজীবনের আবহে, যেখানে প্রেমের ভাষা হয় রাখালের বাঁশি, নদীর ধারা, মেঠোপথে হাঁটা দুটি ছায়া। এ অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করবো তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’, যার মাধ্যমে গ্রামীণ প্রেমের এক চিরন্তন উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছে।
১. রচনাকাল ও পটভূমি
‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ রচিত হয় ১৯৫৯ সালে। এটি একটি কাব্যনাট্য, যা জসীম উদ্দীনের সাহিত্যজীবনের মধ্যগগনে রচিত হলেও এর শেকড় নিহীত তাঁর শৈশব ও কিশোর বয়সের গ্রামীণ অভিজ্ঞতায়। গল্পটি মূলত দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়—মুসলিম ও হিন্দু—এর ভিন্নতা সত্ত্বেও গড়ে ওঠা এক নিখাদ প্রেমের উপাখ্যান। প্রধান চরিত্র সোজন একজন মুসলমান রাখাল, আর দুলালী হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। এই দুই চরিত্রের প্রেম বাংলার পল্লিপ্রেমের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়—যেখানে মন ও মানবতা জয়ী হয় ধর্ম ও সমাজের বিভাজনের ঊর্ধ্বে।
২. কাহিনির সার-সংক্ষেপ
সোজন ও দুলালী একসাথে বড় হয়। শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে এক নিঃস্বার্থ প্রেম গড়ে ওঠে। কিন্তু সমাজ-সংস্কার, ধর্মীয় বিভাজন এবং লোকলজ্জা তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের সময় দুলালীর পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।
কয়েক বছর পর দুলালী আবার ফিরে আসে, কিন্তু ততদিনে অনেক কিছু বদলে যায়। দুলালীর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় অন্যত্র। সোজন তখনো দুলালীকে ভালোবাসে, কিন্তু বলে না কিছু। শেষ পর্যন্ত সোজন দুলালীর বিয়ের জন্য গরু জোগাড় করে দেয়, চুপচাপ কাঁদে, এবং বুকে ব্যথা নিয়েই নদীর ঘাটে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে। এই বিচ্ছেদ একদিকে বিষণ্ন কিন্তু অন্যদিকে প্রেমের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতীক।
৩. গ্রামীণ প্রেমের বৈশিষ্ট্য
জসীম উদ্দীনের প্রেমকাহিনির বৈশিষ্ট্য হলো- আভিজাত্যহীন ও নির্মল সম্পর্ক; ভাষায় সহজতা; ভবিষ্যতের চাহিদা নয়, বর্তমানের আবেগ; সম্পর্কে ধর্ম ও জাতের প্রাচীর ভেঙে ফেলা। সোজন ও দুলালীর প্রেম কোনো কাব্যিক অলংকারে আবদ্ধ নয়; বরং তা এতটাই সত্য ও হৃদয়গ্রাহী যে, পাঠক সহজেই তা অনুভব করতে পারে।
৪. ধর্মীয় বিভাজন ও মানবতা
‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ কেবল প্রেমের গল্প নয়; এটি ধর্মীয় বিদ্বেষ, সমাজের সংকীর্ণতা এবং মানুষের অন্ধতার বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ। দুই ধর্মের দুটি তরুণ-তরুণী—যারা কেবল একে অন্যকে ভালোবেসেছিল—তাদের বিচ্ছেদ সমাজ তৈরি করেছে। কবি এখানে বলেন: ‘ধর্ম যার যার, মানুষ সবার’। একটি লাইনের মধ্যেই জসীম উদ্দীন তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। প্রেমকে তিনি দেখেন জাতি, ধর্ম, সামাজিক সংকটের ঊর্ধ্বে এক শুদ্ধ অনুভব হিসেবে।
৫. নাট্যরূপ ও ভাষার গুণ
‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ একটি গীতিনাট্য হলেও এর গঠন অনেকটা কাব্যিক উপন্যাসের মতো। এতে সংলাপ, স্বগতোক্তি ও আবেগ মিলিয়ে এক অদ্ভুত নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি চরিত্র যেন মাটির মানুষ—তাদের ভাষা, অনুভব, প্রতিক্রিয়া—সবই বাস্তব। যেমন এক স্থানে সোজন বলে: ‘তারে ভালোবাসি—এই কথা যদি কও, লোকে হাসে/ চুপ করিয়া থাকি, বুকের ব্যথা কহে কে বসে!’ এ সংলাপে দেখা যায় প্রেমের নিঃশব্দ ত্যাগ, সমাজের ভয় এবং এক গ্রামীণ তরুণের কষ্টকে।
৬. পাঠকপ্রতিক্রিয়া ও সাহিত্যিক মূল্য
‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। এটি আজও বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়। এ কাব্যনাট্য শুধু প্রেম নয়—মানবতা, পারস্পরিক সহাবস্থান ও আত্মত্যাগের পাঠ। সমালোচকদের মতে, এটি বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় গীতিনাট্য, যা সময় ও স্থান পেরিয়ে চিরন্তন হয়ে উঠেছে।
চলবে...
এসইউ/এএসএম

 5 hours ago
3
5 hours ago
3






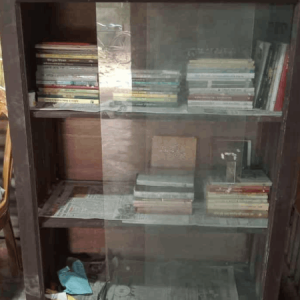


 English (US) ·
English (US) ·