রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই নামের সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও দর্শনের যেমন গভীর সম্পর্ক; তেমনই জড়িয়ে আছে জমিদারির মতো কঠিন এক প্রশাসনিক দায়িত্ব। আজ তাঁর প্রয়াণ দিবসে যখন কবিকে সবাই স্মরণ করছেন; তখন তার জমিদারি জীবনের অধ্যায়টিও বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে।
১৮৯০ সালে দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড ভ্রমণ শেষে বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে কবিগুরু পূর্ববাংলার জমিদারি তদারকির দায়িত্ব নেন। তখন থেকেই তিনি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ছাড়াও নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন নওগাঁ জেলার পতিসরে। এই পতিসরই পরিণত হয় তাঁর জমিদারি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দুতে।
পতিসরের কাছারি বাড়ি থেকে কবিগুরু শুধু খাজনা আদায় বা প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করেননি বরং এখানেই তিনি সৃষ্টি করেছেন মানবিক জমিদারির এক অনন্য উদাহরণ। প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পিতৃতুল্য স্নেহ ও শ্রদ্ধাভরে গড়া। ইন্দিরাদেবীকে লেখা এক চিঠিতে কবি লিখেছেন, ‘এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এদের কোনরকম কষ্ট দিতে আদতে ইচ্ছে করে না। (প্রজারা) যখন তুমি বলতে বলতে তুই বলে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায়, তখন ভারি মিষ্টি লাগে।’ এই বক্তব্য প্রমাণ করে, তিনি জমিদার হিসেবে নিছক কর্তৃত্বের চর্চা করেননি বরং প্রজাদের সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে তুলেছিলেন।
পতিসরে এসে কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, রোগ-শোক আর অবহেলার বাস্তব চিত্র। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরেছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না—এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়! (পত্র ১২১, ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) এমন পরিস্থিতি দেখে তিনি শুধু কবির চোখেই নয়, সমাজ সংস্কারকের চোখেও অবলোকন করেন গ্রামের দুঃখ।
এই দুঃখ লাঘবে রবীন্দ্রনাথ গঠন করেন ‘পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক’ (১৯০৫), যেখানে গরিব কৃষকদের স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে মহাজনী শোষণ থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এমনকি পতিসরের প্রজাদের জমিতে আধুনিক কৃষিযন্ত্র ট্রাক্টর ব্যবহার করার ব্যবস্থাও করেন, যা সেই সময়কার গ্রামীণ বাংলায় বিরল ছিল।
তবে রবীন্দ্রনাথ শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তা করেননি। তিনি শিক্ষার বিস্তারেও আগ্রহী ছিলেন। ১৯৩৭ সালে নিজের উপার্জিত অর্থ—বিশেষত নোবেল পুরস্কার থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ‘কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট’। পতিসরে গড়ে ওঠা হাইস্কুলটি ছিল তার প্রগতিশীল চিন্তার প্রতিফলন। প্রথমদিকে স্কুলে কলকাতা থেকে শিক্ষক আনা হয়েছিল, যা প্রমাণ করে তিনি কতটা আন্তরিক ছিলেন শিক্ষার প্রসারে।
পতিসরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রজাদের আন্তরিকতা ও জীবনসংগ্রাম কবির সাহিত্যকর্মে রসদ জুগিয়েছে। ‘গোরা’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘ঠাকুরদা’, ‘প্রতিহিংসা’ গল্পসহ বহু কবিতা ও গান তিনি লেখেন পতিসরে বসে। নাগর নদীর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি রচনা করেন বিখ্যাত কবিতা ‘মধ্যাহ্ন’, যেখানে বাংলার প্রকৃতি, নিস্তব্ধতা আর গ্রামীণ জীবনের নিপুণ ছবি আঁকা হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক ব্যতিক্রমী জমিদার, যিনি প্রজাদের শুধু শাসন করেননি বরং ভালোবেসেছেন, বুঝেছেন, উন্নয়নের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর জমিদারি জীবন ছিল প্রজাদের সঙ্গে ‘মমতার সেতুবন্ধন’। যেখানে জমিদার-প্রজা সম্পর্ককে রূপ দিয়েছিলেন এক বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়তায়।
১৯৩৭ সালে তিনি পতিসরে শেষবারের মতো আসেন পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। বিদায় বেলায় প্রজাদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি অসুস্থ, আর হয়তো তোমাদের কাছে আসতে পারবো না। তোমরা আমাকে অনেক দিয়েছো। আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারি নাই—আমি প্রার্থনা করি, তোমরা সুখী হও, শান্তিতে থাকো।’ সেদিন পতিসরের আকাশে-বাতাসে কেঁদেছিল ভালোবাসার বিদায়।
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার হিসেবে কেমন ছিলেন?’ তবে উত্তর একটাই, তিনি ছিলেন বাংলার জমিদারি ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। যেখানে ক্ষমতা নয়, মানবতা, মমতা আর সংস্কারের আলো ছড়িয়েছেন প্রতিটি পদক্ষেপে।
তাই তো ইন্দিরাদেবীকে তিনি আরেকটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘আহা, এমন প্রজা আমি দেখিনি, এদের অকৃত্রিম ভালবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক।’
এসইউ/এএসএম

 1 month ago
8
1 month ago
8






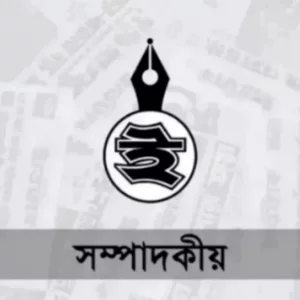


 English (US) ·
English (US) ·