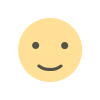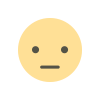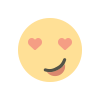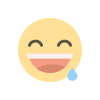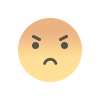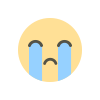বাংলাদেশের উপন্যাসের চলমান ধারা
আলোচনার শুরুতে বলে নিতে চাই, উপন্যাস সাহিত্যের পাশাপাশি সময়ের মনস্তত্ত্ব। সমাজ যেমন : বদলায়, উপন্যাসও তেমনি রূপান্তরিত হয়। সময়কালের বিচারে বাংলাদেশের উপন্যাসকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান পর্ব, দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা-উত্তর ধাপ আর তৃতীয় ভাগে সমকালীন বা ‘চলমান ধারা’। পর্বগুলোর ওপর নির্ভর না-করেও প্রশ্ন তোলা যায়, ‘উপন্যাস কি কেবল সময়কে বর্ণনা করছে, নাকি সময়কেই নির্মাণ করছে?’ এ প্রসঙ্গে কবি ও কথাসাহিত্যিক আল মাহমুদ বলেছেন, ‘সাহিত্য শুধু সময়ের আয়না নয়, সময় নির্মাণেরও হাতিয়ার।’ মনে করি, উপন্যাস শুধু ব্যক্তি বা সমাজের নয়, উপন্যাস নিজেই এক পরিবর্তনশীল সত্তা। চলমান ধারার প্রধান প্রবণতাসমূহ মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস ও জাতীয় চেতনা : স্বাধীনতার পর উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূল কেন্দ্র। সৈয়দ শামসুল হকের ‘নিষিদ্ধ লোবান’, হুমায়ূন আহমেদের ‘আগুনের পরশমনি’, মাহমুদুল হকের \'খেলাঘর\', শহীদুল জহিরের \'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতাসহ দেশের আরও অনেক লেখকের অসংখ্য উপন্যাস সে ধারায় ভূমিকা রেখেছে। আবার স্বাধীনতার আগের দ্রোহের সময়টা উঠে এসেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের \'চিলেকোঠার সেপাই\' উপন্যাসে। আমরা

আলোচনার শুরুতে বলে নিতে চাই, উপন্যাস সাহিত্যের পাশাপাশি সময়ের মনস্তত্ত্ব। সমাজ যেমন : বদলায়, উপন্যাসও তেমনি রূপান্তরিত হয়।
সময়কালের বিচারে বাংলাদেশের উপন্যাসকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান পর্ব, দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা-উত্তর ধাপ আর তৃতীয় ভাগে সমকালীন বা ‘চলমান ধারা’।
পর্বগুলোর ওপর নির্ভর না-করেও প্রশ্ন তোলা যায়, ‘উপন্যাস কি কেবল সময়কে বর্ণনা করছে, নাকি সময়কেই নির্মাণ করছে?’
এ প্রসঙ্গে কবি ও কথাসাহিত্যিক আল মাহমুদ বলেছেন, ‘সাহিত্য শুধু সময়ের আয়না নয়, সময় নির্মাণেরও হাতিয়ার।’
মনে করি, উপন্যাস শুধু ব্যক্তি বা সমাজের নয়, উপন্যাস নিজেই এক পরিবর্তনশীল সত্তা।
চলমান ধারার প্রধান প্রবণতাসমূহ
মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস ও জাতীয় চেতনা : স্বাধীনতার পর উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূল কেন্দ্র। সৈয়দ শামসুল হকের ‘নিষিদ্ধ লোবান’, হুমায়ূন আহমেদের ‘আগুনের পরশমনি’, মাহমুদুল হকের 'খেলাঘর', শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতাসহ দেশের আরও অনেক লেখকের অসংখ্য উপন্যাস সে ধারায় ভূমিকা রেখেছে। আবার স্বাধীনতার আগের দ্রোহের সময়টা উঠে এসেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে। আমরা যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তনের কথা বলি তাহলে শওকত আলির 'দক্ষিণায়নের দিন'-এ দেখি সামাজিক রূপান্তর, রাজনৈতিক মুক্তির পথ কীভাবে জনমনে উঠে আসে তারই বয়ান। বর্তমানে লেখকেরা মুক্তিযুদ্ধকে সরল বয়ানের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক ও পুনঃব্যাখ্যাকেন্দ্রিকভাবে তুলে ধরছেন। যুদ্ধের ভেতরে থাকা মানুষ, যুদ্ধ-উত্তর মানসিকতা, এমনকি প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিও এখন উপন্যাসের উপাদান।
প্রান্তিক ও নিপীড়িত মানুষের বাস্তবতা : এ সময়ের উপন্যাস শুধু শহর কেন্দ্রিক নয়, গ্রাম, চর, পাহাড়, হিজড়া সমাজ, শ্রমজীবী, দলিত মানুষের জগৎ নিয়েও আখ্যান নির্মিত হচ্ছে। হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসসমূহও আমাদের ভিন্ন চোখ খুলে দিয়েছে।
শহুরে জীবন, একাকিত্ব ও মানসিক চাপে ভাঙা মানুষের জীবন : সমকালীন উপন্যাস বলছে, বাইরের সংঘাতের চেয়ে ভেতরের সংঘাত অনেক তীব্র। কর্পোরেট জীবন, পরকীয়া, সম্পর্কের ভাঙন, মাইগ্রেশন, হাহাকার, ভার্চুয়াল বাস্তবতা―এসব এখন চরিত্র নির্মাণের উপকরণ।
সমকালীন নবীন-প্রবীণ অসংখ্য সাহিত্যিকের লেখায় সেই সত্য উঠে আসছে। এক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যের দিকে তাকালেও আমরা তার প্রমাণ পাই। ‘নগরজীবনের ভিড়ে মানুষ সবচেয়ে একাকী’―আলবেয়ার কামুর এই উপলব্ধি এখন একটি বৈশ্বিকরূপ নিয়েছে, আমাদের দেশেও।
নারী-উপন্যাস ও লিঙ্গ-রাজনীতি : আগে নারী ছিল চরিত্র, এখন নারী হচ্ছে বক্তব্য, বয়ান, অবস্থান। শরীর বনাম সত্তা―এই দুই চেতনাকে লেখকগণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন। ‘শরীরের ভাষা মুছে গেলে সত্তার ভাষা শুরু হয়’―আমেরিকান কবি ও সাহিত্যবিশ্লেষক মায়া এঞ্জেলোর এ কথার ভেতরেও লুকিয়ে আছে নারী ও লিঙ্গরাজনীতি বিষয়ক গভীর জীবনবোধ, মনস্তত্ত্ব। আমাদের সমকালীনসাহিত্যেও তার প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। অসংখ্য উদীয়মান লেখক এবং প্রবীণ লেখকগণ বিষয়টিকে নানাভাবে খোলাসা করেছেন।
নতুন ভাষা, নতুন নির্মাণ কিংবা নিরীক্ষায় উত্তরাধুনিক উপন্যাস এখন সরলরৈখিক নয়―খণ্ডিত, ভাঙা, কখনো কখনো কাব্যিক। পুরোনো বা প্রচলিত মিথ ভেঙে নতুন মিথ তৈরি করার প্রবণতা লক্ষণীয়।
'Postmodern fiction is not about telling the story; it is about telling how the story is being told. ক্যানাডিয়ান শিক্ষাবিদ, সাহিত্যতত্ত্ব বিশারদ ও সমালোচক Linda Hutcheon -এর গুরুত্বপূর্ণ কথাটি সাহিত্যে আলাদা দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করে দেয়।
জীবনীভিত্তিক, পুরান, ঐতিহাসিক, অতিপ্রাকৃত, রহস্য কিংবা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস সময়স্রোতে নানাভাবে আমাদের সাহিত্যকে রাঙিয়ে দিচ্ছে। গল্প বলার পাশাপাশি সাহিত্যিকদের মধ্যে লেখার কৌশল বা ঢঙের মধ্যে নানা অনুশীলন কিংবা নিরীক্ষা চলছে।
বিশ্বায়ন ও ডায়াসপোরিক উপন্যাস : অভিবাসী বাঙালির জীবন ধীরে ধীরে উপন্যাসের মসলায় পরিণত হচ্ছে। তাহমিমা আনামের A Golden Age-এর মতো নানা দেশে বসবাসকারী এদেশের লেখকরা আরও অসংখ্য উদাহরণযোগ্য উপন্যাস রচনা করছেন।
শৈলীগত পরিবর্তন : দীর্ঘ বা লম্বা কাহিনি সংক্ষিপ্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। পাঠকের হাতে সমকালীন প্রযুক্তির অসংখ্য বিনোদনের উপকরণ চলে আসায় দ্রুতপঠনের বিষয়টাও বিবেচনা করা হচ্ছে।
উপন্যাসে এখন কী হচ্ছে?
এ সময়ের উপন্যাস উত্তর দেয় না, প্রশ্ন তোলে।
‘The role of the novelist is not to solve the mystery of existence, but to deepen it―Milan Kundera।
ঠিক, সুন্দর সত্য। এটি শুধু সমাজের প্রতিবেদন নয় এখন, সমাজের নানা ক্ষত তুলে আনার পাশাপাশি, অনেক ক্ষেত্রে আত্মার প্রতিবেদনও।
বর্তমানে উপন্যাস কখনো গল্পহীন গল্পও বলছে।
নির্মিত আখ্যানসমূহ কি স্ব-মনস্তত্ত্বমুখী, না সমাজমুখী?
ডিজিটাল যুগে উপন্যাস কি হারিয়ে যাচ্ছে?
লেখকদের মনে রাখতে হবে, যদি কোনো লেখক দ্বারা অন্য লেখক আক্রান্ত হন, অসম্মানিত হন, সেই আক্রমণকারী যতই শক্তিমান লেখক হোন না কেন, গুণগতমানে যতই ভালো উপন্যাস লিখুক না কেন, সাহিত্যমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জুরিবোর্ডের বিবেচনায় তিনি ‘মাইনাস’ পর্যায়ে চলে যান। বিভিন্ন দেশে সাহিত্যবিচারের এটাও একটি মানদণ্ড, নীতিমালার অংশ; জুরিবোর্ডের সদস্যদের পড়ে শোনানো হয়। আমাদের দেশও তার বাইরে নয়। এজন্য আসুন সমকালীন সাহিত্যধারাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে উদার হই, নতুন লেখক এবং পাঠক সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখি।
নাকি নিজেই নতুন ফরম্যাট তৈরি করছে? গল্পহীন গল্পের মধ্য দিয়েও আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই।
বর্তমানে বসে ভবিষ্যতের দিকে তাকালে বোঝা যায় অডিওবুক, ওয়েব উপন্যাস, সিরিজ, চলচ্চিত্রে নতুন অভিযোজন হচ্ছে। তরুণ লেখকরা ফ্ল্যাশ নভেল, মাইক্রোফিকশন, ফিউশন ন্যারেটিভের দিকে ঝুঁকছেন।
নতুন ধারা কি সমাজ, মন উড়িয়ে দিবে?
চলমান ধারা সম্পর্কে বলা যায় : ‘বাংলাদেশের উপন্যাসের চলমান ধারা আসলে এক নদীর মতো―কখনো শান্ত, কখনো দ্রুত, কখনো ভাঙা পথে কিন্তু সে এগোয় সবসময় সময়ের সাগরের দিকে।’
বর্তমান সময়ের ডিজিটাল প্রযুক্তি তরুণ লেখকদের লেখনীতে দুর্দান্তভাবে উঠে আসছে। প্রবীণদের মধ্যে যাঁরা লিখছেন, তাঁরাও এই প্রযুক্তি সাহিত্যে ব্যবহার করে সাহিত্যের সময়কে রাঙিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।
সহজ লেখার গুরুত্ব
‘ভালো উপন্যাস প্রশ্ন তৈরি করে সমাজ পাঠের উত্তর দেয়, পাঠকের মনেই উত্তর জাগানোর প্রক্রিয়ায় নাড়া দেয়।’
‘এখনকার উপন্যাস সমাজের প্রতিবেদন নয়; এটি মানুষের ভেতরের অচলাবস্থার বিরুদ্ধে এক নীরব বিদ্রোহ।’
রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন, ‘সরল লেখা কঠিন শিল্প’, আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ‘সাহিত্যের কোনো শর্ত নেই।’
সাহিত্যিক মানবিকতা : ‘যে সাহিত্যিক বিনয়ী নন, তার সাহিত্য গভীরে পৌঁছায় না'-- বলেছেন জীবনানন্দ দাশ আর গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস বলেছেন, ‘মানুষ ভুল করে; সাহিত্যের কাজ ভুল সংশোধন করা।’
সব মিলিয়ে জোরালোভাবে বলা যায়, ‘উপন্যাস এখন চরিত্রকে বর্ণনা করে না, চরিত্রকে সৃষ্টি করে; পাঠককে পড়ায় না, পাঠকের ভেতরেই প্রবেশ করে।’
সুন্দর সত্য কথা হলো, সাহিত্যের মাধ্যমে মানব মনকে ছুঁয়ে দিতে হবে।
মন ছোঁয়ার জন্য বুঝতে হবে ‘মন’টা আসলে কী?
যদি ‘মন’ই না চিনলাম, অদৃশ্য মনকে ছোঁব কীভাবে?
পড়াশোনা করে কিছুটা জানা যেতে পারে আর নিজের বোধের ভেতর থেকেও আমরা অনেক সময় মেধার গুণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনটা ছুঁয়ে ফেলি। এ জন্য সৃজনশীল সাহিত্যিকদের বিজ্ঞানীও বলতে দ্বিধাবোধ করেন না বিজ্ঞানীরা।
কারণ, সাহিত্যের মাধ্যমে তো প্রতিধ্বনিত হয় মানব মন।
ইতালিয়ান সাহিত্যবিশারদ লঙ্গিনাস এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথও একই ধরনের কথার প্রতিধ্বনি করে গেছেন।
মন জাগাতে হলে, কেবল মন চিনলে চলবে না। মনের চাহিদাও পূরণ করতে হবে, মনের ক্ষুধা নেভাতে হবে। সৃষ্টিশীলতার আলোয় মন জেগে ওঠে তখন।
একেকজনের ক্ষুধা একেক রকম।
তাই সাহিত্যসৃজনেও ব্যতিক্রম থাকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।
সাহিত্যের একটা অংশ হলো 'সমালোচনা সাহিত্য'। এটা
লেখককে সমৃদ্ধ করে। সৃজনশীল বিশ্লেষণও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে একটা নিবিড় পাঠের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়।
‘অমুকের’ সাহিত্য কিছুই হয়নি বলে সহজেই উড়িয়ে দেওয়া এক ধরনের অহংকার।
প্রত্যেকের বইতে কিছু না কিছু ভুল থাকে। সেই ভুল সংশোধন করে দেওয়ার জন্য বন্ধুর মতো লেখক কিংবা প্রকাশককে জানানোই মহান কাজ। তাহলে সাহিত্যের গতিশীল ধারা আরও বেশি ত্রুটিমুক্ত হবে। সমৃদ্ধ হবে।
ছোটোখাটো ভুলের জন্য কোনো লেখককে প্রকাশ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে অপমান করা বা গীবত গাওয়ার অধিকার অন্য কোনো লেখকের থাকা উচিত নয়। কিন্তু এই প্রবণতা এখন কারো কারো মধ্যে উৎকভাবে দেখা যায়। নিজের ভুল ধরার চেয়ে অন্যের ভুল ধরার দিকে আমাদের নজর বেশি। ভাবী নিজের লেখাটাই শ্রেষ্ঠ, ভাবী নিজের সৃষ্টিতে কোনো ভুল নেই, চূড়ান্ত রায় দিয়ে অন্যের লেখাকে উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা চলমান সাহিত্যিক জীবনে ক্ষতিকর। উদ্ধত অহংকারের কারণে বহু নবীন লেখকের লেখকসত্তা, যা বিকশিত হতে পারত, অকাল মৃত্যু ঘটে।
লেখকদের মনে রাখতে হবে, যদি কোনো লেখক দ্বারা অন্য লেখক আক্রান্ত হন, অসম্মানিত হন, সেই আক্রমণকারী যতই শক্তিমান লেখক হোন না কেন, গুণগতমানে যতই ভালো উপন্যাস লিখুক না কেন, সাহিত্যমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জুরিবোর্ডের বিবেচনায় তিনি ‘মাইনাস’ পর্যায়ে চলে যান। বিভিন্ন দেশে সাহিত্যবিচারের এটাও একটি মানদণ্ড, নীতিমালার অংশ; জুরিবোর্ডের সদস্যদের পড়ে শোনানো হয়। আমাদের দেশও তার বাইরে নয়। এজন্য আসুন সমকালীন সাহিত্যধারাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে উদার হই, নতুন লেখক এবং পাঠক সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখি।
আসুন ক্রমান্বয়ে বইবিমুখ হওয়া জাতিকে বইমুখী করার আন্দোলনে যোগ দিই।
আসুন মানুষের মনটা বুঝি, শিশুদের মনটাও।
বই হয়ে উঠুক শিশুদের বিনোদনের শ্রেষ্ঠ উপায়, বন্ধু।
আসুন সমাজকে বুঝি, রাজনীতি-অর্থনীতি-ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধারণ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কটাও বুঝি। বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে আসুন সাহিত্য রচনা করি যা আমাদের সময়কাল এবং জীবন-জগৎ এবং মন আলোময় করবে।
লেখক : কথাসাহিত্যিক, মনোশিক্ষাবিদ ও সম্পাদক, শব্দঘর।
এইচআর/জেআইএম
What's Your Reaction?