যখন পৃথিবীর বাণিজ্য পথে শীতল বাতাস বইতে থাকে, তখন তা কেবল অর্থনীতির ওপর নয়, কূটনৈতিক সম্পর্ক ও ভূরাজনীতির ভারসাম্যেও এর প্রভাব ফেলে। এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি যেন আর কেবল অভ্যন্তরীণ শিল্প রক্ষার হাতিয়ার নয়, বরং হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক প্রগাঢ় ভাষ্য। যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য ঘাটতিতে ভুগছে-দেশটি তার জাতীয় আয় থেকে ব্যয় করে বেশি। আর এই বাণিজ্য ঘাটতি পূরণের প্রচেষ্টা থেকেই অতিরিক্ত বাণিজ্য শুল্ক আরোপের চেষ্টা।
একদা মুক্তবাণিজ্যের অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র আজ নানা নিষেধাজ্ঞা, উচ্চ শুল্ক ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের আশ্রয় নিচ্ছে, বিশেষত চীন, ভারত, রাশিয়া এক কথায় মার্কিনিরা যাদেরকে দমিয়ে রাখতে চায় তাদের বিরুদ্ধে। এই পাল্টে যাওয়া অবস্থান নিছক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অজুহাতে জায়েজ করা হলেও এর ভেতরের গল্প অনেক গভীর। এটি একটি শক্তিমত্তার মেরুকরণ যেখানে বিদ্যমান পরাশক্তি তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে চায়, আর উদীয়মান পরাশক্তি তার জায়গা করে নিতে চায় বিশ্ব বাণিজ্যের মঞ্চে। আমেরিকা বিশ্বের ২০ টি দেশের সাথে FTA চুক্তির মাধ্যমে পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি ভূরাজনৈতিক স্বার্থ নিশ্চিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) আওতায় অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে একটি সুসংগঠিত ও বহুমাত্রিক সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করে।
এই কাঠামোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ধাপে ধাপে শুল্ক হ্রাস বা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে, যাতে অংশীদার দেশের পণ্য বাজারে প্রবেশ সহজ হয় এবং পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, অশুল্ক বাধা যেমন স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কাস্টমস সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে কার্যকর বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। বিনিয়োগ নিরাপত্তার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র ‘ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট’ ও ‘মোস্ট ফেভারড নেশন’ নীতির মাধ্যমে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের স্থানীয় ব্যবসার সমান অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে, যার ফলে পুঁজি ও মুনাফা নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা থাকে।
এছাড়া, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ব্যাংকিং, টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিবহনসহ নানা সেবা খাতে মার্কিন কোম্পানিগুলো অংশীদার দেশের বাজারে প্রবেশাধিকারের সুবিধা পায়। পাশাপাশি, পেশাজীবীদের অস্থায়ী চলাচল সহজ করা হয়, যাতে সেবা ও প্রযুক্তি আদান-প্রদান গতিশীল হয়। যুক্তরাষ্ট্রের FTA গুলোতে বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার (IPR) রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার ফলে মার্কিন পেটেন্ট, কপিরাইট ও ট্রেডমার্ক আইন অংশীদার দেশগুলোতে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং প্রযুক্তি চুরির ঝুঁকি কমে যায়।বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র যেসব দেশের সঙ্গে FTA সম্পাদন করেছে, তার মধ্যে রয়েছে কানাডা ও মেক্সিকো (USMCA), দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ইসরায়েল, বাহরাইন, ওমান, চিলি, পেরু, কলম্বিয়া ও পানামা।
বিশ্ব এখন এক বহুকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে পুরোনো পরাশক্তির আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে এবং নতুন পরাশক্তির উত্থান একটি ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছে। শুল্ক নীতির এই অস্ত্রায়ণ বিশ্ব অর্থনীতিকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছোট ও মাঝারি অর্থনীতিগুলো। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন একটি নতুন বৈশ্বিক সমঝোতা, যেখানে শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞা হবে ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়।
এসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক কাঠামো শুধু অর্থনৈতিক সম্পর্ককে জোরদার করে না, বরং বৈশ্বিক বাণিজ্য রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বজায় রাখতেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। অপর দিকে FTA ছাড়া দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক বেশি শর্তনির্ভর, একতরফা, এবং তুলনামূলকভাবে অনিশ্চিত বা চ্যালেঞ্জিং হয়ে থাকে। এসব দেশের প্রতি মার্কিন আচরণ বেশি নিয়ন্ত্রক (regulatory), এবং অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অবস্থানের প্রতিফলন ঘটায়। ফলে এ ধরনের দেশগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ, টেকসই বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি ও বিনিয়োগ আকর্ষণ করা তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়ে পড়ে। যা বর্তমানে মার্কিন শুল্ক আরোপ নীতি দেখলেই অনুমেয়।
বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতায় শুল্কনীতি শুধু একটি আর্থিক বা রাজস্ব আদায়ের বিষয় নয়, বরং এটি পরিণত হয়েছে ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রে। চীন, যার উত্থান চোখধাঁধানো, মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে একটি কৃষিনির্ভর দেশ থেকে হয়ে উঠেছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। ২০ বছর পূর্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, চীন বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের মাত্র ৮% অবদান রাখতো বর্তমানে চীন বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের প্রায় ৩০% এরও বেশী অবদান রাখে। তার প্রযুক্তি, উৎপাদনশীলতা ও অবকাঠামোগত অগ্রগতি যে হারে ঘটেছে, তা মার্কিন নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী বিশ্বকে নতুন করে চিন্তায় ফেলেছে। ২০১৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনা পণ্যের ওপর ২৫% হারে শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া শুরু করে যা বর্তমানে ১৪৮% এ উপনীত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ ছিল, চীন বাণিজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার নিয়ম লঙ্ঘন করছে, প্রযুক্তি চুরি করছে এবং রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির মাধ্যমে শিল্পকে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখছে। পাল্টা জবাবে চীনও যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়েছে। ফলে দুই পরাশক্তির মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি ট্যারিফ যুদ্ধ শুরু হয়, যার প্রভাব শুধু এই দুটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সারা বিশ্বের সরবরাহ ব্যবস্থা ও বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক শুল্কনীতি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাইডেন প্রশাসন চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ি, সৌর প্যানেল, আধা-পরিবাহী (semiconductor) এবং ব্যাটারির মতো উচ্চ-প্রযুক্তি পণ্যের ওপর শুল্ক বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এর মাধ্যমে একদিকে তারা চীনের প্রযুক্তি খাতে আধিপত্য বিস্তার ঠেকাতে চায়, অন্যদিকে নিজেদের উদীয়মান সবুজ প্রযুক্তি খাতকে রক্ষা করতে চায়। এই দ্বিমুখী লক্ষ্য স্পষ্টতই একটি প্রতিরক্ষামূলক বাণিজ্যবাদের উদাহরণ, যেখানে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আর কৌশলগত আধিপত্য একে অপরের পরিপূরক।
এই শুল্ক যুদ্ধ শুধু যুক্তরাষ্ট্র-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ না থেকে ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, এবং আফ্রিকার দেশগুলোর জন্যও প্রভাব বিস্তার করেছে। বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং বহু উন্নয়নশীল দেশ ন্যায্য বাজার হারাচ্ছে। বিশেষত, যারা চীনের ওপর নির্ভরশীল রপ্তানি বা কাঁচামালের মাধ্যমে যুক্ত, তাদের জন্য এ পরিস্থিতি গভীর অনিশ্চয়তা বয়ে এনেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে আধিপত্য বজায় রেখেছে। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক আরোপের মতো প্রতিরোধমূলক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ আজ কেবল প্রতিযোগিতা নয়, বরং একটি অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধের রূপ নিয়েছে, যা একে ‘বাণিজ্য যুদ্ধ’ নামে পরিচিত করেছে। কিন্তু এই বাণিজ্য যুদ্ধ কেবল দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে এই বাণিজ্যে যুদ্ধ মার্কিনিরা ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী।
সম্প্রতি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের এই অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০%। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫% শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হলেও উভয়পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তিতে উপনীত না হতে পারায় ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক নতুন করে আরও ২৫% শুল্ক যুক্ত করা হয়েছে। এতে করে ভারত এখন ব্রাজিলসহ এমন কয়েকটি দেশের কাতারে চলে এসেছে, যাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি শুল্ক আরোপ করেছে।
এর মূল কারণ হলো ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে রাশিয়ার কাছ থেকে ভারতের বিপুল পরিমাণ তেল কেনা। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ভারত এই তেল কম দামে কিনে তা প্রক্রিয়াজাত করে খোলা বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে।
এই উচ্চ শুল্কের কারণে ভারতের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশেষ করে টেক্সটাইল, সামুদ্রিক খাবার, চামড়া ও জুতা, গহনা এবং রাসায়ানিক পণ্যের মতো শিল্পগুলো মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। Fitch Ratings-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মনে করছে, এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও কিছুটা কমে যেতে পারে। তবে ভারত সরকার এই শুল্ক আরোপকে "অযৌক্তিক এবং অন্যায্য" বলে নিন্দা জানিয়েছে। একই সঙ্গে তারা জানিয়েছে যে ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ অনেক সময়ই কৌশলগত চাপ প্রয়োগের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় বিশেষত চীনবিরোধী কৌশলগত অক্ষ তৈরি করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আবারও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে।
বিখ্যাত অর্থনীতিবিদেরা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সুরক্ষাবাদী শুল্কনীতিকে একটি মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে অভিহিত করছেন। কেননা, ইতিহাসই বলে দেয় যে, অভ্যন্তরীণ বাজারকে শুল্কের দেয়াল তুলে রক্ষা করা দীর্ঘমেয়াদে কোনো দেশের শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। বরং এতে উদ্ভাবনের গতি কমে, প্রতিযোগিতা কমে, এবং উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি অবশেষে তার নিজস্ব শিল্প ও রপ্তানিকে ‘বুমেরাং’ আকারে আঘাত হানতে পারে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত কৌশলগত এবং জটিল। ভারত একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তির অংশীদার, আবার অন্যদিকে ব্রিকস জোটে চীনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে,যা ওয়াশিংটনের জন্য একধরনের কূটনৈতিক দোদুল্যমানতা তৈরি করেছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো, নানা উত্তেজনার মধ্যেও ভারত ও চীনের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০২৪ সালে প্রায় ১৩৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
এখানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে লুকিয়ে আছে কৌশলগত বাণিজ্যিক সমঝোতা যা যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। যুক্তরাষ্ট্র চায় ভারতকে চীনের বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে-বিশেষত হাই-টেক সাপ্লাই চেইনে। এর মাধ্যমে ওয়াশিংটনের লক্ষ্য চীনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি "চীনা-বিকল্প কাঠামো" দাঁড় করানো। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে প্রযুক্তি স্থানান্তর, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও চিপস উৎপাদনে সমঝোতা হয়েছে।
তবে প্রশ্ন হচ্ছে-যুক্তরাষ্ট্র যদি একই সময়ে ভারতের বাজারের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপায়, GSP সুবিধা বাতিল করে এবং ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা হ্রাস করে, তাহলে সম্পর্কের গভীরতা কতটা কার্যকর থাকবে? ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতি, যাকে মার্কিন ভূ-কৌশলগত স্বার্থের কেন্দ্রে দেখা হচ্ছে, যদি বারবার শুল্ক ও বাণিজ্য বাধার শিকার হয়, তাহলে আস্থা ও কৌশলগত অংশীদারিত্বে ফাটল ধরবে না?
অন্যদিকে চীন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও, তার রপ্তানি প্রবাহে যুক্তরাষ্ট্র এখনও একটি বিশাল বাজার। ২০২৩ সালে চীনের যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৫৬০ বিলিয়ন ডলার-যা বাণিজ্য যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞার মাঝেও আশ্চর্যজনকভাবে স্থিতিশীল। একই সময়ে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে আনুমানিক ৯০ বিলিয়ন ডলার, যা দ্রুত বাড়ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভারত একটি বিকল্প হলেও, তা এখনও চীনের তুলনায় ছোট; কিন্তু কৌশলগতভাবে তা অনেক বড় শক্তি হয়ে উঠছে।
ব্রিকস জোটের মধ্যেই আবার ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা-এই পাঁচ দেশ ভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে একত্রিত হলেও, তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা এবং ডলারের বিকল্প মুদ্রাব্যবস্থার প্রতি ঝোঁক যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ও নিষেধনীতি আরও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। সুতরাং, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শুল্কনীতি শুধু অর্থনৈতিক বা রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নয়, বরং এটি ভূরাজনীতির ঘুঁটি হিসেবেও ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। কিন্তু যে পৃথিবী বহুমেরুপ্রবণ হয়ে উঠছে, যেখানে বিকল্প বাজার, বিকল্প মুদ্রা এবং বিকল্প বাণিজ্য পথ গড়ে উঠতে পারে, সেখানে অতি-সুরক্ষাবাদ হয়তো এক সময় নিজস্ব অবস্থানকে সংকুচিত করবে। শুল্ক একটি দেয়াল, যা হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বীকে থামিয়ে দিতে পারে সাময়িকভাবে। কিন্তু দেয়ালের অপর পাশে যদি মিত্ররাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এই দেয়াল একদিন নিজের ওপরই ভেঙে পড়ে।
এই নিষেধাজ্ঞা নির্ভর নীতি বাস্তবিক অর্থে বিশ্ব বাণিজ্যের লিবারাল অর্থনীতিবাদের ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন (WTO)-এর বিধিবদ্ধ কাঠামো আজ প্রায় অচলাবস্থার সম্মুখীন। বহুপাক্ষিক বাণিজ্যের আদর্শ যেখানে এক সময় কার্যকর ছিল, সেখানে এখন দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিড়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) বহুবার এই ট্যারিফ যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, কারণ এটি মুক্ত বাণিজ্যের মূল চেতনার পরিপন্থি। কিন্তু শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ যখন নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় আক্রমণাত্মক বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে, তখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা অনেকাংশেই প্রশ্নের মুখে পড়ে।
বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য এই পরিস্থিতি দ্বিমুখী প্রভাব নিয়ে এসেছে। একদিকে, ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৈরিতা বাংলাদেশকে বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ব বাজারে একটি সম্ভাব্য অবস্থানে নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে, শুল্ক নীতির জটিলতা ও নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা আমাদের রপ্তানি বাজারে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পে প্রবেশ বা নতুন বাজার দখলের কৌশলে তাই বাংলাদেশকে সচেতন ও চতুর কূটনৈতিক অবস্থান নিতে হবে।
বিশ্ব এখন এক বহুকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে পুরোনো পরাশক্তির আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে এবং নতুন পরাশক্তির উত্থান একটি ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছে। শুল্ক নীতির এই অস্ত্রায়ণ বিশ্ব অর্থনীতিকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছোট ও মাঝারি অর্থনীতিগুলো। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন একটি নতুন বৈশ্বিক সমঝোতা, যেখানে শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞা হবে ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। শুল্ক যুদ্ধের উত্তপ্ত ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বৃহৎ অর্থনীতিগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায়সংগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাণিজ্যিক নীতির বিকাশ ঘটানো। অন্যথায়, আজকের শুল্কনীতি আগামী দিনের রাজনৈতিক সংঘাতের বীজ বপন করতে পারে-যার মূল্য গোটা বিশ্বকেই দিতে হতে পারে।
লেখক : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক বিশ্লেষক।
এইচআর/এএসএম

 4 weeks ago
10
4 weeks ago
10


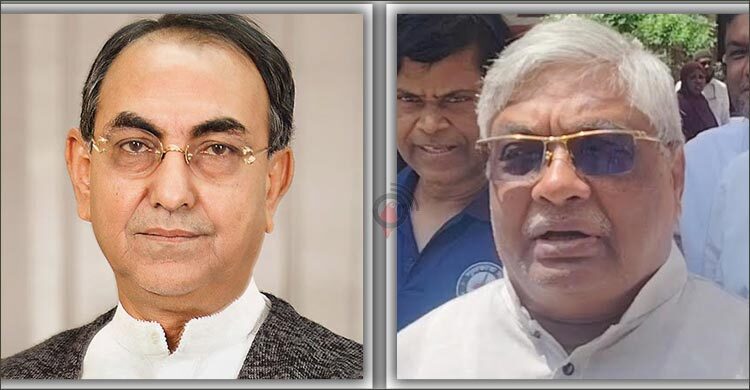






 English (US) ·
English (US) ·