“অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি/জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি
এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম/ অবাক পৃথিবী! সেলাম তোমাকে সেলাম”
ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও অপমান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন এই কবিতা। শুধু যুদ্ধ নয়, মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকার ও তৎকালীন কিছু ধনী সমাজের সৃষ্ট সংকট। তার সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে এসেছিল , বন্যা ও মহামারি । হাজার হাজার অসহায় মানুষ না খেতে পেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে দেখে তিনি লিখেছিলেন ‘কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।’ এরকম উপমার পাশাপাশি বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে যিনি কবিতা লেখেন তিনি বাঙালির সুপরিচিত কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।
বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার শিমুলতলা গ্রামে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস ছিল। তার পিতার পিতা অর্থাৎ কবির পিতামহ পেশায় ছিলেন একজন আদালতের পেশকার। কাজের সূত্রে তিনি পরিবার নিয়ে স্বাধীনতার আগেই স্থায়ীভাবে এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন। ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট (১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৩০ শ্রাবণ ) কলকাতার কালীঘাটের মহিম হালদার স্ট্রিটে মাতুলালয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার সুকান্ত নাম রাখেন জ্যাঠতুতো দিদি। এই দিদি অল্প বয়সে মারা যান। তার কিছুদিন পরেই মাকেও হারান কবি। বাবার নাম ছিল নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও মাতার নাম সুনীতি দেবী। বাবা ছিলেন পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশক। বিখ্যাত সরস্বতী লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী ছিলেন।
কুড়ি বছর বয়সে কবি প্রথমে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন, তারপর সেরে উঠলে মারণ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি যাদবপুর টিবি হাসপাতালে ভর্তি হন। তার লেখা শেষ কবিতার বই ‘ছাড়পত্র’ তখন ছাপা হচ্ছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছাপা অক্ষরে ওই বই আর দেখে যেতে পারেননি। ১৯৪৭ সালের ১৩ মে মাত্র ২১ বছর বয়সে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য অমৃতলোকে যাত্রা করেন। আর বাঙালির জন্য রেখে যান বিপ্লবের প্রেরণা, সাম্যের উৎসাহ বার্তা।
সুকান্ত ভট্টাচার্য ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছে রামায়ণ-মহাভারত শুনতেন। মা যখন পড়তেন তখন তিনি অনেক মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। সেখানে কারও ওপর অন্যায়ের কথা শুনলে তিনি বিচলিত হয়ে উঠতেন। কারও দুঃখের কথা শুনলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। এসবের পাশাপাশি তিনি অনেক ছড়া, কবিতা ও গল্পের বই পড়তেন ।
পশ্চিমবঙ্গের বেলেঘাটায় ‘কমলা বিদ্যামন্দির’ নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কবি সুকান্তকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এখানেই তিনি পড়াশোনা করেন। তার মেধা এবং বিচক্ষণতার কারণে খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষকদের স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। তিনি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তেন তখন থেকেই কবিতা-ছড়া লিখতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি ‘সঞ্চয়’ নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাঁর লেখা কবিতা ‘শিখা’ নামে একটি পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল।
তাঁর লেখা ‘বিবেকানন্দের জীবনী’ ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শিখা পত্রিকায়। বয়স যখন মাত্র দশ-এগারো বছর তখন ‘রাখাল ছেলে’ নামক একটি রূপক গীতি চিত্র রচনা করেন। এছাড়া ‘মধুমালতী’ ও ‘সূর্যপ্রণাম’ নামক দুটি গীতিচিত্রও রচনা করেছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হলে সুকান্ত ভট্টাচার্য বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে ভর্তি হলেছিলেন। যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়তেন তখন ছাত্রদের লেখা ও ছবি নিয়ে হাতে লেখা একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার নাম দিয়েছিলেন ‘সপ্তমিকা’।
স্কুলে পড়ার সময় শিক্ষকরা সুকান্তকে সাহিত্য সাধনায় বিশেষ উৎসাহ দান করতেন। সাহিত্য সাধনায় দারুণ অনুরাগ ছিল। তার পাশাপাশি নানান সমাজসেবামূলক কাজেও বেশ উৎসাহী ছিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় অগ্রগতির জন্য নিজে কোচিং ক্লাস খুলে পড়াতেন।
১৯৪৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে সদস্য পদ লাভ করেন এবং পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর সাহিত্য সাধনা। ১৯৪৪ সালে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পীর সংঘের পক্ষে তাঁর সম্পাদনায় ‘আকাল’ নামের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। পার্টির কাজে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কাগজ বিক্রি করতেন। এই কাগজ বিক্রি করতে গিয়ে অনেক বিপদে পড়েছিলেন। এই বিপদই তাকে সত্যিকারের কবি হতে সাহায্য করেছিল।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উঁচু ক্লাসের মানুষদের অত্যাচার বেড়ে যায় সাধারণ মানুষের প্রতি। মানুষ না খেয়ে ধুকে ধুকে আস্তাকুঁড়ে মারা যাচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকার সাধারণ মানুষের দিকে ফিরেও তাকায়নি সেই সময়। বিভীষিকাময় দিনগুলিতে বিভ্রান্ত জনগণকে সতর্ক করতে, অসহায় মানুষকে একতাবদ্ধ করতে সুকান্তের কলম ঝলসে উঠেছিল। তিনি লিখলেন,
“শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হলো কত মৃত মানুষের হাড়?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।”
সুকান্তের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল অত্যন্ত আর্থিক অনটন ও পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্যে। তিনি স্কুলের গণ্ডি পার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অঙ্কে কম নম্বর পাওয়ায় পরীক্ষা দিয়েও কৃতকার্য হতে পারেননি।
এর কিছুদিনের মধ্যে ‘কিশোর বাহিনী’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। অনেক ছেলে-মেয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়েছিল। এসব ছেলেমেয়ের তিনি স্বাধীনতার আদর্শে ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।
কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা ‘স্বাধীনতা’র কিশোর সভা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন সুকান্ত। কিশোর সভার সব ছড়াগুলোই ছিল সুকান্তের নিজের লেখা । তিনি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে নিজেকে শামিল করেছিলেন। সংসারে অভাব-অনটনের মধ্যেও তাঁর কলম থেমে থাকেনি। তিনি সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের কষ্টের কথা লিখতেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা বিখ্যাত কবিতা ‘রানার’ আমাদের সুপরিচিত। এখানেও তিনি সমাজের এক সাধারণ পেশার অসাধারণ কর্তব্যের আখ্যান তুলে ধরেছেন। সুকান্তের ‘বিদ্রোহ’ কবিতাটি পড়ে আজও অনেকে অনুপ্রাণিত হন।
ভারতের দুটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী সুকান্ত। তাই তার কবিতা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত। তার লেখা আত্মবিশ্বাস, ঘৃণা, ক্ষোভ, ভবিষ্যতের আশা ও স্বপ্ন মিশ্রিত কবিতা প্রত্যেকের কাছেই প্রিয়। সুকান্ত আগামী দিনের ইতিহাসের প্রবক্তা। সুকান্তের কাব্যগ্রন্থ তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় । তাঁর ছাড়পত্র (১৯৪৭)– , ঘুম নেই , পূর্বরাগ (১৯৫০ ), গীতিগুচ্ছ (১৩৭২ বঙ্গাব্দে) , মিঠেকড়া (১৩৫৮ বঙ্গাব্দে) , অভিযান (১৩৮৪ বঙ্গাব্দে) , হরতাল (১৩৬৯ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয়। তার কতকগুলো কবিতা যথা- রানার , সিঁড়ি , ছাড়পত্র , হে মহাজীবন, বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ ।
বাংলা কাব্যের চিরায়ত ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সুফল তিনি তার কবিতায় আত্মসাৎ ও অন্তরস্থ করে নিতে পেরেছিলেন। তার অসামান্য প্রতিভার দ্বারা সামাজিক অন্যায় ও অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনা, সাম্প্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও পীড়ন, ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার কবিতা ছিল সোচ্চার। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বাণী তার রচনায় উচ্চকণ্ঠেই সর্বদা লিপিবদ্ধ করেছেন ।
বাংলাদেশে সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক ভিটেটি হাসিনা সরকার ২০১০ সালে সংরক্ষণ করে অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। এখানে তাদের নানা স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত আছে মর্যাদা সহকারে।পাঁচিল ঘেরা বিরাট এলাকা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বেশ কয়েকবার এখানে এসেছেন স্মৃতির টানে। বাড়ির পাশেই কবি সুকান্ত নামে নির্মিত হয়েছে এক বিশাল পার্ক। এছাড়াও কবির নামে বিশাল অডিটোরিয়াম, গ্রন্থাগার নির্মিত হয়েছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বেশ কয়েকদিন ধরে সুকান্ত মেলা নামে উৎসবের আয়োজন করা হয়। বাড়ির ভেতরে ঢোকার মুখেই রয়েছে কবির বিশাল ভাস্কর্য। সারা বছর ধরেই এখানে দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসেন।
কবির স্বল্প স্থায়ী জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে কলকাতার বেলেঘাটা ৩৪ হরমোন ঘোষ লেনের বাড়িতে। এই বাড়িটি এখনো অক্ষত আছে। পাশের বাড়িটি ছিল ভাইয়ের বাড়ি। এখানে এখনো বসবাস করে কবির একমাত্র ভাইয়ের পরিবার-পরিজন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জননেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কবির নিজের ভাইয়েরই ছেলে।
আমরা শক্তির কথা বলি, জাগরণের কথা বলি। মাত্র কুড়ি বছর কয়েক মাসের জীবন, সদ্য কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেওয়া একজন কবির মধ্যে কতটা বারুদ থাকতে পারে তা সুকান্তের কবিতা পড়লেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। বিপ্লব আর স্বাধীনতার দাবিতে চির আপসহীন ছিলেন তিনি। মাত্র ছয় বছরের লেখার সময়কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদের ভয়াবহ আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কবির কলমে জ্বলেছে আগুন। এসবের বিরুদ্ধে তারুণ্যের গান, কবিতার ছন্দ কিছুই বাদ যায়নি তার কলম থেকে।
সুকান্ত ভট্টাচার্য বুর্জোয়া রাজনীতির প্রভাব বলয় ভেঙে নতুন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে নিবেদিত থেকে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করতে সমাজ চেতনা ও মূল্যবোধ জাগরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাঁর জীবন চর্যায় ও সাহিত্য সাধনায়। সুকান্ত ছিলেন গণমানুষের কবি। তাই জীবদ্দশায় সরকারি রোষানলে পড়ে তাঁর মূল্যায়ন হয়নি। তবে অকাল মৃত্যুর পর তাঁর লেখা অপ্রকাশিত কবিতা একে একে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সচেতন সংবেদনশীল পাঠক সমাজ তাঁর কবিতা থেকে সমাজ পরিবর্তনের জোরালো উদ্দীপনাময় রসদ খুঁজে পান।
সুকান্তর কবিতার বিষয়ে আবর্তিত হয়েছে সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনা। এই ভাবনা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর কলমের ভাষা হয়ে উঠতো তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর। উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা শিশুটির জন্য সূর্যের কাছে তাপ প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু নিজের জন্য কখনো কারও কাছে হাত পাতেননি। 'ছাড়পত্র' কাব্যে তিনি আকাশের চাঁদকে পূর্ণিমার ঝলসানো রুটি বলে অভিহিত করেন। এ যেন দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে আপামর জনতার খাদ্যের আরতি। সুকান্তের কবিতার মূর্ততা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়।
'রানার' কবিতায় চরম দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের যন্ত্রণার কাহিনি ছন্দ রূপ লাভ করেছে। ‘পিঠেতে টাকার বোঝা তবুও যাবে না ছোঁয়া’। তেমনি ‘সিগারেট’ কবিতায় তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাওয়া মানুষের গভীর মর্ম যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। ‘দেশলাই কাঠি' কবিতায় গ্রাম থেকে গ্রামে, শহরে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র বিপদের আগুন ছড়িয়ে পড়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। ‘আমরা বন্দী থাকবো না তোমাদের পকেটে পকেটে, আমরা বেরিয়ে পড়বো ছড়িয়ে পড়বো, শহরে -গ্রামে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে।’ নিজের বাড়ির সিঁড়িতে উঠতে উঠতে লিখেছিলেন তার বিখ্যাত ‘সিঁড়ি’ কবিতা। একের পর এক সিঁড়িকে মাড়িয়ে চলে যেমন মানুষ উপরে ওঠে সমাজের ধনী বড়লোকরা গরিব জনসাধারণের রক্ত চুষে দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে ওঠে। একবার ভুলেও তারা নিচু তলার মানুষের যন্ত্রণার কথা ভাবে না। তাই লিখেছিলেন,
"আমরা সিঁড়ি,
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে, প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরেও তাকাও না পিছন দিকে,
তোমাদের পদধূলি ধন্য আমাদের বুক,
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন।"
১৯৪৬ সালের ভ্রাতৃঘাতী- আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কীভাবে দুর্বল বিভ্রান্ত করেছিল তার দৃষ্টান্ত পাই সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘ঐতিহাসিক’ কবিতায়। তিনি লিখেছিলেন,
"তোমাদের ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলা দেখে/ বন্ধ হয়ে গেছে মুক্তির দোকানের ঝাঁপ”।
পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ কীভাবে সব মানুষকে একইসঙ্গে চরম সংকটে ফেলে এবং সবাই ধর্ম বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে একই খাদ্যের সারিতে দাঁড়িয়ে যায়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘ঐতিহাসিক’ কবিতায়।
"একদিন দুর্ভিক্ষ এল, ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়/ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে,/ইতর -ভদ্র হিন্দু আর মুসলমান একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।"
কবি নির্বিচার খুন, হত্যা লীলা, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ‘দিন বদলের পালা’ কবিতায়। দেশজুড়ে এবং সারা বাংলায় দাঙ্গা হানাহানি, খুন রাহাজানি, চরম দুর্নীতি, অনাচার যেখানে চলছে কবি সুকান্তের সেই কবিতার বাণী মনে হয় যেন আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক।
শ্রমিক কৃষক সম্পদের ভাণ্ডার তৈরি করে অথচ তারাই থেকে যায় নানান দিক থেকে বঞ্চিত। তার ঘরে জোটে না পেটের খাবার, কেঁদে মরে ক্ষুধার্ত শিশু। জোটে না মাথা গাঁজার ঠাঁই, অসুখে পায় না সামান্য চিকিৎসা। নেই কোনো জীবনের নিশ্চয়তা, নারী যেন ভোগ্য পণ্য বিবেচিত হয়। তেমন চিরন্তন বঞ্চনার চিত্র ফুটে উঠেছে ‘প্রিয়তমাসু’ কবিতায়।
"কারা যেন আজ দুহাতে খুলেছে, ভেঙেছে খিল/ মিছিলে আমরা নিমগ্ন তাই, দোলে মিছিল।" সুকান্তের এমন অসংখ্য লেখা আমাদের সাম্যের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে।
কলকাতা কে নিয়ে কবির ছিল অনেক স্বপ্ন, অনুরাগ, ভালোবাসা। তিনি বলতেন কলকাতা আমার প্রেয়সী, সময়ের সাথী। তাঁর জীবন প্রবাহ, কর্মধারা ছড়িয়ে আছে কলকাতার অলিতে গলিতে। তিনি কলকাতাকে নিয়ে বাঁচতে চাইতেন। কবি বিশ্বাস করতেন এদেশে একদিন স্বাধীনতা আসবেই। তাই তাঁর কণ্ঠে উজ্জীবিত হতো তারুণ্যের জয়গান কৈশোরের জয়গান।
তিনি ভালো লেখকই শুধু ছিলেন না, তিনি ভালো পাঠকও বটে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর অনুরাগী ছিলেন তিনি । একবার মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্ত স্থাপনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখবর জানামাত্রই তিনি চলে যান সেখানে কবি গুরুকে দর্শন করতে। পরে তিনি তার লেখায় ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ অসাধারণ মূল্যায়ন করেন, যা আমাদের সবাইকে মুগ্ধ উজ্জীবিত করে। ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি চরণ সেই কবিতায় উদ্ধৃতি আকারে প্রয়োগ করেন তিনি। কিশোর কবির সুমহান চিন্তা একমাত্র মনীষীদের মধ্যে দেখা যায় । তিনি অল্পদিনের জীবনকালে তিনি দেশকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন। যার ঋণ বাঙালি কখনো শোধ করতে পারবে না।
কুড়ি বছর বয়সে কবি প্রথমে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন, তারপর সেরে উঠলে মারণ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি যাদবপুর টিবি হাসপাতালে ভর্তি হন। তার লেখা শেষ কবিতার বই ‘ছাড়পত্র’ তখন ছাপা হচ্ছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছাপা অক্ষরে ওই বই আর দেখে যেতে পারেননি। ১৯৪৭ সালের ১৩ মে মাত্র ২১ বছর বয়সে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য অমৃতলোকে যাত্রা করেন। আর বাঙালির জন্য রেখে যান বিপ্লবের প্রেরণা, সাম্যের উৎসাহ বার্তা।
লেখক : কলাম লেখক।
এইচআর/এমএফএ/জিকেএস

 1 month ago
20
1 month ago
20



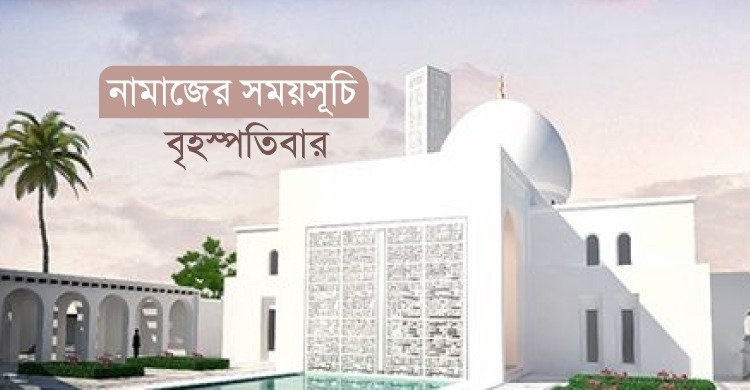
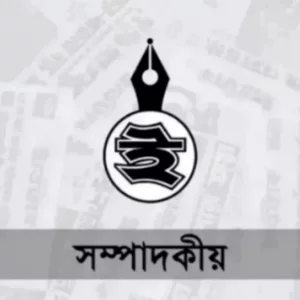




 English (US) ·
English (US) ·