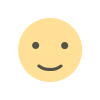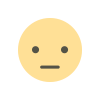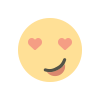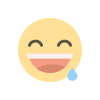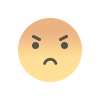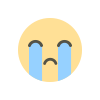ভূমিকম্প ট্রমা ও উদ্বেগ : অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবিলায় উদ্যোগ চাই
ভূমিকম্পকে আমরা সাধারণত একটি নির্ভেজাল ভূতাত্ত্বিক ঘটনা হিসেবেই শ্রেণিবদ্ধ করি। কিন্তু এর সবচেয়ে গভীর, দীর্ঘস্থায়ী এবং অদৃশ্য ক্ষত সৃষ্টি হয় মানুষের সামাজিক ও মানসিক জগতে। মাটির কম্পন যত বড় হয়, সমাজের অভ্যন্তরে তার আঘাত তত বেশি গভীরে প্রবেশ করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ, অবকাঠামোগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এবং অসম নগরায়ণের দেশে ভূমিকম্প কোনো ক্ষণস্থায়ী শারীরিক বিপর্যয়ই নয়; এটি একটি তীব্র সামাজিক মানসিক চাপ, যা মানুষের মন, সম্পর্ক, আচরণ, আস্থা এবং নিরাপত্তাবোধকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। এই মানসিক চাপই প্রকারান্তরে অর্থনীতি এবং উৎপাদনশীলতাকে স্থবির করে দেয়। ২০২৫ সালের ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পের মতো একটি মাঝারি কম্পনও তাই আমাদের সামনে দেশের মনস্তাত্ত্বিক ভঙ্গুরতাকে উন্মোচিত করেছে। ভূমিকম্পের প্রথম আঘাতটি আসে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে, যাকে অস্তিত্বগত অনিরাপত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কয়েক সেকেন্ডের সেই কম্পনের মধ্য দিয়ে মানুষ হঠাৎ উপলব্ধি করে যে তাদের জীবনের ভিত্তি (পৃথিবী) মোটেও স্থিতিশীল বা পূর্বানুমানযোগ্য নয়। এই উপলব্ধি এক ধরনের তীব্র মানসিক চাপজনিত ব্যাধি তৈরি করতে পারে, যা পরবর্তীত
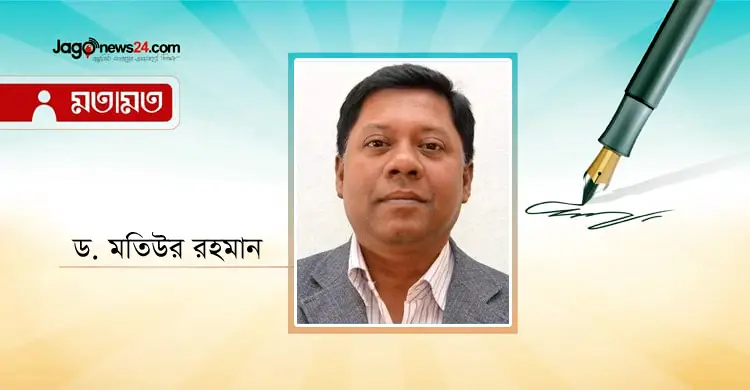
ভূমিকম্পকে আমরা সাধারণত একটি নির্ভেজাল ভূতাত্ত্বিক ঘটনা হিসেবেই শ্রেণিবদ্ধ করি। কিন্তু এর সবচেয়ে গভীর, দীর্ঘস্থায়ী এবং অদৃশ্য ক্ষত সৃষ্টি হয় মানুষের সামাজিক ও মানসিক জগতে। মাটির কম্পন যত বড় হয়, সমাজের অভ্যন্তরে তার আঘাত তত বেশি গভীরে প্রবেশ করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ, অবকাঠামোগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এবং অসম নগরায়ণের দেশে ভূমিকম্প কোনো ক্ষণস্থায়ী শারীরিক বিপর্যয়ই নয়; এটি একটি তীব্র সামাজিক মানসিক চাপ, যা মানুষের মন, সম্পর্ক, আচরণ, আস্থা এবং নিরাপত্তাবোধকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। এই মানসিক চাপই প্রকারান্তরে অর্থনীতি এবং উৎপাদনশীলতাকে স্থবির করে দেয়।
২০২৫ সালের ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পের মতো একটি মাঝারি কম্পনও তাই আমাদের সামনে দেশের মনস্তাত্ত্বিক ভঙ্গুরতাকে উন্মোচিত করেছে। ভূমিকম্পের প্রথম আঘাতটি আসে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে, যাকে অস্তিত্বগত অনিরাপত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কয়েক সেকেন্ডের সেই কম্পনের মধ্য দিয়ে মানুষ হঠাৎ উপলব্ধি করে যে তাদের জীবনের ভিত্তি (পৃথিবী) মোটেও স্থিতিশীল বা পূর্বানুমানযোগ্য নয়। এই উপলব্ধি এক ধরনের তীব্র মানসিক চাপজনিত ব্যাধি তৈরি করতে পারে, যা পরবর্তীতে পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বা পিটিএসডি-এর দিকে পরিচালিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে।
ঢাকার মতো শহরে যেখানে মানুষ প্রতিদিন ফাটলধরা দেয়াল, সংকীর্ণ সিঁড়ি, অবরুদ্ধ অগ্নিনির্বাপক পথ এবং অনুমোদনহীন বহু-তলা ভবনের মধ্যে জীবন কাটায়, সেখানে ভয়ের ভিত্তি শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয়, বাস্তব। এই বাস্তব ঝুঁকি মানুষের মধ্যে জন্ম দেয় অসহায়তা-বোধের। এই অসহায়তা-বোধ হলো এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যেখানে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের কিছু করার নেই, কারণ কর্তৃপক্ষ এবং অবকাঠামো নির্ভরযোগ্য নয়।
বাংলাদেশের মহানগরীগুলোর ভঙ্গুরতা এই মানসিক চাপকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট বা খুলনা—সব শহরই দ্রুত নগরায়ণের ফলে হয়ে উঠেছে এক 'গ্রহীয় নগরীয় অনিশ্চয়তা' কেন্দ্র। এই নগর অবস্থা যেখানে জনঘনত্ব, অব্যবস্থিত গঠন, সেবাদান ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং মৌলিক অবকাঠামোর ওপর চাপ বিদ্যমান। এই দুর্বলতা যে-কোনো ছোট কম্পনকেও ভয়ংকর বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় পরিণত করে।
ভূমিকম্পের মানসিক প্রভাব তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই হতে পারে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ভয়, আতঙ্ক, দ্রুত হৃৎস্পন্দন এবং বিভ্রান্তি। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষণগুলি সাধারণত বিলম্বে প্রকাশ পায়, যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে।
ভূমিকম্প-পরবর্তী অনিদ্রা এবং দুঃস্বপ্ন একটি সাধারণ লক্ষণ, যা দিনের বেলায় কর্মদক্ষতাকে মারাত্মকভাবে হ্রাস করে। সামান্য শব্দ, হঠাৎ ঝাঁকুনি বা উচ্চ ভবনে থাকা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়। এটি মানুষের গতিশীলতা এবং কাজের সুযোগ সীমিত করে দেয়।
বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা একটাই—প্রতিরোধ শুরু করতে হবে এখনই। ভবনের পাশাপাশি মনের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত না হলে কোনো শহরই সত্যিকারের নিরাপদ নয়। মানসিক স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ শুধু মানবিক দিক থেকে জরুরি নয়, এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত।
ট্রমা-পরবর্তী সময়ে মনোসংযোগে সমস্যা দেখা দেয়, যা পেশাগত কাজে ভুলের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। অনেক সময় মানসিক চাপ শারীরিক লক্ষণে রূপান্তরিত হয়, যেমন—মাথাব্যথা, হজমের সমস্যা, বা দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, যার ফলে কাজের অনুপস্থিতি বাড়ে।
তুরস্ক, জাপান বা নেপালের মতো দেশগুলোতে দেখা গেছে যে এসব লক্ষণ কয়েক মাস পর চূড়ায় পৌঁছায়। বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এত বড় চাপ সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। বিশেষজ্ঞের সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল, পরিষেবা সীমিত, আর সামাজিক কলঙ্ক মানুষকে চিকিৎসা নিতে নিরুৎসাহিত করে।
ভূমিকম্পের মানসিক আঘাত সমাজে সমানভাবে অনভূত হয় না। বিশেষ করে প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং নির্ভরশীল মানুষের ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বয়স্ক মানুষরা দ্রুত বের হতে পারেন না, সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, ফলে তাদের চাপ দ্বিগুণ হয়। অনেকেই চলাফেরা করতে পারেন না বা দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভোগেন। পুরোনো দুর্যোগের স্মৃতি নতুন কম্পনে আবার ফিরে আসে। একাকীত্ব, নির্ভরতা এবং উদ্ধার ব্যবস্থার ওপর অনাস্থা তাদের উদ্বেগকে দীর্ঘস্থায়ী করে।
অসুস্থ মানুষ, বিশেষ করে যারা জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা (যেমন : অক্সিজেন, ডায়ালাইসিস) বা নিয়মিত চিকিৎসার ওপর নির্ভর করেন, তারা অবকাঠামোর দুর্বলতার কারণে অতিরিক্ত মানসিক চাপ অনুভব করেন। হাসপাতালগুলোও যদি নিরাপদ না হয়, তবে রোগী ও তাদের পরিবারের আতঙ্ক বহুগুণ বেড়ে যায়।
স্কুল বা আবাসিক ভবনে শিশুরা থাকে আতঙ্কের মধ্যে। ভবন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া বা হুড়োহুড়িতে আহত শিক্ষার্থীদের ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে স্কুলগুলোতে ভূমিকম্পের মহড়া এবং মৌলিক সুরক্ষা পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে আতঙ্ক আরও দ্রুত সংক্রমিত হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের নির্দেশনার অভাব তাদের বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়।
পোশাক শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকেরা (যাদের অধিকাংশই নারী) আতঙ্কের সময় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। তাদের ট্রমা ব্যক্তিগত নয়, বরং শ্রেণিভিত্তিক—নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব তাদের মানসিক দুর্বলতাকে আরও গভীর করে।
গার্মেন্টসসহ বহু-তলা কারখানার শ্রমিকরা মানসিক চাপের ভিন্ন বাস্তবতা বহন করেন। অতীতে রানা প্লাজার মতো দুর্ঘটনার স্মৃতি তাদের মানসিক গঠনে 'সামষ্টিক স্মৃতি' হিসেবে স্থায়ী দাগ রেখেছে। সামান্য দুলুনিও বিশাল আতঙ্ক তৈরি করে, যার ফলে হুড়োহুড়ি বা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। শ্রমিকদের এই ট্রমা সরাসরি উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে।
মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে শুধু মানবিক সমস্যা হিসেবে না দেখে, এর বিশাল অর্থনৈতিক মূল্য বিবেচনা করা আবশ্যক। এই আর্থিক ক্ষতির মাত্রা বোঝা জরুরি। ট্রমা এবং উদ্বেগের কারণে কর্মীরা 'উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত' থাকে। অর্থাৎ, তারা কর্মস্থলে উপস্থিত থাকলেও মনঃসংযোগে ঘাটতি এবং অস্থিরতার কারণে তাদের দক্ষতা কমে যায়, যা সরাসরি আউটপুট হ্রাস করে।
ট্রমা-সংক্রান্ত শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে কর্মীদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি বাড়ে, যার ফলে উৎপাদন লাইনে বিঘ্ন ঘটে। আতঙ্ক ও ট্রমার কারণে চিকিৎসা ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা খাতে সরকারের এবং ব্যক্তিগত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অবকাঠামোগত এবং মানসিক ভঙ্গুরতা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করে।
রিয়েল এস্টেট খাতে ভবনগুলোর ফাটল দেখা দিলে সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায়, যা সামগ্রিক আর্থিক বাজারে অস্থিরতা তৈরি করে। ভূমিকম্পের পর কেবল কংক্রিট পুনর্নির্মাণের খরচই নয়, কয়েক বছর ধরে ট্রমা মোকাবেলায় সামাজিক সহায়তা এবং চিকিৎসা প্রদানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বাজেট প্রয়োজন হয়।
বাংলাদেশের মতো দেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষজ্ঞের সংখ্যা (মনোচিকিৎসক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট) জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম, এবং এই পরিষেবা মূলত শহরকেন্দ্রিক। দুর্যোগের সময় এই দুর্বলতা চূড়ান্ত সংকটে রূপ নেয়।
এই সংকট মোকাবেলায় একটি সমন্বিত মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া মডেল প্রয়োজন।
প্রথমত, তাৎক্ষণিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগের পরপরই ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে প্রাথমিক মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান করা আবশ্যক। এই কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবী এবং সরকারি কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা জরুরি।
দ্বিতীয়ত, মধ্যমেয়াদী ট্রমা কাউন্সেলিং প্রয়োজন। স্কুল, কারখানা এবং কমিউনিটি কেন্দ্রগুলিতে ট্রমা-কাউন্সেলিং ইউনিট স্থাপন করা উচিত। এটি ট্রমার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে (যেমন পিটিএসডি) গুরুতর হওয়ার আগেই মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।
তৃতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সংহতি প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করতে হবে এবং সামাজিক কলঙ্ক দূর করার জন্য ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
নগর পরিকল্পনায়ও পরিবর্তন জরুরি। প্রতিদিনের মানসিক চাপ যদি বেশি হয়, তখন দুর্যোগের চাপ বহুগুণ বেড়ে যায়। ঢাকার শব্দদূষণ, যানজট, ভিড়, সবুজের অভাব—এসবই নাগরিকদের মানসিক স্থিতি কমিয়ে দেয়।
তাই নিরাপদ ও মানসিকভাবে স্থিতিশীল নগর তৈরি করতে হবে। পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, হাঁটার পথ, সুশৃঙ্খল জোনিং—এগুলো মানুষের মানসিক সহনশীলতার শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে। নগর স্থপতিদের অবশ্যই 'মনের স্থিতিস্থাপকতা'কে তাদের নকশার কেন্দ্রে রাখতে হবে।
ভূমিকম্প শুধু ভবনের শক্তি নয়, সমাজের শক্তিকেও পরীক্ষা করে। আমরা কীভাবে আমাদের প্রবীণ, অসুস্থ, শিশু, শ্রমিক, নগরবাসী এবং দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াই—সেই পরীক্ষাতেই নির্ধারিত হবে আমাদের প্রকৃত প্রস্তুতি।
বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা একটাই—প্রতিরোধ শুরু করতে হবে এখনই। ভবনের পাশাপাশি মনের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত না হলে কোনো শহরই সত্যিকারের নিরাপদ নয়। মানসিক স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ শুধু মানবিক দিক থেকে জরুরি নয়, এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত।
লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী।
এইচআর/জেআইএম
What's Your Reaction?