ডেনমার্কের যুবরাজ ছাড়া যেমন হেমলেট নাটক কল্পনা করা যায় না, তেমনি অর্থনীতি জন মেইনার্ড কেইনসকে (১৮৮৩-১৯৪৬) বাদ দিয়ে সরকারি ব্যয়ের আলোচনা অনেকটা অর্থহীন। খুব সম্ভবত কেইনস ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো অর্থনীতিবিদ তার নীতি উপদেশ দিয়ে রাজনীতিবিদদের ওপর অত প্রবল প্রভাব ফেলেছেন বলে জানা নেই। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, ‘কেইনস সবচাইতে তীক্ষ্ণ এবং পরিষ্কার বোদ্ধা। যখন তার সাথে (কেইনসের সাথে) যুক্তি প্রদর্শন করতাম মনে হতো যেন জীবনটা আমি হাতে নিয়েছি এবং প্রায়ই নিজেকে বোকা ঠাহর করে বের হতাম।’
ত্রিশ শতকের মহামন্দা কাটিয়ে ওঠার পথ খুঁজতে যখন বিশ্বের সেরা সেরা মাথাগুলো মহাব্যস্ত, তখন ব্রিটেনের ট্রেজারি (অর্থ মন্ত্রণালয়) ধৈর্য ধরার সুপারিশ এবং আশ্বস্ত করেছিল যে দীর্ঘমেয়াদে সব ঠিক হয়ে যাবে। এ কথা শুনে কেইনস ক্ষেপে গিয়ে বলছিলেন, দীর্ঘমেয়াদে আমরা সবাই মৃত। সুতরাং যা করতে হবে স্বল্পমেয়াদে করতে হবে। কেইনসের ক্যাপসুল ফরমুলা এলো সরকারি কিংবা বেসরকারি ব্যয় বাড়াও এবং সেটাই হচ্ছে মন্দার বিপক্ষে প্রয়োগ করার মতো মহৌষধ।
এর কারণ খুব সহজেই অনুমেয় অর্থনৈতিক মন্দা তখনই ঘটে যখন পণ্য ও সেবার মোট চাহিদা মোট আয়ের চাইতে কম হয়। কেইনস সাবধান করে দিয়ে খানা ও ব্যবসার অপর্যাপ্ত চাহিদার কথা বলেন। তারা যদি যথেষ্ট ক্রয় না করে, মালিক কর্মচারী ছাঁটাই করে দেবে এবং উৎপাদন হ্রাস করবে। কেইনসীয় মতবাদে সরকারের ভূমিকা খুব বেশি। কর হ্রাস করে অথবা বেশি ব্যয় করে সরকার সরাসরি অর্থনীতির ডুবন্ত জাহাজকে রক্ষা করতে পারে।
এটাই হচ্ছে মন্দার বিপরীতে কেইনসের ক্যাপসুল প্রেসক্রিপশন যদি অপর্যাপ্ত চাহিদার জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের রিশিসন ব্যবধান হয় এবং প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হয় দুই-তৃতীয়াংশ, তখন গুণক হবে ৩। অতএব, ৪ বিলিয়ন ডলারের সরকারি ব্যয় সম্বলিত কর্মসূচি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে এ ব্যবধান ঘোচাতে সাহায্য করবে। কেইনস বলতেন, অর্থনীতিবিদদের দন্তচিকিৎসকের মতো প্রায়োগিক হতে হবে; রোগী নির্বিশেষে একই দাঁত খোঁচালে কজন দন্তচিকিৎসকের হেলানো চেয়ারে হা করে বসে থাকবে?
অর্থনৈতিক মন্দা ও রিশিসনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। মন্দা (ডিপ্রেশন) হচ্ছে সেই অবস্থা যখন অব্যাহতভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে সবকিছুই নিম্নমুখী হয়-অর্থাৎ যখন উৎপাদন, কেনাকাটা, কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে ব্যাপক ধস নামে। আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাময়িক স্থবিরতা (রিশিসন ) হচ্ছে মোট উৎপাদন আয় এবং কর্মসংস্থানে তাৎপর্যপূর্ণ হ্রাস, বিশেষত ৬ মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত, যখন অর্থনীতির অনেক খাতে বহুবিস্তৃত সংকোচন প্রত্যক্ষ করা যায়।
রিশিসন অর্থনৈতিক মন্দারই অপেক্ষাকৃত একটা নমনীয় ধরন, যদিও এটা মন্দার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে । এই পার্থক্য সম্পর্কে সাবেক এবং প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনার্ল্ড রিগানের একটা কৌতুকপূর্ণ কথা আছে। ১৯৮০ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সাথে ভোটযুদ্ধে নেমে তিনি বলেছিলেন, ‘রিশিসন হচ্ছে যখন আপনার প্রতিবেশী তার চাকরি হারায়, আর ডিপ্রেশন হচ্ছে যখন আপনি আপনার চাকরি হারান। রিকভারি হচ্ছে যখন জিমি কার্টার তার চাকরি হারান।’
যাই হোক, পুনরুক্তি যদিও, লর্ড মেইনার্ড কেইনস খুব সংক্ষেপে মন্দার মর্মার্থ তুলে ধরেছেন এভাবে- খানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার অপর্যাপ্ত চাহিদার কারণে ব্যবসায়ী চাকরি থেকে ছাঁটাই করে এবং উৎপাদন কমিয়ে দেয়। যেহেতু খানাগুলো বেশি করে পণ্য কেনে, সামগ্রিক চাহিদা সম্প্রসারণে খানার ভূমিকা বেশ বড় থাকে। একটা খানা কতটুকু ব্যয় করবে তা নির্ভর করে খুব তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান পরিবারের আকার, রুচি এবং প্রত্যাশার ওপর।
তবে, আয় হচ্ছে চাহিদার প্রধান চালক আয় বাড়লে খানা বেশি কিনবে, আয় কমলে কম কিনবে। বস্তুত কেইনস ধরে নিয়েছেন যে যখনই কারও হাতে একটা অতিরিক্ত ডলার বা টাকা আসে, সে অতিরিক্ত ডলারের বা টাকার অধিকাংশ খরচ করবে এবং বাকিটা সঞ্চয় করবে। কেইনস এটাকে বলেন প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা। শুধু ভোক্তা কেন, যন্ত্রপাতি ও মজুতে বিনিয়োগ করে ব্যবসায়ী মহলও সার্বিক চাহিদায় অবদান রাখে।
বিনিয়োগ নির্ভর করে মূলত প্রত্যাশা, সুদের হার, আস্থা, আবহাওয়া এবং রাজনীতি- এ সবকিছুর ওপর। মোট কথা, পূর্ণ কর্মসংস্থান সমেত একটা শক্তিশালী অর্থনীতি পেতে হলে খানাগুলো যথেষ্ট ভোগ ব্যয় করতে হবে এবং একই সাথে ব্যবসায়ী মহল পণ্য বিক্রিতে যথেষ্ট বিনিয়োগ করতে হবে, যাতে বিক্রির পরিমাণ উৎপাদনের সমান হয়। অতএব, কেইনসীয় অর্থনীতি তত্ত্বে বা কেইনসীয় মতবাদের দুটো মৌলিক উপাদান হচ্ছে- ক. ব্যক্তি অর্থনীতি পূর্ণ কর্মসংস্থানের নাও পৌঁছাতে পারে এবং খ. সরকারি ব্যয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে এ ব্যবধান দূর করতে পারে।
ব্যক্তির ব্যয় কীভাবে অর্থনীতি ব্যাধিমুক্ত করে? নিজের ব্যয় নিজের জন্য, সরকারি ব্যয় সবার জন্য। ব্যয়ের একটা অর্থনীতি তো আছেই এবং সেজন্যই প্রতি বছর সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। সরকারি ব্যয় অর্থনৈতিক্র প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে বেশ বড় ভূমিকা রাখে যেমন, রাস্তাঘাট, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ মালামাল পরিবহনে সুযোগ করে দেয়; বিদ্যুৎ প্লান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ঘটিয়ে উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব হয়; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় মানুষের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করত মানবপুঁজি সংঘটনে সহায়তা দেয়।
অন্যদিকে, আছে দেশ রক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা, সিভিল প্রশাসন, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে ব্যয় যে সব কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিখাত নানান কারণে খুব একটা এগিয়ে আসে না বলে সরকারকে ব্যয় বৃদ্ধির দায়িত্ব নিতে হয়। বলা দরকার যে এ সব ব্যয় সাধারণত তাৎক্ষণিক কোনো উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটায় না, তবে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোর প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।
যদি কোনো ব্যক্তি বা খানা তার সবটুকু আয় খরচ করে ফেলে সেক্ষেত্রে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান হবে ১. অর্থাৎ, ১ টাকার অতিরিক্ত আয় সমান ১ টাকার অতিরিক্ত ব্যয়। ধরা যাক যে ‘ফ্রেন্ডস’ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস কোং’ কোম্পানি কারখানায় একটা অতিরিক্ত রুম বানাতে গিয়ে ১০০ ডলার খরচ করলো। তাহলে মোট ব্যয় বাড়লো ১০০ ডলার। মিস্ত্রি, নকশাবিদ ও অন্যান্য রসদ ক্রয়ের পেছনে।
প্রশ্ন হলো, যাদের কাছে ১০০ ডলার গেলো তারা বাড়িতে এসে ওই ডলার দিয়ে কী করে? নিশ্চয়ই কিছু না কিছু কেনাকাটা করে এবং বাকিটা সঞ্চয় করে। যারা এ দ্রব্যগুলো বিক্রি করে তাদের আয় বেড়ে যায় এবং তারাও অতিরিক্ত আয় দিয়ে নানান কাজে ব্যয় করে। এমনিভাবে যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ০.৬৬ হয় অর্থাৎ, ১ টাকার আয় বাড়লে ৬৬ পয়সা খরচ হয় তাহলে প্রাথমিক ১০০ ডলারের খরচ সমগ্র অর্থনীতিতে মোট আয় বৃদ্ধি ঘটায় ৩০০ ডলারের-অর্থাৎ, অর্থগুণক ৩। (গুণক = ১/ [১- প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ] অথবা, (১/প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা )।
বুঝতে কষ্ট হয় না যে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা যত বেশি হবে গুণক তত বেশি হবে আর প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণত যত বেশি হবে গুণক তত কম হবে। এই সূত্র ধরে যে কারণেই হোক বিনিয়োগ একটু কমলেই মানুষের আয় কমে যাবে, চাহিদা হ্রাস পাবে এবং অর্থনীতিতে বিরাট চাপ সৃষ্টি হবে। যদি মানুষ অতিরিক্ত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ সঞ্চয় করে (তার মানে দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় করে) তাহলে গুণক হবে ৩। আর সেক্ষেত্রে যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশের সরকার ৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ হ্রাস করে, তাহলে জাতীয় আয় কমে যাবে ১৫ কোটি টাকার।
সুতরাং, চাহিদার ঘাটতি যদি সাময়িক অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণ হয়, তাহলে এই রোগের ওষুধ হলো সরকারি বা বেসরকারি ব্যয় বাড়ানো। এমনিভাবে, যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা দেওয়া থাকে, তাহলে গুণক সম্পর্কে ধারণা নিয়ে কত টাকা অর্থনীতিতে ঢাললে উৎপাদন ও বিক্রির ঘাটতি পূরণ হবে তাও জানা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষত সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকার পালন করতে পারে।
ধরা যাক যে, বাংলাদেশে চাহিদা ঘাটতি ১২ কোটি টাকার পরিমাণ স্থবিরতা জন্ম দেয় এবং এই দেশে হিসাবকৃত প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা দুই-তৃতীয়াংশ। তাহলে অর্থগুণক হবে ৩ এবং যার মানে ৪ কোটি টাকার সরকারি ব্যয় কর্মসূচি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে ওই ব্যবধান ঘোচাতে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং, এটা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয় যে মন্দা বা রিশিসনের সময় সরকার নানান উপায়ে- সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতির ওপর ভর করে।
লেখক : অর্থনীতিবিদ, কলামিস্ট। সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
এইচআর/এমএফএ/এমএস

 1 month ago
8
1 month ago
8





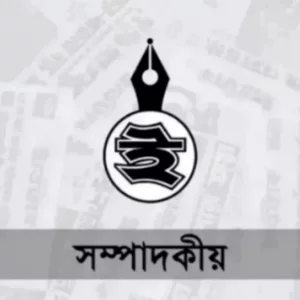



 English (US) ·
English (US) ·