সিরাজুল আলম খানের দুটি বই পড়ছেন বলে জানিয়েছেন লেখক ও চিন্তক ফরহাদ মজহার। ১৩ আগস্ট দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে তিনি এক লেখায় এ কথা জানান। লেখাটি জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো:
‘আমি সিরাজুল আলম খানের দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পড়ছি। একটি ‘দ্বিতীয় ধারার রাজনীতি’ এবং দ্বিতীয়টি ‘বাংলাদেশে গণতন্ত্র’। জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে যে দুইজন গণনায়ক ও গণঅভ্যুত্থানের কারিগরের কাছে বারবার ফিরে যেতে হবে এবং সবক নিতে হবে; সেই দুইজন হচ্ছেন, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং সিরাজুল আলম খান। বলাবাহুল্য, আমাদের বিপ্লবী ঐতিহ্যের মহান নায়কদের কাউকেই আমরা ভুলে যেতে পারি না। ফলে আবদুল হক, আবদুল মতিন, সিরাজ সিকদারসহ সকলকেই আমাদের জানতে ও বুঝতে হবে। আমরা যদি অতীতের ভুল এড়াতে চাই, তাহলে আমাদের পাঠ ও পর্যালোচনার এন্টেনাকে শার্প রাখতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না আমরা ইতিহাসের সন্তান।
মওলানা ভাসানী নিয়ে আমরা কম-বেশি আলোচনা করি। কিন্তু সিরাজুল আলম খান নিয়ে আমাদের আলোচনা ও পর্যালোচনা খুবই কম। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন এবং আগামী দিনে যাঁরা আমাদের পেছনের ইতিহাসের সফলতা-ব্যর্থতা-সীমাবদ্ধতার আলোকে নতুন গণরাজনৈতিক ধারা গড়ে তুলবেন; তাদের জন্য সিরাজুল আলম খান অতি অবশ্যই পাঠ্য। কীভাবে তাঁকে আমরা জানবো, পড়বো এবং বুঝবো সে সকল বিষয় নিয়ে আমরা আলাদা আলোচনা করবো। আপাতত এটি একটি নোক্তা।
ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শক্তির আগমন ঘটে ‘সুবেহ বাংলা’র পতনের মধ্য দিয়ে; পলাশীর আম্রকাননের যুদ্ধে সিরাজ উদ্দৌল্লার পতন ছিল সেই ঐতিহাসিক পরাজয়ের মুহূর্ত। তাহলে এই ভূগোলে উপনিবেশ বিরোধী লড়াই শুরু হয়েছে পলাশীর আম্রকাননে। ‘সুবেহ বাংলা’র সেই অবিস্মরণীয় পরাজয়ের ক্ষত ধারণ করে সিরাজুল আলম খানের জাতিবাদী ও শ্রেণি রাজনীতির চিন্তা গড়ে ওঠে। তিনি ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসুর অনুসারী। সিরাজুল আলম খানের রাজনীতির নির্ধারক মর্ম শুধু ঔপনিবেশিক শক্তিকে বিতাড়িত করার মধ্যে নিহিত ছিল না বরং তিনি ছিলেন আরও বিস্তৃত ও গভীর। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার মানচিত্র ইংরেজের কলমের খোঁচা দিয়ে তৈরি নয়। তাঁর ‘বাংলা’ সুবেহ বাংলার মতোই আরও বৃহৎ পরিসরের স্বাধীন বাংলা।
স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি যে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছেন তার উদ্দেশ্য পাঠ করলেই খানকে সহজেই বোঝার সূত্র পাওয়া যায়। সংগঠনের উদ্দেশ্য হিসাবে তিনি লিখেছেন: “আভ্যন্তরীণ পরাধীনতা’ মুক্ত রাষ্ট্রীয়-রাজনীতির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করা”–এটাই তাঁর উদ্দেশ্য। (দেখুন ‘দ্বিতীয় ধারার রাজনীতি’)। তিনি ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ‘জাতীয় ঐক্য’ চান। সোজা কথায় এমন এক গণরাজনৈতিক ধারার তিনি জন্ম দিতে চান, যে ধারা ঔপনিবেশিক পরাধীনতা ও শাসনের ফলে সৃষ্ট মন-মানসিকতা, সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক নিগড় থেকে আমাদের যেমন মুক্ত করবে; তেমনই পুঁজিতান্ত্রিক গোলকায়নের রূপ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান রূপকে চ্যালেঞ্জ করে বিশ্বসভায় নিজেদের শক্তিশালী আসন নিশ্চিত করবে। কারণ তিনি যে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা ‘আভ্যন্তরীণ পরাধীনতা”–অর্থাৎ ঔপনিবেশিক চিন্তা চেতনা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধত্ব থেকে মুক্ত। এই দিকটি বুঝলে তিনি কেন ‘অংশীদারত্বের গণতন্ত্র’ কথাটা জোরেসোরে তুলে ধরেছিলেন তার মর্মও আমরা বুঝবো।
তাঁর ‘বাংলাদেশে গণতন্ত্র’ পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন, “আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপকে অনুমোদন (সমর্থন বা বিরোধিতা উভয় অর্থে) করাকে ‘গণতন্ত্রে’র কোনো সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। গণতন্ত্র হতে হবে অংশীদারত্ব ভিত্তিক। রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি সামাজিক শক্তিসমূহের অংশীদারত্বের স্বীকৃতি এবং এর ভিত্তিতে গড়ে তোলা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কাঠামোই হলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ‘অংশীদারত্বের গণতন্ত্র’। বাংলাদেশের সমাজশক্তির বিন্যাস, মানুষের সামগ্রিক চাওয়া-পাওয়া এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ‘অংশীদারত্বের গণতন্ত্র’কে আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন কাঠামোয় প্রয়োগ করতে হবে।”
কীভাবে তিনি এই ‘অংশীদারত্বের গণতন্ত্র’ কায়েম করবেন, তার একটি পরিচ্ছন্ন রূপরেখা তিনি ‘বাংলাদেশে গণতন্ত্র’ পুস্তিকায় পেশ করেছেন।
ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে শুধু বাহ্যিক স্বাধীনতা লাভ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। সাদা সাহেবদের তাড়িয়ে স্যুট-টাই পরা বাদামি সাহেবদের শাসন তিনি চাননি। (বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের কথা ভাবুন)। এমনকি এমন কোনো ‘বাঙালি জাতি’ তিনি চাননি; যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য চিন্তার প্রতি অন্ধ। উপমহাদেশ থেকে ইসলাম নির্মূলের যে রাজনীতি ভারতে হিন্দুত্ববাদ এবং বাংলাদেশে বাকশাল ও শেখ হাসিনার ‘বাঙালি জাতিবাদ’র নামে চর্চা করা হয়েছে, তিনি তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শেখ মুজিবরের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের এটাই প্রধান কারণ। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি ‘জাতীয় সরকার’ চেয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাব শেখ মুজিব অগ্রাহ্য করায় উভয়ের মধ্যে যে ছেদ ঘটেছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তার প্রভাব হয়েছে সুদূর প্রসারী।
আমরা যেন অতীত থেকে শিখি এবং গ্যাজেট জেনারেশান বা জি-জেনারেশনের মতো নিজেদের অতি পণ্ডিত না ভাবি।’
এসইউ/জিকেএস

 1 month ago
11
1 month ago
11






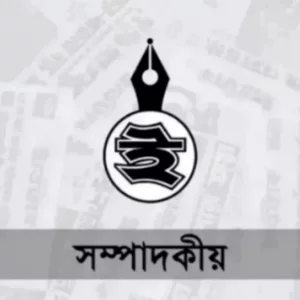


 English (US) ·
English (US) ·