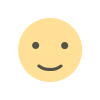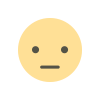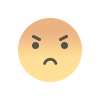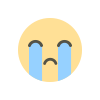রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস বাস্তবায়ন কতদূর?
কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের পাহাড়ঘেরা রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির। ধুলোবালি মাখা পরিবেশে যখন জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস একত্রে ইফতারের টেবিলে বসলেন, তখন তা কেবল একটি মানবিক অনুষ্ঠান ছিল না। এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রতি এক বিশাল কূটনৈতিক বার্তা। আজ এমন এক সময়ে আমরা এই সংকটের উত্তর খুঁজছি, যখন বৈশ্বিক রাজনীতির মনোযোগ ইউক্রেন আর গাজার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিবদ্ধ। আছে পাক-ভারত-চীন, সাথে সম্প্রতি যোগ হয়েছে ভেনেজুয়েলা প্রসঙ্গ। ফলে রোহিঙ্গা ইস্যুটি অনেকটা ‘বিস্মৃত ট্র্যাজেডি’ হিসেবে আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারের তলায় হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এটি কোনো বিলাসিতা নয়, বরং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য এক বিশাল টাইমবোম। এখন আলোচনায় টানতে হয়- রোহিঙ্গারা কী কেবলই আশ্রিত এক উদ্বাস্তু গোষ্ঠী? ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, তাদের আত্মপরিচয় অত্যন্ত গভীর ও সুপ্রাচীন। অষ্টম শতাব্দী থেকে আরব, পারস্য ও মুর বণিকদের হাত ধরে আরাকানের উপকূলে যে বসতি স্থাপিত হয়েছিল, তা থেকে আজকের এই রোহিঙ্গা জাতিসত্তার বিকাশ। তারা

কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের পাহাড়ঘেরা রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির। ধুলোবালি মাখা পরিবেশে যখন জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস একত্রে ইফতারের টেবিলে বসলেন, তখন তা কেবল একটি মানবিক অনুষ্ঠান ছিল না। এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রতি এক বিশাল কূটনৈতিক বার্তা।
আজ এমন এক সময়ে আমরা এই সংকটের উত্তর খুঁজছি, যখন বৈশ্বিক রাজনীতির মনোযোগ ইউক্রেন আর গাজার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিবদ্ধ। আছে পাক-ভারত-চীন, সাথে সম্প্রতি যোগ হয়েছে ভেনেজুয়েলা প্রসঙ্গ। ফলে রোহিঙ্গা ইস্যুটি অনেকটা ‘বিস্মৃত ট্র্যাজেডি’ হিসেবে আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারের তলায় হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এটি কোনো বিলাসিতা নয়, বরং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য এক বিশাল টাইমবোম।
এখন আলোচনায় টানতে হয়- রোহিঙ্গারা কী কেবলই আশ্রিত এক উদ্বাস্তু গোষ্ঠী? ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, তাদের আত্মপরিচয় অত্যন্ত গভীর ও সুপ্রাচীন। অষ্টম শতাব্দী থেকে আরব, পারস্য ও মুর বণিকদের হাত ধরে আরাকানের উপকূলে যে বসতি স্থাপিত হয়েছিল, তা থেকে আজকের এই রোহিঙ্গা জাতিসত্তার বিকাশ। তারা মিয়ানমারের মাটিতে কোনো ‘বহিরাগত’ বা ‘বাঙালি অনুপ্রবেশকারী’ নয়, বরং তারা ওই ভূমিরই ভূমিপুত্র।
আরাকানের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ছিল ১৪৩০ থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত। ম্রাউক-ইউ বংশের শাসনের সময় আরাকান ছিল একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। রাজা নারামেইখলা বা সোলাইমান শাহ্-এর আমল থেকে শুরু করে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আরাকান ছিল এক অনন্য সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। সেখানে বৌদ্ধ রাজারা মুসলিম নাম গ্রহণ করতেন এবং রাজদরবারে বাংলা ও ফারসি সাহিত্যের চর্চা হতো। মহাকবি আলাওল বা মাগন ঠাকুরের মতো প্রতিভারা এই আরাকান রাজদরবারেরই অলংকার ছিলেন।
১৯৪৮ সালে মিয়ানমার যখন ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, তখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী উ নু রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের অন্যতম ‘আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী’ (Indigenous Ethnic Group) হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের পার্লামেন্টে নির্বাচিত সদস্য তথা এমপি, মন্ত্রী ও সরকারি উচ্চপদে আসীন ছিলেন। অর্থাৎ, যে জনগোষ্ঠীকে আজ ‘রাষ্ট্রহীন’ বলা হচ্ছে, তারা কয়েক দশক আগেও একটি রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন। জাতিসত্তার এই দীর্ঘ ইতিহাসই প্রমাণ করে যে, তাদের অধিকার কেবল মানবিক নয়, বরং আইনি ও ঐতিহাসিক।
রোহিঙ্গাদের পরাধীনতার ট্র্যাজেডি শুরু হয় ১৭৮৪ সালে। বর্মী রাজা বোডাওপায়া যখন স্বাধীন আরাকান রাজ্য আক্রমণ করে দখল করে নেন, তখন থেকেই এই জনগোষ্ঠীর ওপর শুরু হয় সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক নিপীড়ন। সেই সময় থেকেই আত্মরক্ষার্থে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে (তৎকালীন বঙ্গদেশ) আশ্রয়ের এক নির্মম ঐতিহাসিক ধারা তৈরি হয়।
১৯৪২ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালের সামরিক জান্তার ‘অপারেশন ড্রাগন কিং’ ছিল জাতিগত নিধনের একেকটি ভয়ংকর অধ্যায়। প্রতিবারই মিয়ানমার সেনাবাহিনী একই ছক অনুসরণ করেছে— প্রথমে নাগরিক অধিকার হরণ, তারপর পরিকল্পিত নিধনযজ্ঞ এবং শেষে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া। নাফ নদী আজ কেবল একটি ভৌগোলিক সীমানা নয়, এটি রোহিঙ্গাদের কান্না আর রক্তে ভেজা এক দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী।
কিন্তু এসব ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা নিজেই ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর পরিহাসের শিকার হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, রোহিঙ্গারা ঐতিহাসিকভাবেই মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকারের (নেপিডো) প্রতি অনেক বেশি অনুগত ছিল। তারা কখনোই রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর মতো আলাদা রাষ্ট্র বা বিচ্ছিন্নতাবাদের স্বপ্নে বিভোর হয়নি। বরং তারা বর্মী ফেডারেল কাঠামোর ভেতরেই নিজেদের নাগরিক অধিকার চেয়েছিল। জান্তার জন্য রোহিঙ্গারা ছিল রাখাইন রাজ্যে এক ধরনের ‘বাফার কমিউনিটি’ বা সার্বভৌমত্ব রক্ষার পিলার।
কিন্তু উগ্র বর্মী জাতীয়তাবাদ আর বর্ণবাদী জিঘাংসায় অন্ধ হয়ে জান্তা সেই অনুগত গোষ্ঠীকেই নির্মূল করার আত্মঘাতী পথ বেছে নেয়। রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করে জান্তা মূলত রাখাইন রাজ্যে নিজের পতন নিজেই ত্বরান্বিত করেছে। রোহিঙ্গাদের চলে যাওয়ার ফলে যে বিশাল জনপদ শূন্য হয়ে পড়ে, সেখানে জান্তার কোনো স্থানীয় ‘লয়াল বেস’ বা অনুগত শক্তি অবশিষ্ট থাকেনি। এই শূন্যতা বা ‘পাওয়ার ভ্যাকুয়াম’কে সুচতুরভাবে কাজে লাগিয়েছে আরাকান আর্মি (এএ)। তারা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষকে উসকে দিয়ে জান্তাকে দিয়ে তাদের তাড়াতে বাধ্য করেছে। আর এখন সেই খালি মাঠে জান্তাকেই একের পর এক পরাজিত করে রাখাইনের প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকা দখল করে নিয়েছে। জান্তা আজ নিজের খোঁড়া গর্তে নিজেই পড়েছে।
এদিকে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকারের কৌশলগত ব্যর্থতা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। শেখ হাসিনার সরকার ২০১৭ সালের সেই চরম সংকটের মুহূর্তে, দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় নিরাপত্তার চেয়ে আন্তর্জাতিক ‘ব্র্যান্ডিং’ এবং নিজের ‘ইমেজ’ গড়ার দিকে বেশি মনোযোগী ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর একটি অধরা ‘নোবেল শান্তি পুরস্কার’ পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাকে দিয়ে এমন এক আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত নেওয়ানো, যা আজ রাষ্ট্রকে এক ভয়াবহ দীর্ঘমেয়াদি সংকটে ফেলে দিয়েছে।
সীমান্ত খুলে দিয়ে কয়েক লাখ মানুষকে আশ্রয় দেওয়া হয়তো মানবিকতার দাবি ছিল, কিন্তু তার পরপরই যে শক্তিশালী ‘ডিফেন্সিভ ডিপ্লোম্যাসি’ বা কঠোর কূটনৈতিক অবস্থানের প্রয়োজন ছিল, তা তিনি নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ১৯৭৮ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বা ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার আমলে যেভাবে মিয়ানমারকে শক্ত চাপে ফেলে দ্রুততম সময়ে প্রত্যাবাসন শুরু করা সম্ভব হয়েছিল, ২০১৭ সালে সেই দৃঢ়তা দেখা যায়নি। বরং ‘মাদার অব হিউম্যানিটি’ সাজার নেশায় তিনি সমস্যাটিকে একটি দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। যার খেসারত হিসেবে আজ কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত অঞ্চলে জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এটি কোনো সমাধান নয়, বরং দেশের সার্বভৌমত্বকে এক গভীর অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়া।
অপরদিকে মিয়ানমার আজ আর কোনো অখণ্ড রাষ্ট্র নয়, বরং এটি এখন জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর এক সুবিশাল যুদ্ধক্ষেত্র। মিয়ানমারের প্রশাসনিক মানচিত্রের ৭টি রাজ্য ও ৭টি অঞ্চলের প্রায় প্রতিটিতেই আজ বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। একদিকে জান্তা বাহিনী তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে মরিয়া, অন্যদিকে আরাকান আর্মি, কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মি (কেআইএ) এবং পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের (পিডিএফ) মতো গোষ্ঠীগুলো জান্তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। বিশেষ করে রাখাইনে আরাকান আর্মির উত্থান রোহিঙ্গা সমস্যার সমীকরণকে আরও জটিল করে দিয়েছে। জান্তা বাহিনী সীমান্ত ছেড়ে পালাচ্ছে, আর বিদ্রোহীরা এখন বাংলাদেশের সাথে তাদের সীমান্তের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কার সাথে কথা বলবে? ক্ষয়িষ্ণু জান্তা নাকি উদীয়মান বিদ্রোহী শক্তি? এই দোলাচলই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে। আরাকান আর্মি রাখাইনের মালিক হতে চললেও রোহিঙ্গাদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো জান্তার মতোই বর্ণবাদী, যা একটি টেকসই সমাধানের পথে সবচেয়ে বড় দেয়াল।
রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন আজ আর কেবল ঢাকা-নেপিডো দ্বিপাক্ষিক ইস্যু নয়, এটি এখন একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক দাবার বোর্ড। এই বোর্ডে চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব চাল রয়েছে, যেখানে রোহিঙ্গাদের মানবিক অধিকারের চেয়ে কৌশলগত স্বার্থই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।
চীন বর্তমানে রাখাইন ও মিয়ানমার জান্তার সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিভাবক। রাখাইনের কিয়াকপু (Kyaukpyu) গভীর সমুদ্রবন্দর থেকে চীনের ইউনান পর্যন্ত যে বিলিয়ন ডলারের গ্যাস ও তেলের পাইপলাইন গেছে, তার নিরাপত্তা চীনের এক নম্বর অগ্রাধিকার। চীন চায় স্থিতিশীলতা, কিন্তু তারা চায় না এই অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে পশ্চিমা বা মার্কিন প্রভাব তৈরি হোক। ফলে চীন একদিকে মধ্যস্থতার নাটক করে, অন্যদিকে জাতিসংঘে জান্তার পক্ষে ‘ভেটো’ দিয়ে তাদের রক্ষা করে। চীনের সরাসরি সবুজ সংকেত ব্যতীত মিয়ানমারকে এক ইঞ্চি নড়ানো সম্ভব নয়।
অন্যদিকে, ভারত তার ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ পলিসির অংশ হিসেবে ‘কালাদান মাল্টি-মোডাল প্রজেক্ট’ নিয়ে রাখাইনে সক্রিয়। ভারত একদিকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু দাবি করলেও, রাখাইনে তাদের কৌশলগত বিনিয়োগ রক্ষার জন্য তারা জান্তা এবং বর্তমানে আরাকান আর্মি— উভয়কেই চটাতে চায় না। ভারতের এই ‘নিশপাস’ বা কৌশলগত নীরবতা কার্যত মিয়ানমার জান্তাকে একটি দায়মুক্তির সুযোগ করে দিচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্র ‘বার্মা অ্যাক্ট’-এর মাধ্যমে মিয়ানমারে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বললেও, তাদের মূল লক্ষ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের আধিপত্য কমানো। ফলে রোহিঙ্গা সমস্যা তাদের কাছে মিয়ানমারের জান্তাকে চাপে ফেলার একটি কার্যকর অস্ত্র মাত্র। এই তিন শক্তির সক্রিয় ও আন্তরিক উদ্যোগ ব্যতীত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এক অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।
বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘ মহাসচিবের উপস্থিতিতে গত (২০২৫) রমজানে ইফতার মাহফিল আয়োজন করেন। সেখানে আগামী ঈদ নিজেদের মাটিতে করার প্রস্তুতি নিতে বলেন। কিন্তু আগামী ঈদের আগেই প্রত্যাবাসনের যে আশ্বাস দেন, তখন তিনি সম্ভবত বিশ্ব সম্প্রদায়ের ওপর একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাঠের বাস্তবতা অত্যন্ত কঠোর। প্রথমত, মিয়ানমারে ১৯৮২ সালের যে বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইন রয়েছে, তা বহাল রেখে কোনো রোহিঙ্গা মর্যাদার সাথে ফিরতে রাজি হবে না। দ্বিতীয়ত, রাখাইন এখন একটি সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্র। যেখানে জান্তা ও আরাকান আর্মি একে অপরের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত, সেখানে হাজার হাজার বেসামরিক মানুষকে ফিরিয়ে নেওয়া কতটা নিরাপদ?
তাছাড়া আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও এখন প্রতিকূল। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং গাজা সংকটের কারণে বৈশ্বিক ত্রাণ তহবিলের বড় অংশ সেখানে চলে যাচ্ছে। বিশ্ব মিডিয়ার নজরও এখন আর কক্সবাজারের ক্যাম্পে নেই। এই অবস্থায় প্রধান উপদেষ্টার আশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কেবল কথার ফুলঝুরি নয়, বরং মিয়ানমার এবং আরাকান আর্মির ওপর এক ধরনের ‘স্মার্ট প্রেশার’ বা কঠোর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা প্রয়োজন।
তাহলে রোহিঙ্গা সংকটের শেষ কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এক ‘অপ্রচলিত কূটনীতি’র (Unconventional Diplomacy) মধ্যে। বাংলাদেশকে বুঝতে হবে যে মিয়ানমার জান্তা এখন আর রাখাইনের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রক নয়। ফলে প্রত্যাবাসনের জন্য আমাদের এখন ছায়া সরকার এবং সরাসরি আরাকান আর্মির (এএ) সাথে দরকষাকষির টেবিলে বসতে হবে। একে আমরা বলতে পারি ‘ট্র্যাক-টু ডিপ্লোম্যাসি’।
একইসাথে, রাখাইনের ভেতরে একটি ‘নিরাপদ অঞ্চল’ (Safe Zone) তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াতে হবে, যা জাতিসংঘ বা কোনো তৃতীয় শক্তির অধীনে থাকবে। রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকেও একটি শিক্ষিত ও রাজনৈতিক সচেতন নেতৃত্ব গড়ে তোলা জরুরি, যারা জেনেভা বা নিউ ইয়র্কের টেবিলে নিজেদের অধিকারের কথা নিজেরাই বলতে পারবে।
বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো রোহিঙ্গা ইস্যুটিকে জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে দেখা, কেবল মানবিক বোঝা হিসেবে নয়।
পরিশেষে, রোহিঙ্গা সমস্যা কেবল কক্সবাজারের টেকনাফ বা উখিয়ার সমস্যা নয়। এটি পুরো বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদি সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য এক বিশাল অশনিসংকেত। আপনি যদি আপনার রাজনৈতিক দর্শনের চশমায় দেখেন, তবে বুঝতে পারবেন যে এই সংকট যত দীর্ঘায়িত হবে, আমাদের পার্বত্য অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকাগুলোতে অস্থিরতা তত বাড়বে।
জাতিসংঘ মহাসচিবের উপস্থিতি বা প্রধান উপদেষ্টার আশ্বাস তখনই সার্থক হবে, যখন বিশ্বশক্তিগুলো বুঝতে পারবে যে— রোহিঙ্গা সংকট নিরসন না হলে এই পুরো অঞ্চলটিই উগ্রপন্থা ও অস্থিতিশীলতার আখড়ায় পরিণত হবে। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে একটি টেকসই, মর্যাদাপূর্ণ ও নাগরিকত্বসহ প্রত্যাবাসনই হতে পারে এই ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়ের চূড়ান্ত ইতি।
What's Your Reaction?