জিয়াউদ্দিন লিটন
বাংলা কবিতার পরিসরে যারা গভীর নির্জনে শব্দের সুষমা ও যন্ত্রণার রূপ শোনেন; আমিনুল ইসলাম তাদের একজন নিভৃত সাধক। তিনি শুধু কবি নন—তিনি এক বোধের স্থপতি। যিনি আধুনিকতার কোলাহলে থেকেও নির্মাণ করেন নিস্তব্ধ আত্মকথন। তার কাব্যভাষা, চেতনা ও কাব্যচর্চার ধারা বাংলা সাহিত্যের পরম্পরাকে দিয়েছে এক নব অভিমুখ।
১৯৬৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জে জন্ম নেওয়া সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এ কবি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে পাঠ গ্রহণ করলেও তার প্রকৃত পাঠশালা ছিল সমাজজীবনের অন্তরস্ত স্তর এবং ভাষার অনুভব। তার কবিতায় কখনো নেমে আসে যন্ত্রণার মেঘ, কখনো ওঠে প্রেম ও প্রতীতির ইন্দ্রধনু। আমিনুল ইসলামের কবিতায় রূপক, প্রতীক ও বাস্তবতার দোলাচলে তৈরি হয় এক পরিশীলিত অভিঘাত। তার কবিতায় সময় যেমন অনুপম, তেমনই আত্মজিজ্ঞাসার ছায়াও দীর্ঘ। তার কাব্যে মেলে বাস্তব জীবনের ক্লেদ ও ক্লান্তি, মেলে স্বপ্ন ও সংবেদনার দীপ্তি। একাধারে তিনি প্রেমিক, প্রতিবাদী, দ্রষ্টা এবং ধ্যানী—তার কলমে শব্দ পায় আত্মা, বাক্য পায় নন্দনের নূতন ব্যঞ্জনা। তিনি পেয়েছেন ‘দাগ সাহিত্য পুরস্কার’, ‘বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কার’, ‘আইএফআইসি ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার’, ‘বিন্দু বিসর্গ পদক’সহ প্রায় অর্ধডজনেরও বেশি স্বীকৃতি। তার চেয়েও বড় স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন পাঠকের হৃদয়ে।
অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এ প্রকাশিত হয়েছে আমিনুল ইসলামের ‘লীলাবতীর ঘাট’। এটি কেবল একটি কাব্যগ্রন্থ নয়; এক কাব্যিক ভূগোল, যেখানে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে পাঠক খুঁজে পান আত্মপরিচয়ের দিগন্ত। তার ভাষা শহরের চকমকে নয়, মাটি ছোঁয়া, হৃদয়-দাগ-কাটা এক জীবন্ত স্পন্দন। ‘লীলাবতীর ঘাট’ এক অনন্য কাব্যগ্রন্থ, যেখানে নদীর প্রতীকী ঘাটে বসে কবিজীবন, সময়, প্রেম ও সমাজচেতনার বহুস্তরীয় প্রতিফলন তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষা, রূপক এবং বোধ গভীরভাবে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে, যা পাঠককে টেনে নেয় কাব্যের নিভৃত জগতে। বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় যে কবিতাটি নজর কারলো তার নাম ‘অনুসন্ধান বিজ্ঞপ্তি’। কবিতায় ‘মানুষ’ শব্দটি আজকের সমাজে শুধু একটি বিশেষণ নয় বরং একটি অনুসন্ধানযোগ্য বস্তু। মানুষ কি কেবল দুই পায়ে হাঁটে বলেই মানুষ? না কি মনুষ্যত্বই মানুষকে মানুষ করে? এ প্রশ্নগুলোরই একটি গভীর, অন্তর্দাহমূলক এবং দার্শনিক উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন কবি আমিনুল ইসলাম তার অনবদ্য কবিতাটিতে, যার শিরোনাম—‘অনুসন্ধান বিজ্ঞপ্তি’।
শিরোনামের মাধ্যমেই পাঠককে একটি ঘোর লাগানো দুঃসংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়—মানুষ হারিয়ে গেছে এবং এই খোঁজ—তার শুধু শরীর নয় বরং আত্মার, বিবেকের, বোধের ও মনুষ্যত্বের। কবিতার শুরুতেই কবি বলেন:
‘আমি তো বাড়িয়ে প্রাণ। কই গেল মানুষের জাত।
লোকভারে টলমল এই গ্রহ—একথা কি ভুল?’
এ বাক্য দুটি আমাদের অস্তিত্বের এক গভীর সংকটে দাঁড় করায়। পৃথিবী ‘লোকভারে’ ভারাক্রান্ত হলেও সেখানে ‘মানুষ’ অনুপস্থিত। এ দ্বৈততা আমাদের চেতনাকে নাড়িয়ে দেয়। সভ্যতার বহর বেড়েছে কিন্তু মানবিকতা গেছে কমে। লোকের সংখ্যা আছে কিন্তু জাত নেই—এ এক প্রলেপযুক্ত শূন্যতা। কবিতার সবচেয়ে দার্শনিক স্তবকটি সম্ভবত এটি:
‘মানুষের জামা গায়ে কারা এত ঘোরে দিনরাত?
বস্ত্র বালিকারা বোনে কার জামা হে নক্ষত্রকুল।’
কবি এখানে ‘মানুষের জামা’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করে খুব সূক্ষ্মভাবে সভ্যতার ছদ্মবেশ তুলে ধরেন। আমরা সমাজে যাদের দেখি, তারা কি আদৌ মানুষ? নাকি মানুষের মতো মুখোশধারী? জামা-গায়ে মানবদেহ অথচ মনুষ্যত্ব নেই। বস্ত্রবালিকারা হয়তো জামা বোনে শরীর ঢাকার জন্য, কিন্তু আত্মা উলঙ্গ।
‘হায়েনা কুকুর বাঘ চেনা যায় আগের মতন
নদী তো নদীই আছে অবিকল সেই স্রোত ঢেউ
শোনেনি সুন্দরবন ধর্ষণের সুসভ্য ক্রন্দন’
এ বাক্যে কবি বুঝিয়েছেন প্রকৃতি আর পশুরা তাদের স্বভাব পাল্টায়নি। তারা গণহত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, সাম্রজ্যবাদিতা প্রভৃতি অপরাধের সঙ্গে কোনোদিনও জড়িত ছিল না। এখনো নেই। কিন্তু মানুষ? সে হয়ে উঠেছে পশুর চেয়ে অনেক নিচু। ‘শোনেনি সুন্দরবন ধর্ষণের সুসভ্য ক্রন্দন’ বলতে শুধু পরিবেশ ধ্বংস নয় এক বৃহৎ মূল্যবোধের চিৎকার বুঝিয়েছেন কবি। সভ্যতার নামে ধর্ষিত হচ্ছে বন, নদী, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ—সব। কিন্তু যারা বনে বাস করে—যাদের নাম বন্যপ্রাণী, তারা কিন্তু ধর্ষণের মতো গর্হিত অপকর্ম করে না। এটা করে কেবল সভ্যজীব উপাধিধারী মানুষ। এটি একটি বিরাট স্যাটায়ার বা শ্লেষের চাবুক অপরাধমূলক তৎপরতায় নিয়োজিত মানুষ নামের প্রাণীদের প্রতি। একই কবিতায় বলা হয়েছে:
‘মানুষ কোথাও নেই; তবে তারা গেল কোন দেশে?
শহরে বন্দরে ঠাসা এরা কেউ বন্যপ্রাণী নয়
সকলের পাছা বুক ঢাকা দ্যাখো মানুষের বেশে
অথচ মানুষ নয়, কে জানাবে মূল পরিচয়?’
এর মাধ্যমেই কবি চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছেন। কবি আর কোনো কৌশল নয়, সরাসরি নির্ঘোষ দেন: মানুষ নেই। মানুষের মতো দেখতে, পোশাক পরা, শহর-বন্দরে ছড়ানো এরা কেউ মানুষ নয়। সভ্যতার মুখোশ পড়ে এক আত্মাহীন, নিষ্ঠুর, শোষণমুখী ভোঁতা প্রজাতির জন্ম হয়েছে—যারা না জানে ভালোবাসা, না জানে সহানুভূতি, যাদের মধ্যে না আছে মমতা। কবিতাটি মূলত আধুনিক সময়ের মানবতাবিরোধী সমাজব্যবস্থার এক কঠোর ভাষ্য—যা সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে।
‘অনুসন্ধান বিজ্ঞপ্তি’ কেবল একটি কবিতা নয়, এটি একটি যুগযন্ত্রণার শব্দচিত্র। যেখানে কবি কেবল অনুভব করেননি বরং অনুভব করিয়েছেন—এক নিঃশব্দ বিপর্যয় আমাদের গ্রাস করছে। যেখানে মানুষ নেই, আছে মানুষ নামের একরকম বিবেকহীন ‘ব্র্যান্ডেড জীব’। কবিতাটি আমাদের চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, কাঁপিয়ে দেয়, ভাবিয়ে তোলে এবং সর্বোপরি—সচেতন করে তোলে। সত্যিই, মানুষ কোথায়? আছে কি সে শুধু বিজ্ঞপ্তিতে?
গ্রন্থভুক্ত ‘বাঁশবাগানের চাঁদ’ কবিতাটি একটি রাজনৈতিক ঘ্রাণযুক্ত বার্তা বহন করে। এটি কেবল কাব্যিক প্রশস্তি নয় বরং একটি ইতিহাসনির্ভর ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখিত প্রতিবাদী কাব্য, যেখানে দেশের কোনো ক্রান্তিলগ্নে কোনো নেতার অনন্যসাধারণ ভূমিকার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তবে এ কবিতায় কোনো নেতার নাম নেই। কোনো সময়েরও উল্লেখ করা হয়নি। ‘যাহার জন্য প্রযোজ্য’—এমন একটা পটভূমি তৈরি করে কবিতাটিকে সেখানে বসানো হয়েছে।
‘অন্ধ-শক্তির আগ্রাসনে এলোমেলো হয়ে ওঠে জনপদ’—এ পঙক্তির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে কোনো রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আগমন, যারা কোনো বিশেষ দেশ বা জাতিকে দাবিয়ে রাখতে চায় কিংবা যারা কোনো দেশের গণতান্ত্রিক বাতা-বাঁধন ও মানবিক ভিত্তি ভেঙে দিতে চায়। এখানে কবি একটি পরোক্ষ টানাপোড়েনের ছবি এঁকেছেন, যেখানে ‘অন্ধ শক্তি’ হলো ক্ষমতালোভী, অগণতান্ত্রিক চক্র। আর সেই চক্রের বিরুদ্ধে যিনি আলো ছড়িয়ে জনপদকে পথ দেখিয়েছেন, তিনি সেই ‘বাঁশবাগানের চাঁদ’। ‘আমাদের ধানখেতের সবুজ শ্যামলিমায়... চা-বাগানের উপচানো একতায়... ভাবনার অন্তরঙ্গ নিজস্বতায়’—এ উপমাগুলো দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, সেই নেতার প্রভাব কেবল রাজনৈতিক পরিসরে নয় বরং দেশের মাটি, মানুষ ও সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে গভীরভাবে প্রোথিত। এ এক জননেতার সাথে জনগণের আত্মিক বন্ধন। ‘তোমার নামটি মুছে ফেলতে হলে মুছে ফেলতে হয়... জ্বলজ্বলে সত্যের অনিরুদ্ধ টুটি’—এ লাইনগুলোতে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য আছে: কোনো কোনো শক্তি ইতিহাসকে মুছে ফেলতে বা বিকৃত করতে চায়। তারা সেই নেতৃত্ব বা আন্দোলনের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চায়, যেটি দেশের ক্রান্তিলগ্নে ছিল আলোর প্রতীক। এটি রাজনৈতিক বাস্তবতায় রাজনৈতিক চরিত্র হনন, ইতিহাস বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির কৌশলের প্রতিচ্ছবি। ‘মহাকাল হাতে ধরে তোমাকে বসিয়েছে অর্জুনের আসনে’—এখানে অর্জুন প্রতীক ন্যায়ের যোদ্ধার। কবি বোঝাতে চেয়েছেন, ঐতিহাসিক নেতৃত্ব সময়ের নির্বাচিত সত্যবাহক, যিনি ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতার পরিবর্তনে কিংবা কারও অপপ্রচারে হারিয়ে যাবেন না। শেষ লাইনে কবি লিখেছেন—‘তুমি বাঁশবাগানের চাঁদ হয়ে এসেছিলে, আছো, থাকবে চিরটাকাল...’ এটি একটি ঐতিহাসিক অবস্থান ঘোষণা।
প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে কিংবা প্রতিটি জাতির জীবনে সময়ের মোড়ে মোড়ে এমন কিছু নেতার আবির্ভবাব ঘটে, যারা অন্ধকারে আলোর প্রদীপ নিয়ে পথ দেখান হাতাশার অন্ধকারে পতিত সিদ্ধান্তহীন ও দিশেহারা জাতিকে। সংকীর্ণ দলবাজি কিংবা রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি তাদের অনন্য ভূমিকা, অবদান ও ত্যাগকে অস্বীকার করতে অপতৎপরতা চালায় কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যায় না। বিশেষত ভারত এবং বাংলাদেশে এমন ছবি আজকাল প্রায়শ চোখে পড়ে। ‘বাঁশবাগানের চাঁদ’ একটি রাজনৈতিক ঘ্রাণযুক্ত কবিতা, যা ঐতিহাসিক নেতৃত্বের বৈধতা, রাজনৈতিক চরিত্র হত্যার প্রতিবাদ, গণমানুষের সাথে নেতার আত্মিক সম্পর্ক এবং জনতার অলিখিত রায়ে সত্য প্রতিষ্ঠার চিরন্তন বার্তা বহন করে। কবিতায় কোনো দেশ বা ব্যক্তির নাম কিংবা বিশেষ সময়কালের উল্লেখ না থাকায় এটি দলীয় না হয়ে সর্বজনীন কাব্যভাষ্য হয়ে উঠেছে। এটি রাজনৈতিক ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে, কাব্যিক ভাষায়।
কাব্যগ্রন্থের ‘নিউটনের সূত্র’ শিরোনামে কবিতাটি আধুনিক নগরসভ্যতার পটভূমিতে রচিত একটি প্রতীকধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় রচনা। এ কবিতায় দারুণ সুন্দর শৈল্পিক শ্লেষ আছে। স্যাটায়ার ও পরিহাস আছে।
‘প্রতিদিনই ভোর হয়; প্রতিপ্রাতেই সুমনাকে ন্যাংটা করতে
গোয়েবেলসের কারখানা থেকে নিত্যনতুন ব্লোয়ার নেয় সীমা,
সীমার বন্ধুরা হাততালি দেয়:
ওই দ্যাখ—দ্যাখ! আমাদের সীমাদি কী যে এক্সপার্ট।’
কবিতাটির প্রথম অংশে ‘ভোর’ প্রতিদিনকার শুরু, চক্রাকার জীবনযাপন ও অনিবার্যতাকে বোঝায়। ‘সুমনাকে ন্যাংটা করা’—এখানে একটি প্রতীক, যা মিডিয়া বা সামাজিক প্রচারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নারীত্বের হরণকে নির্দেশ করে। ‘গোয়েবেলসের কারখানা’ নাৎসি প্রোপাগান্ডার রেফারেন্স, যা এখনকার ভোগবাদী মিডিয়া বা সমাজের মানসিকতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সীমা ও তার বন্ধুরা যেন ভিকটিম নয় বরং প্রোপাগান্ডার অংশীদার। হাততালি দেওয়া সেই অসংবেদনশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা ‘দেখে আনন্দ পায়’ কিন্তু কিছু করে না। দ্বিতীয় স্তবকে এসে কবি লেখেন,
‘কিন্তু হাওয়ারা বড্ড বেশি খামখেয়ালি
ডিগবাজি দিয়ে কোনো কোনো দুপুরে সীমার দিকে ফিরে যায়-সাঁই... সাঁই...
ওপাশ থেকে অট্টহাসির শব্দে উদ্ভ্রান্ত চোখ যায় নিজ নাভির নিচে।’
এখানে ‘হাওয়া’ প্রতীকীভাবে নিয়তি, সমাজের প্রতিক্রিয়া বা অনিয়ন্ত্রিত বাস্তবতা বোঝায়। সীমা যে অন্যকে উন্মোচন করছিল, এখন সেই হাওয়ার উন্মোচন তার দিকে ফিরে আসে—প্রতিক্রিয়ার সূত্র! নিউটনের তৃতীয় সূত্র: ‘প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে’—এ অংশে তা স্পষ্ট হয়। ‘অট্টহাসি’ যেন সীমারই আত্মনগ্নতার উপহাস আর ‘নাভির নিচে’ চোখ যাওয়া—নিজের অনাবৃত ও দুর্বল জায়গার দিকে মুখোমুখি হওয়া। অর্থাৎ সীমাও ভিকটিম—তার নিজের পাপের ফলাফল তাকেই ভোগ করতে হয়। আবার ‘বেতমিজ হাওয়া! আমাকেও...!’ সীমার এ চিৎকার আত্মপ্রতারণার প্রতিফলন। সে ‘হাওয়া’কে দোষ দিচ্ছে, অথচ মূলত সে নিজেই ছিল এর উসকানিদাতা। এ পঙক্তি স্বীকারোক্তিও, প্রতিবাদও, আতঙ্কও। পরিশেষে বলা যায়, ‘নিউটনের সূত্র’ এখানে নিছক বৈজ্ঞানিক নয়, এক সামাজিক ও নৈতিক সত্যের ব্যঞ্জনা—যা আমরা করি, তা একদিন ফিরে আসে—বিপরীত প্রতিক্রিয়ায়। অন্যায়ভাবে অন্যের চরিত্রহনন করে যারা তাদের জন্য এ কবিতা একটি সতর্ক চাবুক। কবিতাটি ভাষায় তীব্র, ব্যঙ্গাত্মক ও প্রতীকসমৃদ্ধ। এটি একটি উঁচু সাহিত্যিক মানসম্পন্ন কবিতা—যা সমাজ, মিডিয়া ও নেতৃত্বকে ঘিরে নৈতিক বিপর্যয়ের একটি জ্বালাময় চিত্র আঁকে।
‘লীলাবতীর ঘাট’ কবিতার বইটিতে আমিনুল ইসলামের ‘সনদ’ কবিতাটি সমাজে ‘সনদ’ বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির অন্ধ মোহের বিরুদ্ধে এক তীব্র ব্যঙ্গ। ‘ট্যারা চোখ’ এখানে প্রতীক—ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতার। কবি প্রশ্ন তুলেছেন, কেউ যদি নিজের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন থাকে, তবে সে কেন মিথ্যা সৌন্দর্য বা যোগ্যতার সনদ পেতে উদগ্রীব হয়? ‘মৃগনয়না’ আর ‘সনদ’-এর মিল ঘটিয়ে কবি দেখিয়েছেন—সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার জন্য মানুষ কতখানি নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে। ‘বিড়ম্বিত রাত’ ও ‘বেশরম দিন’—এই দুটি চিত্রে মানুষের আত্মবিক্রয়ের কষ্ট ও কৃত্রিম জীবনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। ‘কেন বিনিয়োগ করছো তোমার বিড়ম্বিত রাত/ বেশরম দিন!’ লাইন দুটি গভীরতম ক্লান্তি, অবসাদ ও আত্মবিক্রয়ের ছবি আঁকে। ‘বিড়ম্বিত রাত’ বলতে বোঝানো হয়েছে নির্ঘুম কষ্টকর রাত, আর ‘বেশরম দিন’ বলতে বোঝানো হতে পারে আত্মসম্মানহীন, আত্মবিক্রয়কারী কর্মব্যস্ততা। কবি বলছেন—তুমি যেটা আসলে পাওয়ার যোগ্য না, সেটার জন্য এত কিছু খরচ করছো কেন? শেষ পঙ্ক্তিতে কবি তির্যকভাবে বলেন, সনদ পেলেই কি ট্যারা চোখ সুন্দর হয়ে যাবে? প্রকৃত বাস্তবতা কি বদলে যাবে কাগজের ছাপানো একটি অনুমোদনে? এ কবিতার ভাষা সহজ হলেও ব্যঞ্জনা প্রবল। ‘সনদ’ কবিতাটি এক ধরনের প্রতিবাদ—সেই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যেখানে সার্টিফিকেট আর স্বীকৃতি দিয়েই মানুষকে বিচার করা হয়। অথচ সত্যিকারের গুণ ও সত্য আড়ালেই পড়ে থাকে। এটি প্রশ্ন তো তোলে—কিন্তু তার উত্তর দিতে পাঠককে বাধ্য করে।
আমিনুল ইসলাম আমাদের কাব্য-ভুবনের এক অনুপম নির্মাতা, যিনি দৃশ্য নয়, দৃশ্যপটের অন্তর্গত চেতনা অবলোকন করেন। তার কবিতা ‘দৃশ্য’ শুধু একটি দৃশ্যের বর্ণনা নয় বরং একটি সভ্যতার নৈতিক বিপর্যয় ও চিন্তার বিপ্লবী অনুবাদ। প্রতীক ও ব্যঞ্জনায় গঠিত এক সমসাময়িক রূপকচিত্র, যা মনে করিয়ে দেয় আধুনিক সভ্যতার প্রতীকী মহাসমুদ্র—‘তাকাও শ্বেতহাঙরের লেজে ঢেউ ওঠা অটলান্টিকে!’ এই ‘অটলান্টিক’ কেবল একটি ভৌগোলিক উপাদান নয়; এটি পুঁজিবাদ, ভোগবাদ ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকতার চকচকে অথচ শূন্য ব্যূহ। কবি এখানে বিশ্বায়িত সভ্যতার এক ভেলকিবাজি তুলে ধরেন, যা আসলে সত্য নয়—ছায়াজ্বর। ‘চলে আসছে সান্ধ্যপ্রযুক্তিতে তৈরি ধুপছায়া প্রকল্প—’। এ পঙ্ক্তিতে কবি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তথাকথিত উন্নয়নকে ব্যঙ্গ করেন—যেখানে সত্যকে প্রান্তিক করে তুলে ধরা হয় একটি ধূসর পরিকল্পনার অন্তর্গত ছায়া হিসেবেই। মিথ্যার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সত্যের নিঃসঙ্গতা বলা যায়। ‘অথচ বেয়াড়া সত্য মেঘলুপ্ত চাঁদের মতন... ঐ যে সত্য—দ্যাখ! দ্যাখ!’ কবি এখানে সত্যকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করেছেন—যা নিজের আলোয় উজ্জ্বল কিন্তু সব সময় দৃশ্যমান নয়। সত্য এখানে একটি নৈতিক দায়, যা কেউ বহন করতে চায় না, কারণ তা ঝুঁকিপূর্ণ, জটিল এবং একাকী পথচলার নামান্তর। ‘মান্নান সৈয়দ কেন সত্যকে বদমাশ বলেছিলেন/ ঝুঁকি নিয়ে পালটা আক্রমণের’—এ অংশে কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন সেইসব চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের, যারা সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে হয়েছেন বদনামের শিকার। কবি আক্ষেপ করেন—সত্য কখনো কাউকে আক্রমণ করেনি, অথচ তার বিরুদ্ধে প্রতিবার তৈরি হয় শক্তিশালী মিথ্যার যন্ত্রণা। সাহসী উচ্চারণ: ‘সত্য’ নয়, মিথ্যা-নির্ভর সভ্যতা। শেষে ধ্রুপদী উপসংহার—সত্যের বশ্যতা, মিথ্যার বিস্তার:
‘সত্য বেঁচে আছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির প্রাণে
ভেঙে পড়ার নিয়তি নিয়ে
তাকে আড়াল করে বেড়ে চলে মিথ্যার বহুবর্ণ পাহাড়...’
চিত্রকল্পটি অত্যন্ত শক্তিশালী। সত্যকে যেখানে জীবন্ত রাখা হয়েছে; সেখানে তা এক ভয়াবহ নির্ঘুম অগ্নিগিরির প্রান্তে, বিপদসংকুল একাকিত্বে বন্দি। বিপরীতে, মিথ্যা বহুবর্ণ রূপে বিস্তৃত, শ্রেণি, পেশা ও ক্ষমতার জালে গেঁথে ফেলেছে নিজেকে।
আধুনিক প্রতীকধর্মী প্রেম-প্রতিবাদী সাধারণ দু’লাইনের কবিতা ‘শীত’। কবিতার শুরুতেই একটি শক্তিশালী রূপক ব্যবহার করা হয়েছে—‘চিতাবাঘিনীর কোমর অথচ তুমি একটা ভীতুর ডিম’; এখানে ‘চিতাবাঘিনী’ প্রতীক হয়ে উঠেছে বাহ্যিক সাহসিকতা বা আকর্ষণীয়তার আর ‘ভীতুর ডিম’ অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও প্রেমহীনতার। এ বৈপরীত্যই কবিতার মূল দ্বন্দ্ব। ‘কেমনে হবে প্রেম তোমার!–রোদ-তিরিশেও হৃদয় হিম।’—এই লাইন প্রেমহীন, শীতল হৃদয়ের আভাস দেয়। বাহ্যিক তাপ (রোদ-তিরিশ) থাকা সত্ত্বেও হৃদয় ‘হিম’, অর্থাৎ প্রেমহীন, নিস্তরঙ্গ, শূন্য। ‘শীত’ কবিতাটি প্রেমের খোলসকে ভেঙে প্রেমহীন বাস্তবতার দিকে আঙুল তোলে। কবিতার দুটি পঙক্তিই তীব্র প্রতীকী ও ব্যঙ্গাত্মক। সংক্ষিপ্ত, সংহত এবং আধুনিক ভাবপ্রবণতায় নির্মিত কবিতাটি প্রেমের নামে আবেগহীনতার বিরুদ্ধে এক ধরনের কাব্যিক প্রতিবাদ। যেখানে কবি ভাষাকে করেছেন ধারালো, প্রতীককে করেছেন অস্ত্র।
‘এইসব মহাজন’ শিরোনামের কবিতাটির প্রথম অংশে, ঈগলের রূপকে এসেছে আগ্রাসী শোষকের চিত্র, যে উঠোনের ব্যাঙ-মুরগি-টিপ-খাবার নিয়ে যায় অথচ ‘মহাজন’ শ্রেণি তার গতি ও শক্তির প্রশংসা করে। কিন্তু গেরস্তের শিশু বা কিশোর যখন প্রতিরোধে তীর-গুলতি তোলে, তখন তার বিরুদ্ধেই রচিত হয় ‘সন্ত্রাসবিরোধী’ বয়ান। এটি গণতন্ত্রের নামে চালানো ক্ষমতার অব্যাহত ভণ্ডামিকে নগ্ন করে। দ্বিতীয় অংশে, চাঁদের আলো রূপক হিসেবে এসেছে আলোকিত সত্য, স্বাধীনতা বা সৌন্দর্যের। কিন্তু সেই আলোককে দোষারোপ করা হয় ‘শান্তিভঙ্গকারী অন্ধকারবাদী’ হিসেবে। এখানেই উঠে আসে মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডা চালিয়ে সত্যকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা। তৃতীয় অংশে, দুর্নীতির ফাঁস হওয়া সত্যকে আড়াল করতে এই মহাজনগণ গল্প রচনা করে, দোষ চাপায় নিরীহদের ওপর। দর্শক হয়ে থাকা ‘টিকটিকি’ এখানে টিকিটিকি হচ্ছে স্পাই বা গোয়েন্দার প্রতীক। টিকিটিকিরা হচ্ছে সমাজের সেই গোয়েন্দাস্বভাবের মানুষ যারা গোপন অন্যায় কাজে অভ্যস্ত—যারা অন্যায়ের সাথে সহাবস্থান করে। শেষাংশে, ব্যাজধারীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতীক, আর যারা তা পায় না, তারা আঁধারের দরবারে তদবির করে—এই ‘মহাজন সিন্ডিকেট’র আন্তর্জাতিক শাখাও আছে, যা দুর্নীতি, মিথ্যাচার ও দমননীতির বিশ্বায়নকেই নির্দেশ করে। ‘এইসব মহাজন’ কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নয়, এটি বিবেকের অগ্নিপরীক্ষা। রূপক, বিদ্রূপ ও চরম প্রতীকায়নের মাধ্যমে কবি আমাদের বুঝিয়ে দেন—আলো, সত্য আর প্রতিরোধ যখনই মাথা তোলে, তখনই এক সিন্ডিকেট তা নিপীড়নে নেমে পড়ে। এই কবিতা তাই এক সাহসী সাহিত্যিক প্রতিবাদ, যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—কে চোর, কে রক্ষক, আর কারা সেই মুখোশধারী ন্যায়বিরোধী ক্ষমতালোভী ‘মহাজন’। এসব ‘মহাজন’ কি ‘মগজ বিকিয়ে দেওয়া’ লোভী পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদেরও নির্দেশ করে?
‘বোবা আকাশের নিচে’ কবিতাটি মানুষের ভেতরের অসারতা, ভণ্ডামি এবং আত্মপরিচয়ের সংকটকে প্রতীক ও রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। ময়ূরের মতো মানুষ আজ আর নিজের মতো করে ভাবতে বা প্রকাশ করতে পারে না, কারণ তার পরিচয়টাই অন্যের দেওয়া। সমাজে যারা নেতৃত্ব দেয়, তারা চাতুর্যের জোরে ক্ষমতা নেয়, অথচ সংকটে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকে। ‘সমুদ্র-সনদ-লোভী জলাশয়’ আসলে সেসব মানুষ, যারা বড় হওয়ার ভান করে, অথচ তাদের ভেতরে গভীরতা নেই। তারা উচ্চকণ্ঠে হইচই করলেও সত্যিকারের জ্ঞানী ও সংযত মানুষেরা নীরব, অথচ অথই। এ কবিতায় কবি মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনা, মুখোশধারিতা ও অন্তঃসারশূন্যতার এক নির্মম চিত্র এঁকেছেন, যা আমাদের সমাজেরই প্রতিফলন।
কবিতাগ্রন্থের নামসূত্র কবিতা এবং গ্রন্থের শেষ কবিতা ‘লীলাবতীর ঘাট’ কবিতাটি প্রেম, স্মৃতি, প্রতীক এবং আত্মগবেষণার এক অন্তর্মুখী ভ্রমণ। কবিতাটিতে কবির সঙ্গে লীনার সম্পর্ক একটি সাধারণ প্রেম নয়—তা বিস্তৃত হয়েছে খুফুর পিরামিড থেকে তুতেনখামুনের ভূমধ্যসাগর, সুয়েজ খাল, উম্মে কুলসুমের গান, নেফারতিতির মূর্তি—এসব ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের প্রতীকে। লীনার ওড়না যেন পাল, যা কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কল্পনার, স্মৃতির ও প্রেমের বহু তটে। কবিতায় আছে ইনানী বিচ, হিজল, টাঙ্গুয়ার হাওর, গঙ্গামতির মোড়—বাংলার ভূপ্রকৃতি, প্রেমিকের চোখে রূপ পেয়েছে এক অসাধারণ আবেগী সৌন্দর্যে। লীনা সর্বত্র, লীনা প্রতিটি সৌন্দর্যের রূপান্তর। কিন্তু ‘লীলাবতীর ঘাটে’ এসে যেন সবকিছু ভেঙে পড়ে। সেখানে প্রেমিকার কণ্ঠে ভিড় করে গুলতেকিন, সিলভিয়া প্লাথ, তসলিমা নাসরিন—অর্থাৎ নারীর শক্তি, বেদনা, প্রতিবাদ, ব্যক্তিত্ব—প্রেমিকের চোখে ধরা দেয় এক অনির্বচনীয় আশঙ্কা ও নতুন ব্যাখ্যায়। এখানে টেনে আনা হয়েছে প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ব্যক্তিজীবনের দৃষ্টান্ত, টেনে আনা হয়েছে—একদিকে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী গুলতেকিন, অন্যদিকে নতুন প্রেম শাওনের প্রসঙ্গ। এসবই প্রতীকী ব্যবহার। কবির নিজের মধ্যবয়সে সেই দ্বন্দ্ব প্রবেশ করে—‘তুমিও যদি কোনো শাওন পেয়ে যাও!’—এ প্রশ্নই কবিকে চমকে দেয়, কাঁপিয়ে তোলে। সে ভয় থেকে উঠে আসে ‘পরাজিত কণ্ঠ’, চিৎকার আটকে যায়, উত্তর দিতে গিয়ে শুধু বলে—‘পানি খাবো।’ ‘লীলাবতীর ঘাট’ কেবল প্রেমের কবিতা নয়, এটি প্রেমের মধ্যে একজন পুরুষের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা, আত্মসমালোচনা এবং মূল্যবোধের টানাপোড়েনকে স্পষ্ট করে তোলে। এখানে প্রেম যেমন বিস্ময়কর, রূপকথার মতো, তেমনই একসময় তা হয়ে ওঠে আত্মবিশ্লেষণের আয়না—যেখানে একজন প্রেমিক নিজেকেই প্রশ্ন করে, ভয় পায় এবং থেমে যায়।
আমিনুল ইসলামের ‘লীলাবতীর ঘাট’ গ্রন্থে অনেকগুলো কবিতার সমাহার ঘটেছে। বিষয়ভাবনা এবং কাব্যকৌশল উভয় দিক থেকে বৈচিত্র্যে ভরপুর সেসব কবিতা। সামাজিক ভাবনা ও শিল্পবোধ একসঙ্গে মিলে নতুন স্বাদের কবিতা হয়েছে। এসব কবিতা গভীর চিন্তাভাবনা এবং নিজস্ব কাব্যভাষা পাঠকদের গভীর আনন্দ দেবে বলে আমার বিশ্বাস। বইটির প্রচ্ছদ নামকরণের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ এবং খুবই আকর্ষণীয়। সব মিলিয়ে একটি চমৎকার কাব্যগ্রন্থ।
কবিতাগ্রন্থ: লীলাবতীর ঘাট
লেখক: আমিনুল ইসলাম
প্রকাশক: বর্ণধারা
প্রচ্ছদশিল্পী: রাফসান, ক্রিয়েটিভ প্লাস
প্রকাশকাল: বইমেলা ২০২৫
মূল্য: ২০০ টাকা।
এসইউ/জিকেএস

 2 months ago
8
2 months ago
8






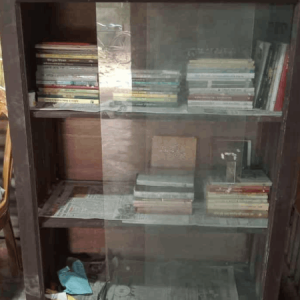


 English (US) ·
English (US) ·