সমাজবিজ্ঞান মানুষের আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক এবং সমষ্টিগত জীবনের জটিলতা বোঝার এক অন্তহীন প্রচেষ্টা। বাংলাদেশে এই শাস্ত্রের গবেষণা গত কয়েক দশকে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। প্রথাগত সমাজতত্ত্ব যেখানে মূলত সাক্ষাৎকার, জরিপ ও নৃবিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করত, সেখানে এখন যুক্ত হয়েছে উন্নত প্রযুক্তি, ডেটা বিশ্লেষণ ও অ্যালগরিদমিক পদ্ধতি। এর ফলেই উদ্ভূত হয়েছে একটি নতুন এবং অত্যাধুনিক গবেষণাক্ষেত্র—কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞান (Computational Sociology)। এটি শুধু সমাজগত ঘটনা বিশ্লেষণের একটি নতুন পদ্ধতি নয়, বরং সামাজিক বাস্তবতাকে বোঝার জন্য এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে বিগ ডেটা (Big Data), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিন লার্নিং (Machine Learning) এবং সিমুলেশন মডেলিংকে কাজে লাগানো হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও জনবহুল দেশে এই শাখার গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বাড়ছে, বিশেষত নগরায়ণ, শ্রমবাজার, মাইগ্রেশন, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক গতিশীলতা বিশ্লেষণে।
কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞানের মূল দর্শন হলো সমাজের জটিলতা বোঝার জন্য তথ্যভিত্তিক মডেল তৈরি করা। এটি প্রথাগত সমাজবিজ্ঞানের গুণগত (qualitative) এবং পরিমাণগত (quantitative) পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। প্রথাগত গবেষণায় একটি ছোট জনগোষ্ঠীর ওপর জরিপ চালিয়ে বা সাক্ষাৎকার নিয়ে সামগ্রিক সামাজিক প্রবণতা অনুমানের চেষ্টা করা হয়, যা প্রায়শই সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং সীমিত পরিসরের কারণে সামগ্রিক চিত্র দিতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, কম্পিউটেশনাল পদ্ধতিতে বিগ ডেটা ব্যবহার করে একই সময়ে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি মানুষের আচরণ, মিথস্ক্রিয়া এবং প্রবণতা বিশ্লেষণ করা সম্ভব।
বাংলাদেশে প্রতিদিন অসংখ্য তথ্য তৈরি হচ্ছে—মোবাইল ফোন ব্যবহার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম (ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব), অনলাইন লেনদেন, ই-গভর্ন্যান্স সেবা, এমনকি গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পগুলোও প্রতিনিয়ত ডেটা তৈরি করছে। এই বিপুল ডেটা যদি প্রথাগত সমাজবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কম্পিউটেশনাল পদ্ধতিতে এই ডেটাগুলো থেকে সামাজিক প্রবণতা, নীতি-সংস্কার এবং উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা তুলনামূলকভাবে দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃতভাবে সম্ভব। এটি গবেষকদেরকে একটি নতুন লেন্স দিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা সমাজের লুকানো প্যাটার্ন এবং সংযোগগুলো উন্মোচন করতে পারেন।
বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ এখন একটি তথ্য-নির্ভর, পূর্বাভাসভিত্তিক এবং প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ পর্যায়ে প্রবেশ করছে। এই পরিবর্তনের সঠিক ব্যবহারের জন্য দরকার নৈতিক নিয়ন্ত্রণ, সমতা ভিত্তিক ডেটা অ্যাক্সেস এবং স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল তৈরি। নাহলে এই প্রযুক্তি যেমন উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে, তেমনি বৈষম্য ও শোষণ বাড়ানোর অস্ত্রও হয়ে উঠতে পারে। সঠিক প্রস্তুতি, গবেষণা বিনিয়োগ এবং আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতার মাধ্যমে কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞান বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের গতিপথে এক নতুন অধ্যায় যোগ করবে।
কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে।
১. জনস্বাস্থ্য ও মহামারি মোকাবিলা
বাংলাদেশে এই শাখার একটি বড় প্রয়োগ দেখা গেছে কোভিড-১৯ মহামারির সময়। মোবাইল ফোনের অবস্থানভিত্তিক ডেটা, ফেসবুকের জনমিতি বিশ্লেষণ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টের সমন্বয় করে মানুষের চলাচল, সামাজিক দূরত্ব রক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্তি সম্পর্কে একটি গতিশীল চিত্র তৈরি করা হয়েছিল। এই বিশ্লেষণ এজেন্ট-ভিত্তিক মডেলিং (Agent-Based Modeling) ব্যবহার করে করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে একটি 'ডিজিটাল এজেন্ট' হিসেবে ধরে সামাজিক আচরণের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। এই মডেলগুলো দেখিয়েছে যে লকডাউনের মতো নীতি কীভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে পারে এবং কোন অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো দুর্বল। এভাবেই প্রমাণিত হয় যে কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞান শুধু তাত্ত্বিক অনুসন্ধান নয়, বাস্তব নীতিনির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
২. নগরায়ণ ও গ্রামীণ অভিবাসন
বাংলাদেশে নগরায়ণ একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। প্রথাগত গবেষণায় এই অভিবাসনের কারণ ও ফলাফল বুঝতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু কম্পিউটেশনাল পদ্ধতিতে এটি আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে বোঝা সম্ভব। স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন, ফসলের উৎপাদন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করা যায়। একই সাথে, মোবাইল ফোনের ডেটা বিশ্লেষণ করে অভিবাসনের গতিপথ এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগের সন্ধান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন গ্রাম থেকে কোন শহরে বেশি মানুষ যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে এবং তাদের পেশাগত পরিবর্তনের ধরন কেমন—এই সবকিছুই ডেটা বিশ্লেষণ করে বোঝা সম্ভব। এই ডেটাভিত্তিক তথ্য ভবিষ্যতের নগর পরিকল্পনা, অবকাঠামো নির্মাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩. ডিজিটাল অর্থনীতি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি অন্যতম চালিকাশক্তি হলো ডিজিটাল অর্থনীতি। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) যেমন বিকাশ, নগদ, রকেট; ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলো গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ককে নতুনভাবে গড়ে তুলছে। এই নেটওয়ার্কের গতিশীলতা বোঝার জন্য নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ এবং অ্যালগরিদমিক ট্রেসিং অত্যন্ত কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, MFS লেনদেন ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কীভাবে অর্থ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সঞ্চালিত হচ্ছে, কোন অঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বেশি সক্রিয়, কিংবা কোন সময়ে অর্থপ্রবাহ কমে যায়। এই বিশ্লেষণ শুধু আর্থিক খাতের জন্য নয়, সামাজিক বৈষম্য হ্রাসের কৌশল নির্ধারণেও সহায়ক হতে পারে। এটি দেখায় যে কীভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক বৈষম্য চিহ্নিত করা এবং নীতিগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তা হ্রাস করার উপায় খুঁজে বের করা যায়।
৪. রাজনৈতিক গতিশীলতা ও জনমত বিশ্লেষণ
রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কম্পিউটেশনাল পদ্ধতির ভূমিকা বাড়ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন, কোটাবিরোধী প্রতিবাদ কিংবা ডিজিটাল প্রচারণার ধরন বিশ্লেষণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ডেটা ব্যবহার করা হচ্ছে। সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস এবং টপিক মডেলিং ব্যবহার করে টুইটার বা ফেসবুক পোস্ট থেকে বোঝা সম্ভব কোন অঞ্চলে জনমত কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, কোন বিষয়গুলো জনগণের মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত, কিংবা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য (misinformation) কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এই বিশ্লেষণ নীতিনির্ধারকদেরকে জনগণের চাহিদা ও উদ্বেগের বিষয়ে দ্রুত অবগত হতে সাহায্য করে, কিন্তু এখানে নৈতিকতা ও গোপনীয়তা রক্ষার প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলাদেশে কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
১. ডেটা অবকাঠামো ও অ্যাক্সেস: বাংলাদেশে এখনো পর্যাপ্ত ডেটা অবকাঠামো, প্রশিক্ষিত জনবল এবং নৈতিক নীতিমালা পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। অনেক সময় সরকারিভাবে সংগৃহীত ডেটা গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত নয়। বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, যেমন পরিসংখ্যান ব্যুরো বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রচুর ডেটা থাকলেও সেগুলোর সঠিক সংরক্ষণ, সমন্বয় এবং গবেষকদের কাছে সহজলভ্য করার প্রক্রিয়া এখনও অপ্রতুল। এছাড়া, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন টেলিকম কোম্পানি) কাছে থাকা বিপুল ডেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনি ও বাণিজ্যিক বাধা রয়েছে।
২. নৈতিকতা ও গোপনীয়তা: ব্যক্তিগত ডেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত অস্পষ্টতা রয়েছে। ডেটা সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী আইনের অভাব থাকায় ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহারের ঝুঁকি থাকে। ডেটা বিশ্লেষণ করার সময় গবেষকদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয় যাতে কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয়। অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত (algorithmic bias) একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। যেসব ডেটা দিয়ে মডেল তৈরি হয় সেগুলো যদি অসম্পূর্ণ বা পক্ষপাতমূলক হয় (যেমন, যদি শুধু শহুরে ডেটা ব্যবহার করা হয়), তবে বিশ্লেষণও বিভ্রান্তিকর হতে পারে এবং সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
৩. আন্তঃবিষয়ক জ্ঞানের অভাব: কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞান সফলভাবে প্রয়োগের জন্য কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, এবং সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের সমন্বয় প্রয়োজন। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই তিনটি ক্ষেত্রকে একীভূত করে পাঠ্যক্রম তৈরি করা এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ফলে, পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত গবেষক ও ডেটা বিজ্ঞানীর অভাব রয়েছে যারা সামাজিক সমস্যা সমাধানে এই পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন।
ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানে কম্পিউটেশনাল পদ্ধতির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:
১. শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বিনিয়োগ: বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ বা অন্তত আন্তঃবিষয়ক পাঠ্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। শিক্ষার্থীদেরকে বিগ ডেটা বিশ্লেষণ, মেশিন লার্নিং, এবং পাইথন বা R-এর মতো প্রোগ্রামিং ভাষা শেখানোর মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করা সম্ভব। এছাড়া, এই বিষয়ে গবেষণা তহবিল বাড়ানো প্রয়োজন যাতে গবেষকরা উচ্চমানের গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন।
২. উন্মুক্ত ডেটা (Open Data) উদ্যোগ: সরকারি নীতিনির্ধারণে ওপেন ডেটা উদ্যোগ বাড়ানো হলে গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং সাধারণ মানুষ সহজেই জনগুরুত্বপূর্ণ ডেটা ব্যবহার করতে পারবে। এটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতেও সাহায্য করবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ডেটা সংগ্রহের পাশাপাশি সেগুলোকে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করতে পারে, যা গবেষকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।
৩. নৈতিক ও আইনগত কাঠামো তৈরি: ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা এবং ডেটা ব্যবহারের নৈতিকতা নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। ডেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত যাতে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় এবং অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত হ্রাস করা যায়। গবেষকদেরকে এই নীতিমালা মেনে চলার জন্য প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন।
কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বাস্তবতাকে বোঝার জন্য শুধু পরিসংখ্যানগত সংখ্যাগুলি বিশ্লেষণ করা নয়, বরং তার পেছনের মানবিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেও অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করছে। এই শাখা তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের অদৃশ্য ধারাকে দৃশ্যমান করে তুলছে। বাংলাদেশের মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল দেশে এই শাখা হতে পারে উন্নয়নের পথনকশা তৈরির এক নতুন হাতিয়ার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর সমাজনীতি প্রণয়ন, জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা, শহুরে যানজট নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা নীতি সংস্কার কিংবা স্বাস্থ্য খাতের সেবাদান—সব ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।
অতএব, বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ এখন একটি তথ্য-নির্ভর, পূর্বাভাসভিত্তিক এবং প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ পর্যায়ে প্রবেশ করছে। এই পরিবর্তনের সঠিক ব্যবহারের জন্য দরকার নৈতিক নিয়ন্ত্রণ, সমতা ভিত্তিক ডেটা অ্যাক্সেস এবং স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল তৈরি। নাহলে এই প্রযুক্তি যেমন উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে, তেমনি বৈষম্য ও শোষণ বাড়ানোর অস্ত্রও হয়ে উঠতে পারে। সঠিক প্রস্তুতি, গবেষণা বিনিয়োগ এবং আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতার মাধ্যমে কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞান বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের গতিপথে এক নতুন অধ্যায় যোগ করবে।
লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী।
এইচআর/এএসএম

 2 days ago
10
2 days ago
10






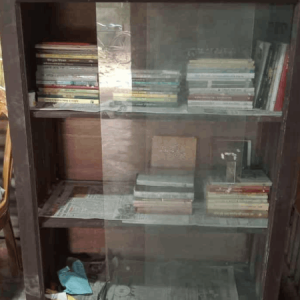


 English (US) ·
English (US) ·