যদিও একজন রোজগার করে, তবু ভালোই চলছিল আবির আর বহ্নির সংসার (দুজনারই ছদ্মনাম)। পড়ালেখা শেষ করলেই বহ্নি ঢুকবে চাকরিতে। তখন আবিরের ওপর থেকে চাপ কিছুটা কমবে। এ রকমই ছিল পরিকল্পনা।
পড়ালেখা শেষ হলো, ব্যাংকে চাকরি হলো। চাকরি পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতনও বাড়লো। কিন্তু প্রথম পদোন্নতির পর বহ্নির বেতন যখন বাড়লো, স্বামী আবিরের বেতনকে তা ছাড়িয়ে গেল। আইনজীবীর কাছে আক্ষেপ করে আবির বলছিলেন, ভেবেছিলাম, স্ত্রীর বেতন বাড়লে সংসারে স্বচ্ছলতা আসবে। কিন্তু যা হলো…
কর্মক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। উদ্যোগ থেকে কর্পোরেট জগত, ব্যাংক থেকে তথ্যপ্রযুক্তি — প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ও উজ্জ্বল অবদান এখন দৃশ্যমান। তাই পুরুষের সমান পারিশ্রমিকের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘ইক্যুয়াল পে’ বা সমমজুরির দাবি উঠেছে। বাংলাদেশে যদিও তা নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য নেই, তবে পরিবার চালানোর ক্ষেত্রে নারীর আর্থিক অবদান বেড়েছে। কিন্তু নারীর এই বাড়তি আয়ের প্রভাব তার পারিবারিক সম্পর্ক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর পড়ছে।

২০২৪ সালে দ্য ইকোনমিক জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, স্বামীর চেয়ে স্ত্রী বেশি আয় করলে অনেক দম্পতির মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে মানসিক চাপ, হতাশা কিংবা আসক্তিজনিত সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
গবেষণাটি সুইডেনের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলছে, যখন স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর আয় বেশি হচ্ছে, তখন পুরুষদের মধ্যে মানসিক সমস্যা দেখা দেওয়া সম্ভাবনা প্রায় ৮ থেকে ১১ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। কিন্তু কেন?
দ্বন্দ্বের কারণ কী?
১. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়লেও গড়পরতা সামাজিক মানসিকতায় এখনও পুরুষকেন্দ্রিক ‘উপার্জনকারী’ বা ‘ব্রেডউইনার’ ধারণা প্রাধান্য পায়। ধারনাটি এমন — পরিবারে উপার্জন ও আর্থিক প্রয়োজনীয়তা মেটানো শুধু পুরুষের কাজ! একে পুরুষের একমাত্র অবদান হিসেবেও দেখা হয়।

২. ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ-এ প্রকাশিত ‘বাংলাদেশে পুরুষ-উপার্জনকারী ধারণার কারণ ও পরিণতি’ শীর্ষক একটি গবেষণা বলছে, অনেক পরিবারেই স্ত্রী বেশি আয় করলে পুরুষ মানসিক চাপে পড়েন, নিজের পরিচয় নিয়ে সংকট বোধ করেন। আবার স্ত্রীও সামাজিক চাপের মুখে পড়েন এই ভেবে যে, তিনি পরিবারের ‘প্রধান উপার্জনকারী’ হয়ে উঠেছেন।
৩. দ্য ইকোনমিক জার্নালের ‘দম্পতিদের আপেক্ষিক আয় ও মানসিক স্বাস্থ্য’ শীর্ষক গবেষণা বলছে, পুরুষদের মধ্যে যখন ঐতিহ্যগত ‘ব্রেডউইনার’ পরিচয় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, তখন সেটা পরিচয়-সংকট তৈরি করে। ফলাফল হয় স্ট্রেস, উদ্বেগ ও আসক্তি। সুইডিশ গবেষণাটিতেও দেখা গেছে যে, স্ত্রী স্বামীকে ছাড়িয়ে গেলে পুরুষদের মধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়।
তাহলে পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাবেন কীভাবে? সমাধান কী? সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, সমস্যার শেকড় শুধু ব্যক্তি-স্তরে নয়, সামাজিক মানসিকতা ও আদর্শে। ব্যক্তিগত ও সম্পর্কভিত্তিক কাউন্সেলিং, দুটো সমান্তরাল পথে চললে এই মানসিক সংকট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যেমন:
১. কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি: আন্তর্জাতিক রিভিউগুলোতে প্রমাণ মিলেছে যে কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি আসক্তি, উদ্বেগ ও বিষণ্নতা কমাতে কার্যকর।
২. যুগল কাউন্সেলিং বা কাপল থেরাপি: সম্পর্কের টানাপোড়েন, যোগাযোগ সমস্যার সমাধানে যুগল থেরাপি অনেক ক্ষেত্রে সফল প্রমাণিত হয়েছে।
৩. কমিউনিটি-ভিত্তিক জেন্ডার ডায়লগ গ্রুপ: অনেক গবেষণা বলছে, অর্থনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে লিঙ্গ বিষয়ক সংলাপ যুক্ত করলে পরিবারে চাপ কমে এবং পুরুষ-নারীর মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ে।
৪. নীতিগত সমতা নিশ্চিত করা: কর্মক্ষেত্রে সমান মজুরি ও নারীর নেতৃত্বকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া গেলে সামাজিক চাপও কমবে।

এগুলো গবেষণা থেকে পাওয়া সমাধানের পথ। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে কোন পদক্ষেপগুলো কাজ করবে সেটা বোঝার জন্য আঞ্চলিক গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশে নারীর কর্মক্ষমতা ক্রমেই বাড়ছে। আর এই পরিবর্তনকে ইতিবাচক রাখতে হলে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে।
১. কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করতে হবে। স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা রাখলে সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে চিকিৎসা নেওয়া যায়।
২. কমিউনিটি-লেভেলে সচেতনতা ক্যাম্পেইন চালানো দরকার, যাতে পুরুষরা বুঝতে পারেন, নারীর আয় বৃদ্ধি মানে পরিবারের উন্নতি।
৩. নীতিগত সুরক্ষা জোরদার করতে হবে। সমান মজুরি নিশ্চিত হলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে, এবং ‘ব্রেডউইনার সংকট’ ধীরে ধীরে কমে যাবে।

অর্থাৎ, সমাধান হতে হবে দ্বিমুখী — ক্লিনিকাল মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। তাহলেই নারীর অগ্রযাত্রা সত্যিকার অর্থে পরিবার ও সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে। তাই আজ, ১৮ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক সমান মজুরি দিবসে এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিন।
সূত্র: দ্য ইকোনমিক জার্নাল (২০২৪), কোয়ার্টারলি জার্নাল অব ইকোনমিক্স (২০১৫), বি এম সি ইন্টারন্যাশনাল হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস (২০১৩), কাপল থেরাপি ইন দ্য ২০২০স – কারেন্ট স্ট্যাটাস অ্যান্ড এমার্জিং ডাইরেকশনস (২০২২), সিবিটি এফিকেসি ফর অ্যালকোহল অ্যান্ড ড্রাগ ইউজ ডিসঅর্ডারস (২০২৩)
এএমপি/আরএমডি/জেআইএম

 3 hours ago
1
3 hours ago
1

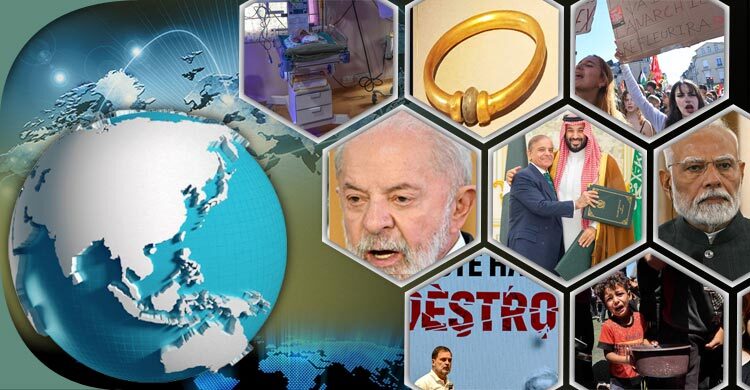


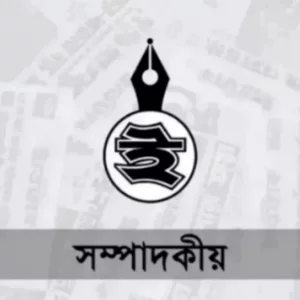




 English (US) ·
English (US) ·