সম্প্রতি ‘ইলিশের দামের লাগাম টানতে কেন্দ্রীয়ভাবে মূল্য নির্ধারণে যাচ্ছে সরকার-’ শীর্ষক খবরে চোখ আটকে গেল। ইতোমধ্যে প্রধান উপদেষ্টার সম্মতি পাওয়ার পর বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ইলিশের দাম নির্ধারণের একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল এবং সেটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে উপস্থাপন করা হলে তিনি এতে সম্মতি দিয়েছেন।
আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশের স্বাদ ও সুনামের সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ী ও আড়তদাররা নিজেদের ইচ্ছেমতো দাম নির্ধারণ করছেন। ফলে সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ইলিশ। শুধু পদ্মানদী বা মেঘনা, যমুনার ইলিশ নয়—বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, কক্সবাজার, বরগুনা, ঝালকাঠিসহ দেশের ১০ থেকে ১২টি উপকূলীয় জেলা থেকে ইলিশ আহরণ করা হয়। অথচ এসব জায়গায় উৎপাদনের কোনো সরাসরি খরচ না থাকলেও সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে ইলিশের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে।
বাংলাদেশে ইলিশ শুধু একটি প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন মাছ নয়। এটি এক আবেগ, এক স্বাদ, এক সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের প্রতীক। এই মাছকে ঘিরে উৎসব, রাজনীতি, কূটনীতি এমনকি কাব্যচর্চাও হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই রূপালী জলের রাজার দামে যে ‘নৈরাজ্য’ দেখা দিয়েছে, তাতে ইলিশ আজ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। তাই দেশের সাধারণ মানুষেরা ক্রয়ক্ষমতা এবং বাজারব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে।
বাজার নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি ও পর্যাপ্ত নজরদারির অভাব থাকায় মাছ ধরার মৌসুম এলেই বাজারে গুজব ছড়ায় ‘মেঘনায় আর মাছ নেই’, ‘বড় ইলিশ উঠছে না’, ‘জেলেরা নেমেই পারেনি’, ইত্যাদি। অথচ একই সময় দেখা যায়, ভারতে হাজার টন ইলিশ রপ্তানির প্রস্তুতি চলছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এসব গুজব কারা ছড়ায়, আর কীভাবে তারা বাজারকে প্রভাবিত করে?
আমাদের উৎসব-পার্বণ হোক বা নিত্যদিনের বাজার, ইলিশের দাম যেন এক স্বেচ্ছাচারী চরিত্রে রূপ নিয়েছে। এক অঞ্চলে যেখানে এক কেজি ইলিশ ১২০০ টাকা, সেখানে অন্য অঞ্চলে তা ২৬০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়।যার কোনো যৌক্তিকতা নেই, নেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ।
ইলিশের দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো একক মূল্য নির্ধারণ না থাকা। কৃষিপণ্য বা মাছের ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে কিছুটা দামের পার্থক্য যৌক্তিক হলেও, ইলিশের ক্ষেত্রে তা মাত্রাতিরিক্ত। বরিশাল, চাঁদপুর বা ভোলার বাজারে যেখানে ইলিশ তুলনামূলক কম দামে পাওয়া যায়, ঢাকায় তার দাম দ্বিগুণ হয় কীভাবে? একেকজন বিক্রেতা একেক মূল্য চেয়ে থাকেন—কেউ বলে ‘খাঁটি পদ্মার ইলিশ’, কেউ ‘একদম নতুন’ বলে দাম বাড়ায়। অথচ এসব দাবির প্রমাণ নেই, মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও নেই। ফলে বাজারে দেখা দিয়েছে নৈরাজ্য, আর সাধারণ ভোক্তা পড়ে গেছে অসহায় অবস্থায়।
এই নৈরাজ্যের পেছনে আরও কিছু কাঠামোগত কারণ রয়েছে। যেমন, সরবরাহ শৃঙ্খলা দুর্বল, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব, এবং সর্বোপরি সরকারি তদারকির সীমাবদ্ধতা। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলোতে কোনো প্রকার দামের তালিকা নেই। পাইকারি বাজারে কেউ দাম নিয়ন্ত্রণ করে না। আবার খুচরা পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ অনেক সময় অভিযান চালালেও তা হয় ক্ষণস্থায়ী এবং ঢিলেঢালা।
প্রশ্ন হলো, তাহলে কি সারাদেশে একক দামে ইলিশ বিক্রি করা সম্ভব? ইলিশপ্রিয়দের নিকট থেকে সরাসরি উত্তর আসছে হ্যাঁ, তবে শর্তসাপেক্ষে।
প্রথমত, সরকারকে ইলিশ বাজারজাতকরণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। তাতে নির্ধারণ করতে হবে কোন আকারের ইলিশের দাম কত হবে, কীভাবে মান যাচাই করা হবে, কীভাবে পরিবহন ও সংরক্ষণ করা হবে, এবং কোন পদ্ধতিতে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানো হবে। এজন্য উৎপত্তি কেন্দ্রিক মূল্য নির্ধারণ বা ইলিশ যেখানে ধরা হয় চাঁদপুর, ভোলা, পাথরঘাটা ইত্যাদি জায়গায় মৌসুমভিত্তিক উৎপাদন খরচ, মজুরি ও পরিবহন বিবেচনায় একটি ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা উচিত। এরপর পরিবহন ও পাইকারি স্তরে যৌক্তিক মুনাফা যোগ করে ভোক্তা মূল্য ঠিক করা যায়।
দ্বিতীয়ত, একটি অনলাইনভিত্তিক ‘ইলিশ ট্র্যাকিং সিস্টেম’ চালু করা যেতে পারে, যেখানে মাছ ধরা থেকে বিক্রি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে তথ্য থাকবে। এতে বাজারে ভেজাল, প্রতারণা ও মজুতদারদের দৌরাত্ম্য কমবে। চীনসহ বহু দেশ ইতোমধ্যেই মাছ বা ফলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করছে।
তৃতীয়ত, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে নিয়মিত বাজার নজরদারি করতে হবে। বাজারে সরকার নির্ধারিত দাম লঙ্ঘন করলে তাৎক্ষণিক জরিমানা ও লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। একইসঙ্গে বিক্রেতাদের জন্য প্রশিক্ষণও থাকা উচিত যেন তারা মানসম্মতভাবে পণ্য বিক্রি করেন।
চতুর্থত, একটি জাতীয় ‘ইলিশ মূল্য বোর্ড’ গঠন করা যেতে পারে। এ বোর্ডে মৎস্য বিভাগ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মাছ ব্যবসায়ী সমিতি এবং ভোক্তা সংগঠনের প্রতিনিধি থাকবে। এই বোর্ড প্রতি মৌসুমে ইলিশের গড় উৎপাদন, চাহিদা ও সরবরাহ বিবেচনায় রেখে প্রতি কেজির দাম নির্ধারণ করবে। বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে হলে প্রয়োজন একটি কেন্দ্রীয় মুদ্রানীতিমালার মতো ‘মাছমূল্য নীতিমালা’। ঠিক যেভাবে সরকার ডিম, পেঁয়াজ, চাল কিংবা চিনির ক্ষেত্রে একটি গাইডলাইন দেয়, তেমনি ইলিশের ক্ষেত্রেও প্রান্তিক পর্যায় থেকে ভোক্তা পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট মূল্য কাঠামো নির্ধারণ করা দরকার।
এছাড়া, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সরকারি ইলিশ বাজার চালু করা যেতে পারে, যেখানে একক দামে মান যাচাই করা ইলিশ সবার জন্য সহজলভ্য হবে। এতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম স্থিতিশীল থাকবে এবং অপ্রয়োজনীয় দাম বাড়ানো ঠেকানো যাবে। সারাদেশে একক দাম বাস্তবায়নে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেমন: ডিজিটাল স্কেল, মোবাইল অ্যাপস এবং বাজার মনিটরিং সেল গড়ে তুলে সরকার ইলিশের দৈনিক বা সাপ্তাহিক দর নির্ধারণ করে সেটি প্রচার করতে পারে। এভাবে একটি ‘রেফারেন্স প্রাইস’ বা সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব।
আমাদের দেশে ইলিশ সংরক্ষণ বনাম বাণিজ্য এই দ্বৈত নীতির সমন্বয় নেই। এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ইলিশ কি শুধুই বাণিজ্যিক পণ্য, নাকি একটি প্রাকৃতিক সম্পদও? যদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার মাছ ধরার ওপর মৌসুমভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তবে সেই নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পরে বাজারে কেন এমন দামবৃদ্ধি ঘটে? এখানে মজুতদার ও জাল ব্যবসায়ীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে হবে। ইলিশের ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারলে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, জেলেরাও লাভবান হবে। কারণ তখন প্রকৃত উৎপাদক ন্যায্য দাম পাবে, মধ্যস্বত্বভোগীরা বাজার থেকে হারিয়ে যাবে, আর ক্রেতা পাবে নির্ভরযোগ্য মানের মাছ নির্ধারিত মূল্যে।
ইলিশ শুধু একটি মাছ নয়, এটি আমাদের ঐতিহ্য, গর্ব এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভের প্রতীক। এ সম্পদকে যদি আমরা বাজারের নৈরাজ্যে নষ্ট হতে দিই, তবে তা হবে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, সাংস্কৃতিক অপচয়ও বটে। তাই এখনই প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ, বাস্তবভিত্তিক নীতিমালা ও কঠোর প্রয়োগ। তাহলেই হয়তো কোনো একদিন আমরা বাজারে গিয়ে বলতে পারব, ইলিশ কিনছি নির্ধারিত দামে, প্রতারণা ছাড়াই।
তবে ইলিশের এর উৎপাদনে মূলত আহরণ ও পরিবহন ব্যয়ই জড়িত, তাই দেশব্যাপী একটি যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করা হলে ভোক্তারা সাশ্রয়ী মূল্যে ইলিশ কিনতে পারবেন এবং বাজারেও স্থিতিশীলতা আসবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ইলিশ বাজারে নৈরাজ্য কমবে এবং ভোক্তারা স্বস্তিতে মাছ কিনতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইলিশের উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে হবে। এখনো বহু জেলেপাড়ায় ‘ইলিশ নিষেধাজ্ঞা’ মৌসুমে সরকারি সহায়তা সঠিকভাবে পৌঁছায় না, ফলে তারা বাধ্য হয়ে চোরাপথে মাছ ধরে। এ অবস্থা বন্ধ না হলে বাজারে একক দামের স্বপ্নও অধরাই থেকে যাবে।
ইলিশের মতো রসনাপ্রিয় মাছ ইউনেস্কো ঐতিহ্যখাতা অলংকৃত, স্বাদেগন্ধে অতুলনীয়, সুনামধন্য আমাদের জাতীয় মাছের বাজার বিশৃঙ্খলায় ছেড়ে দিলে তা শুধু ভোক্তাদের ঠকানো নয় বরং একটি জাতির ঐতিহ্যকেই লুণ্ঠনের শামিল। একক দাম শুধু অর্থনৈতিক সমতা নয়, তা একটি সাংস্কৃতিক মর্যাদার প্রশ্ন যার সুরক্ষা দান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
লেখক : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের প্রফেসর ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন। [email protected]
এইচআর/এমএস

 1 month ago
8
1 month ago
8





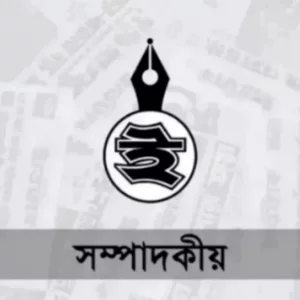



 English (US) ·
English (US) ·