বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাম্যবাদী চেতনার উপন্যাস ‘মৃত্যুক্ষুধা’। উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু হলো দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার মধ্যে নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। উপন্যাসটি সওগাত পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক মুদ্রিত হয়। বই আকারে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯৩০ সাল) প্রকাশিত হয়।
কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের একটি বস্তিতে দরিদ্র মুসলিম পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। যেখানে বৃদ্ধা মা, বিধবা পুত্রবধূ ও তাদের সন্তানদের জীবনযাত্রার কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রেম, রোমান্টিকতা এবং সামাজিক বিদ্রোহের মতো উপাদানও বিদ্যমান।
উপন্যাসের প্রধান পটভূমি হলো তৎকালীন বাংলার এক বস্তি, যেখানে মানুষের জীবনযাত্রা দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের ছোবলে জর্জরিত। একটি দরিদ্র মুসলিম পরিবারের জীবন সংগ্রামের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য সংগ্রাম করে। উপন্যাসে নারী জীবনের দুর্বিষহ অন্ধকার এবং সমাজের বাস্তবচিত্র তুলে ধরা হয়।
কাহিনিতে দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গভীর সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের টিকে থাকতে সাহায্য করে। প্যাঁকালে নামের এক যুবকের সঙ্গে কুর্শি নামের এক খ্রিষ্টান মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক প্রতিভাত হয়েছে। যা উপন্যাসে একটি রোমান্টিক ছোঁয়া যুক্ত করেছে। এ ছাড়া আনসার ও রুবির প্রেমকাহিনিও পাঠককে নাড়া দেয়।
আরও পড়ুন
উপন্যাসের চরিত্রগুলো শুধু দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার নয়। তারা সামাজিক অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। উপন্যাসটি কাজী নজরুল ইসলামের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে রচিত। যেখানে তিনি বস্তি এলাকার জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি মাত্র তিনটি উপন্যাস লিখেছেন। যেমন- ‘বাঁধন হারা’, ‘মৃত্যুক্ষুধা’ ও ‘কুহেলিকা’। তার মধ্যে মৃত্যুক্ষুধা বহুল পঠিত একটি।
‘মৃত্যুক্ষুধা’ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কবি নজরুল পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে বাস করতেন। সেখানকার চাঁদসড়কের পাশে বিরাট চত্বরওয়ালা একতলা গ্রেস কটেজে তিনি অবস্থান করতেন। উপন্যাসটির প্রথমাংশ কৃষ্ণনগরে এবং শেষাংশ কলকাতায় অবস্থানকালে লিখিত।
‘মৃত্যুক্ষুধা’ প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালের রচনা। এ কারণে যুদ্ধোত্তর যুগের অর্থসংকট, শ্রেণিবৈষম্য, নগরচেতনার প্রকাশ এবং উপলদ্ধিতে সার্থক। এ উপন্যাস রচনায় নজরুলের দ্বৈতসত্তা পাশাপাশি কাজ করেছে। উপন্যাসের চরিত্র, প্লট ও ভাষা জীবনস্পর্শী। এর ভাষা একান্তই নজরুলীয় বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ। চরিত্রের স্বাভাবিকতার স্বার্থে যার যার মুখে যে সংলাপ প্রযোজ্য, তা-ই রাখতে সচেষ্ট ছিলেন নজরুল।
ভাষায় যমক, শ্লেষ, উৎপ্রেক্ষা বা অলঙ্কার বিশিষ্টতা নজরুলের গদ্য রচনার অনন্যতা। প্রাত্যহিক শব্দের নতুনতর ব্যঞ্জনা এবং ভাষার ধ্বনিময়তা উপন্যাসের গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দারিদ্র্যের চিত্র, সাম্য ও বিপ্লবী চেতনা এ উপন্যাসের রূপকল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই উপন্যাসটি এখনো সুখপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত।
এসইউ/এমএস

 2 days ago
4
2 days ago
4


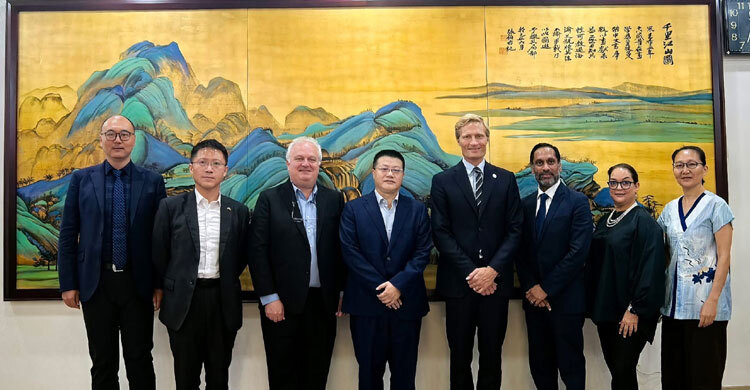






 English (US) ·
English (US) ·