ফারজানা অনন্যা
আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর হাতেই ঘটে বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল মুক্তি। বাংলা সার্থক ছোটগল্পের রচয়িতা তিনি। বাংলা সাহিত্যে শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়োত্তীর্ণ লেখক; যাঁর সাহিত্যকর্মের সূচনালগ্ন থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ রচনায় নারীর বিচিত্র জীবন, পরিচয় ও তাদের বিবর্তিত রূপ অঙ্কিত হয়েছে। ‘গল্পগুচ্ছ’, ‘গল্পস্বল্প’, ‘সে’ এবং ‘লিপিকা’ গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পেই প্রকাশিত হয়েছে নারীর বহুমাত্রিক রূপ। তাঁর গল্পের নারীরা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। পুরুষ চরিত্রের আধিপত্যে রবীন্দ্র-গল্পের নায়িকারা ম্লান হয়ে যায়নি। রবীন্দ্র-গল্পে ‘নারী’ উপলক্ষ হিসেবে আসেনি, এসেছে কেন্দ্রস্থ লক্ষ্য হিসেবে।
রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে অবিস্মরণীয় সব নারী চরিত্র। বিশেষত ছোটগল্প শাখাটিতে নারী এসেছে মমতাময়ী, কোমলমতি, স্নেহশীল, প্রেমিকা, এমনকি নীতির প্রশ্নে আপসহীন সত্তা রূপে। যেখানে উনিশ শতকের অন্য সাহিত্যিকরা নারীকে দেখেছেন তাঁদের কাব্যপ্রেরণার অংশ হিসেবে, নারীকে পুরুষের ছায়ামাত্র ভেবেছেন; সেখানে রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক অনেক লেখকের চেয়ে নারীকে এঁকেছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি নারীকে করেছেন কেন্দ্রীয় চরিত্র। পুরুষের ছায়াসঙ্গী হিসেবে না দেখিয়ে দেখিয়েছেন পথচলার সঙ্গী হিসেবে। নারী অধিকার উপস্থাপিত হয়েছে অকল্পনীয় মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মদৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর নারীরা যেমন একদিকে কোমলমতি; অন্যদিকে স্বাধীনচেতা, প্রগতিশীল এবং প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যুগের তুলনায় আশ্চর্যরকমের অগ্রসর।
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতিবাদী ও সচেতন নারী চরিত্রের উপস্থিতিতে পরিবারের নারীদের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রধান রসদ জুগিয়েছে তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবন। কবিতার মতো গল্পেও আবিষ্কার করা যায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবনবীক্ষণ। ইউরোপের নারী আন্দোলনের প্রভাব অথবা নিজস্ব কর্তব্যবোধ যেটাই হোক, রবীন্দ্রনাথ নারীকে স্বাধীন কর্মপরিবেশ এবং বাঁচার স্পর্ধিত অধিকার দানে প্রয়াসী ছিলেন। বহু নারীর আগমন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে। তবে সবাই যে গৃহের দাবি নিয়ে এসেছেন এমন নয়। নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি নারীর ভালোবাসা ছিল বহুমাত্রিক। তাঁর জীবনে আসা নারীর সুদীর্ঘ তালিকায় রয়েছে মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা, ভক্ত, বৌদি, বন্ধু এবং একাধিক প্রেমিকা। রবীন্দ্র গবেষকদের মতে, ব্যক্তিজীবনে ঠাকুরবাড়ির নারীদের মধ্যে প্রতিবাদী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রের মধ্যে বউদি কাদম্বরী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, বোন স্বর্ণকুমারী দেবী, বোনঝি সরলা ঘোষাল, ভাইঝি ইন্দিরা দেবী, স্ত্রী মৃণালিনী দেবী, কন্যা মাধুরীলতা, রেনুকা, মীরাদেবী প্রমুখের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে নারী থেকে গৃহীত আঘাত ও আনন্দকে তিনি শিল্পের শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহারা হতে দেখা যায়নি। এ কারণে গান, কবিতা থেকে শুরু করে গ্রন্থ পর্যন্ত ব্যক্তিজীবনের সাথে জড়িত নারীদের নামে রচিত ও উৎসর্গীকৃত।
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারী চরিত্রের পদচারণা বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীর প্রতি সমাজ কিংবা ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে ‘পুরুষতান্ত্রিক-ক্ষমতাকাঠামো’। নারী চরিত্রের সাথে পুরুষতন্ত্রের উৎপীড়ন বা আগ্রাসী মনোভাব বরাবরই সম্পর্কযুক্ত থেকেছে। পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন কোনো কোনো নারী। আবার কোনো কোনো নারী পুরুষতন্ত্রের বীভৎস সহিংসতায় অতলে ডুবেছেন। রবীন্দ্র-গল্পে নারী কখনো জ্বলন্ত অঙ্গাররূপে আবির্ভূত সমাজের প্রথাগত ধারাকে পুড়িয়ে দিতে আবার রবীন্দ্র-গল্পের নারীই কখনো কখনো সমাজের স্বার্থপর ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গিতে ভেঙে পড়া অভিমানী রূপে প্রতীয়মান। নারীর সত্তা অনুযায়ী গল্পের নারীদের মোটা দাগে প্রধানত দু’ভাগে ভাগ করা যায়: ক. সনাতন বা প্রথাগত নারী এবং খ. প্রথামুক্ত নারী।
রবীন্দ্র-ছোটগল্পে সামাজিক শোষণ ও অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রথামুক্ত নারী চরিত্র হলো: ‘অপরিচিতা’ গল্পের কল্যাণী, ‘পয়লা নম্বর’ গল্পের অনিলা, ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের মৃণাল, ‘শাস্তি’ গল্পের চন্দরা, ‘দেনা-পাওনা’ গল্পের নিরুপমা প্রমুখ। সমাজের স্বার্থপর ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গিতে ভেঙে পড়া আত্মসমর্পিত অসহায় নারী চরিত্র হলো: ‘হৈমন্তী’ গল্পের হৈমন্তী, ‘জীবিত ও মৃত’ গল্পের কাদম্বিনী, ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের রতন, ‘সুভা’ গল্পের সুভাষিণী, ‘নষ্টনীড়’ গল্পের চারুলতা, ‘সমাপ্তি’ গল্পে মৃন্ময়ী, ‘রবিবার’ গল্পের বিভা, ‘ঘাটের কথা’ গল্পের কুসুম, ‘খাতা’ গল্পের উমা, ‘মণিহারা’ গল্পের মণি প্রভৃতি।
পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, অপমান, অনাদর, অবমাননা, সুখ-দুঃখ, বঞ্চনা এবং সেইসঙ্গে প্রতিক্রিয়া, প্রতিবাদ, আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, আত্মমর্যাদা ও অসম্মান আহরণের বিচিত্র মিথস্ক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে। বহু বিচিত্র নারীর দেখা মেলে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে। এর মধ্যে বেশ কিছু নারী চরিত্র সম্পর্কে বলা যেতে পারে, তারা সময়ের চেয়ে অগ্রসর। একশ বছর পেরিয়েও তারা আধুনিক। শুধু গল্পসাহিত্যে নয়, রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নাটক ও উপন্যাসে নারীর আপসহীন কণ্ঠস্বর শোনা গেছে বারবার। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের কুমুদিনী, ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্য, ‘দৃষ্টিদানে’র কুমু, ‘গোরা’র সুচরিতা, ‘ঘরে-বাইরে’র বিমলা, ‘চোখের বালি’র বিনোদিনী, নাট্যসাহিত্যে ‘রক্তকরবী’র নন্দিনী, ‘চিত্রাঙ্গদা’র চিত্রাঙ্গদা, ‘মায়ার খেলা’র প্রমদা প্রমুখ চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমর্পণ করেছেন নারীমুক্তির মোক্তারনামা। তাঁর বিশাল সাহিত্য ভান্ডারে নারীকে যেমন বৈচিত্র্যময় রূপে উপস্থাপন করেছেন, তা আরও একশত বছর পরেও বাঙালির জীবনে প্রাসঙ্গিক ও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকবে।
‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের মৃণাল বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। মৃণালের জীবনটা কোনোদিন ঠিক গতিতে চলেনি। মেয়ে হয়ে জন্মানোর কারণে শিশুকাল থেকেই অনেক কটুকথা হজম করতে হয়েছে। পরিবার সমাজ কটুকথা বলতে দুবার ভাবেনি। মৃণাল মনোবল হারানোর মেয়ে নয়। তাই প্রতিবাদই হয়েছে তার একমাত্র ভাষা। কিন্তু এই মৃণাল সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে চলতে পারেনি। ছোটবেলায় সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগে তার ভাইটি যখন মারা গেলো এবং একই রোগে ভুগে মৃণাল ফিরে এলো, তখন পরিবার-সমাজ সেটাকে বেশ সুবিধার মনে করেনি। বরং অল্পবয়সী মেয়েটির প্রতি চালিয়েছে সামাজিক শোষণ! নারী হয়ে জন্মালে ক্ষয় নেই, তাই সে বেঁচে গেছে। কিন্তু মৃণালকে যারা কটুবাক্যে জর্জরিত করেছে, তাদের অধিকাংশই নারী! মৃণাল অজপাড়াগাঁ থেকে উঠে আসা একটি মেয়ে। তার বাবার বাড়ি পূর্ববঙ্গের গ্রামে। ‘বাঙাল দেশের রান্না’ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে কবিপত্নী মৃণালিনীর কথা। তিনিও খুলনার গ্রামের মেয়ে। তাকেও অভিজাত ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে অনেক বাঁকা কথা শুনতে হয়েছিল ‘বাঙাল দেশের মেয়ে’ হিসেবে। জমিদার পরিবারের মেজ বউ মৃণাল ছিল অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু সে যে সুন্দরী সে কথা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দ্রুত ভুলে গেলেও, সে যে বুদ্ধিমতী সেটা তারা ভুলতে পারেনি। মৃণাল সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধির অধিকারিণী। তাই অন্যায় দেখলে এর প্রতিবাদে সত্য কথাটি সে সহজে উচ্চারণ করতে পারে। তাই শ্বশুরবাড়িতে তাকে প্রতি পদে হেয় করার চেষ্টা চলে। তবে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মৃণাল সেসব তুচ্ছ করে প্রতিবাদী ভূমিকা ধরে রাখে। অসহায় নিরাশ্রয় মেয়ে বিন্দুকে আশ্রয় দেয়। বিয়েই নারী জীবনের মুক্তি এমন ধারণা থেকেই বিন্দুর বিয়ে আটকানো সম্ভব হলেও মৃণাল তা করেনি।
বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বিন্দুকে এক পাগলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়ায়। বিয়ের পর যখন বিন্দু আবিষ্কার করে তার স্বামী পাগল; তখন আশ্রয় হিসেবে মৃণালের কাছেই ছুটে এসেছে। বিন্দু পালিয়ে এলে মৃণাল তাকে আশ্রয় দেয় সবার সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করেই। পাগল স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত বিন্দু শেষপর্যন্ত গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু নারীর জীবন দোষময়। তার সব কাজের মধ্যে খুঁত খুঁজে বের করা সমাজের স্বভাব। তাই আগুন লাগিয়ে অসহায় বিন্দু মরে গেলেও সমাজ তাকে ছেড়ে কথা বলেনি। বরং পাগল পুরুষের সংসারে কেন জীবনকে নিঃশেষ করে দিলো না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। দেশসুদ্ধ লোক চটে গিয়ে বলেছে, মেয়েদের গায়ে আগুন লাগিয়ে মরা ফ্যাশান! কী আজব সমাজ! কী আজব দেশ! যেখানে নারীর মরণও স্বাভাবিক রূপে নেয় না কেউ। বিন্দু বেঁচে থাকতে যারা নাক সিটকিয়েছে; তারাই সে মরলেও প্রশ্ন তুলেছে। সংসারে নারীর অবস্থান যে কত দুঃসহ তা নতুন ভাবে উপলব্ধি করে মৃণাল। একসময় সাংসারিক বন্দিদশা থেকে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। সে পুরীর তীর্থক্ষেত্রে চলে যায়। বাঙালি ঘরের একজন কুলবধূর এই সাহসী ভূমিকা ছিল চমকপ্রদ। মৃণাল আগাগোড়া বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। এই বিদ্রোহ স্বামীর পরিবারের নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে যেমন; তেমনি রুগ্ন মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ-সমাজের বিরুদ্ধেও। বিন্দুর প্রতি সবার অমানবিক ব্যবহার দেখে মৃণাল মধ্যযুগীয় মূল্যবোধহীন সমাজের চেহারাটা উপলব্ধি করেছে। এই জন্য সব রকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ। মৃণাল বিন্দুকে দেখে উপলব্ধি করেছে সংসারে নারীদের অবস্থান কোথায়! এই জন্যই পত্নীত্ব থেকে নারীত্বের মহিমায় তার মুক্তিসন্ধান। মৃণাল নিজেই বলে সে আত্মহত্যা করবে না বরং স্বাধীনভাবে বাঁচবে। ‘মীরাবাইকে তো বাঁচার জন্য মরতে হয়নি’।
প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিজেও অন্বেষণ করছিলেন নারীর মুক্তির পথ। সে কি সংসারে যাঁতাকলে পিষ্ট হতেই থাকবে? ‘রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা’র চক্র থেকে নারীকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু সেই মুক্তি কি কেবল ধর্মের পথে? না, তা নয়। নারীর মুক্তি তার স্বাধীন জীবনে। তার কর্মের সাধনায়। সেই পথই খোঁজে ‘অপরিচিতা’র কল্যাণী। কল্যাণী বাঙালি নারীর চিরাচরিত বিয়ে ও সুখী সংসারের লোভকে সংবরণ করে বরণ করেছেন নারীশিক্ষার আলোককে পথচলার পাথেয় হিসেবে। যা ওই সময়কার সামাজিক প্রেক্ষাপটে অকল্পনীয় ছিল। ‘অপরিচিতা’ গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই এক বাবা ও তার আদরের মেয়েকে। কল্যাণী সুন্দরী ও শিক্ষিতা। তার বাবা ডাক্তার শম্ভুনাথ অনেকটাই হৈমন্তীর বাবা গৌরসুন্দরের মতো। তিনি বাংলার বাইরে ভারতের অন্য প্রদেশে মাতৃহীন কন্যাকে নিয়ে থাকেন। তবে বাবা ও মেয়ে দুজনেই তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ় মনোভাবের।
কল্যাণীর বিয়েতে তার বাবা পাত্রপক্ষের দাবিমতো যৌতুকের টাকা ও অলংকার দিতে রাজি হন। বিয়ের আসরে পাত্রের মামা বড়কর্তা হিসেবে মেয়ের গা থেকে সব অলংকার খুলে তা মেপে নিতে চায়। দেখা যায় প্রতিশ্রুত পরিমাণের চেয়ে তিনি বেশিই দিয়েছেন। পাত্রপক্ষ সন্তুষ্ট হলেও শম্ভুনাথ বলেন, ‘আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।’ মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তিনি পাত্রপক্ষকে বিয়ের আসর থেকে বিদায় করে দেন। কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শম্ভুনাথ সেনের বলিষ্ঠ প্রত্যাখান গল্পটিকে সার্থক করে তুলেছে। এদিকে পাত্র অনুপম ছিল সুবোধ ভালো মানুষ। মামার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ সে বিয়ের আসরে করতে পারেনি বটে কিন্তু হবু স্ত্রী কল্যাণীকে ভুলতে পারে না। মা এবং মামার আদেশ অগ্রাহ্য করে সে কল্যাণীর সন্ধান করে। কল্যাণীকে অনুপম খুঁজে পায়, তবে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আকস্মিকভাবে। কল্যাণী নারীর শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে। সে বিয়েতে রাজি হয় না। কল্যাণীর সমাজসেবার কাজে অনুপম সহযোগী হয়। বিয়ের আসরে এই গণ্ডগোলের কিছুটা আভাস আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ের বিয়ের আসরের ঘটনায়। মীরা দেবীর স্বামী ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির। বিয়ের আসরে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই অভদ্র ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে মীরা দেবীর সঙ্গেও দুর্ব্যবহারের কারণে তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে। মীরা দেবীর অসুখী দাম্পত্যজীবন রবীন্দ্রনাথকে সব সময়ই পীড়া দিতো। এবং তিনি প্রায়ই ভাবতেন যে, যদি আসরেই বিয়েটি বন্ধ করা যেতো, তাহলে হয়তো পরবর্তীতে এত কষ্টভোগ করতে হতো না। এই ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটে তার ‘অপরিচিতা’ গল্পে।
কল্যাণীই রবীন্দ্র-গল্পের ক্ষেত্রে প্রথম নারী চরিত্র যে দেশকে ‘মা’ ডেকেছে। বিয়ে না করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিয়েছে ‘মাতৃ-আজ্ঞা’। কল্যাণী চরিত্রটি মৃণালের মতোই তেজস্বী ও বিদ্রোহী। কল্যাণী শিক্ষিত সমাজের নারী প্রতিনিধি হয়েও সামাজিক রীতি-নীতি ও বাধ্যবাধকতার বাইরে এসে বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করেছে, ‘আমি বিবাহ করিব না’। কল্যাণীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণ, সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ এবং ভবিষ্যতে নতুন রূপে নারীর আগমনের ইঙ্গিতের আহ্বায়ক ছিল।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সার্থক সামাজিক গল্প ‘দেনা-পাওনা’। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন পণপ্রথার কুফল ও বাঙালি ঘরের বিষময় বেদনার রুদ্ধ ইতিহাস। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিয়ের মতো পবিত্র সামাজিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে জঘন্যতম ব্যবসা করার দৃশ্য এবং এর ভয়াবহ পরিণতির আঁচ পাওয়া যায়। সমাজ-সংসারের নির্মমতার মধ্য দিয়ে গল্পটিতে ফুটে উঠেছে যৌতুকের দায়ে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিরুপমার মৃত্যুর কথা। নিরুপমা বিকশিত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী নারী। গল্পটিতে দেখা যায়, মধ্যবিত্ত বাবা রামসুন্দরের আদরের মেয়ে নিরুপমা। জমিদার রায়বাহাদুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অনেক টাকা পণ স্বীকার করেন বাবা। নিরুপমা সুন্দরী। কিন্তু সেই রূপের কোনো কদর বা আদর তার শাশুড়ির কাছে নেই। চাকরিরত স্বামী থাকে শহরে। প্রসঙ্গত বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতার স্বামী শরৎ ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বেশ মোটা অঙ্কের যৌতুক দিয়েই মাধুরীলতার বিয়ে দিয়েছিলেন কবি। স্বামীর ভালোবাসা পেলেও নিঃসন্তান মাধুরীলতা শ্বশুরবাড়িতে নিগৃহীত ছিলেন। মাধুরীলতা যখন ক্ষয়রোগে ভুগছেন; তখন শ্বশুরবাড়িতে তার অযত্নে অবহেলায় দুঃখ পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এমনকি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে তার সঙ্গেও যথেষ্ট শীতল ব্যবহার করা হয়। তাকে বাইরের ঘরে কাঠের চেয়ারে অবহেলায় বসিয়ে রাখা হতো। দীর্ঘ অপেক্ষা করে মেয়ের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেতেন তিনি। গল্পেও আমরা দেখি, পণের পুরো টাকা দিতে পারেনি বাবা। তাই শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ির প্রবল নির্যাতনের শিকার। নিরুপমার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়েদের অর্থলোভীরা বুঝতে পারে না। বোঝার চেষ্টাও করে না। নিরুপমাকে পিতৃগৃহে নিয়ে যেতে রামসুন্দর শেষপর্যন্ত ভিটেবাড়ি বিক্রি করে রায়বাহাদুরের সমস্ত ঋণ শোধ করতে এসেছিল। প্রকৃতার্থেই এক বাঙালি পিতা চেয়েছিল কন্যার মুক্তি আর কল্যাণ।
প্রবল আত্মসম্মানবোধে উদ্বুদ্ধ বিদ্রোহিনী নিরুপমার পিতার প্রতি আবেদন, ‘বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবেনা, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।’ এই একটিমাত্র সংলাপে নিরূপমার ব্যক্তিত্ব ঝল্সে উঠতে দেখি। বিদ্রোহী আলো প্রজ্বলনের জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিরুপমাকে শাশ্বত বাঙালি নারীর খোলস থেকে বের করে এনেছিলেন। নিরুপমা পুরুষতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে একদিন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ অকালে ঝরে পড়া কুন্দ ফুলের মতো পরপারে চলে যেতে হয় নিরুপমাদের। শেষ পর্যন্ত অবহেলায় নির্যাতনে মৃত্যু হয় নিরুপমার। শেষ দেখাও হয় না পরম প্রিয় বাবার সঙ্গে।
নারীর অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘শাস্তি’ গল্পে। আখ্যানটি সামাজিক, কিন্তু গল্প শেষের প্রশ্নটি মানবিক। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাধনা পত্রিকায়। গল্পের নায়িকার নাম চন্দরা। চন্দরা বাংলা সাহিত্যের একটি বিপ্লবী চরিত্র। দুখিরাম, ছিদাম এবং তাদের স্ত্রী রাধা ও চন্দরাকে নিয়ে অভাবের সংসার তাদের। একদিন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাজ থেকে বাড়িতে ফিরে দুখিরাম রাধার কাছে ভাত চাইলে রাধা কর্কশ স্বরে বলে, ‘ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।’ এই বেদনাময় পরিস্থিতি এবং পুরুষের ক্ষমতাতান্ত্রিক দৃষ্টি রাধা হত্যার ইন্ধন জুগিয়েছিল। দুখিরাম একথা সহ্য করতে না পেরে রাধার মাথায় দা দিয়ে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে রাধা মারা যায়। রাধা মারা যাওয়ার পর ছিদাম ভাইকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত দোষ চন্দরার ওপর চাপিয়ে দেয়। তখন ‘... সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল।’ পুরুষশাসিত সমাজের গর্হিত একটি অপরাধ নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। গল্পে চন্দরার স্বামী ছিদামের সংলাপে পুরুষের কর্কশ স্বার্থবাদী রূপটির উলঙ্গ বহিঃপ্রকাশ ঘটে, ‘ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।’ স্বামীর এ কথা শোনার পরে স্ত্রী চন্দরা স্তব্ধ হয়ে যায়। সে কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারতো। তাকে ফাঁসি দেওয়ার আগে তার ইচ্ছের কথা জিজ্ঞেস করা হলে সে তার মাকে দেখতে চায়। এরপরে যখন তাকে বলা হয় যে, তোমার স্বামী তোমার সাথে দেখা করতে চায়, তখন সে বলে ‘মরণ!’ একটি শব্দের মাধ্যমে চন্দরা প্রতিবাদ জানিয়েছে স্বামীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও এই সমাজের স্বার্থপরতা ও নীচতার বিরুদ্ধে চন্দরার প্রতিবাদ তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত করেছে।
এ কারণেই চন্দরাকে আমি একটি বিপ্লবী চরিত্র মনে করি। হিন্দু শাস্ত্রমতে সাত পাকে ঘুরে যেভাবে বিয়ে হয়; তাতে পুরো জীবন সমর্পণ করে দেওয়ার একটা বিষয় থাকে। কিন্তু যখন একজন নারী দেখে যে সেই বৈবাহিক সম্পর্কে তার মূল্য নেই, তার অস্তিত্বের মূল্য আসলে তার স্বামীর কাছে নৈর্ব্যক্তিক, সে সেখানে একটা পুতুলমাত্র, তখন সে তার নিয়তিকে মেনে নেয়। তার কাছে মৃত্যুটাই এখানে শ্রেয়। সে কারণেই শেষে তার অমোঘ উচ্চারণ ছিল ‘মরণ’। চন্দরার কাছে তুচ্ছ জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক বেশি সম্মানের। চন্দরার সাথে হেনরিক ইবসেনের ‘ডলস হাউজ’ নাটকের নোরা চরিত্রের মিল পাওয়া যায়। যখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পুতুলের সংসার ‘ডলস হাউজ’ থেকে। একজন সাহিত্য সমালোচক বলেছিলেন, ‘নোরা দরজা ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যায় সংসার থেকে, যেখানে তার অস্তিত্বের মূল্য নেই। এই দরজা ধাক্কা দেওয়াটা ওয়াটারলুর কামানের ধ্বনির চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ।’ অস্তিত্ববাদের ক্ষেত্রে চন্দরা চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ‘পয়লা নম্বর’ অত্যন্ত সিদ্ধ একটি প্রতিবাদী গল্প। গল্পে অনিলা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবহেলা এবং লালসাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খুঁজে নিয়েছিল আত্মসম্মানের স্বাধীন জীবনকে। গল্পের কাহিনি পারিবারিক হলেও সামাজিক চেতনায় তা ভরপুর। গল্পের নায়িকা অনিলা। অনিলা বিদ্রোহিনীর প্রতীক। স্বামী অদ্বৈতচরণ ছিলেন স্ত্রীর প্রতি উদাসীন। নিজের পড়াশোনা ও বন্ধুদের নিয়েই ব্যস্ত।
তার স্বামী অদ্বৈতচরণ বিদ্যা-বুদ্ধির চর্চায় বুঁদ হয়ে থাকে ও নিজের দলবল নিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত সময় পার করে। সংসারের আয়-ব্যয়, অভাব-অভিযোগ কোনো কিছুতেই তার মন নেই। তার কয়েকজন শিষ্য গোছের বন্ধু আছে। তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখা, বই পড়ে ব্যাখ্যা করাই তার একমাত্র নেশা। স্ত্রীর চাওয়া-পাওয়ার প্রতি তার ন্যূনতম ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনকি অনিলার সুমধুর গানের গলার কদরও করেনি কখনো। অদ্বৈতচরণের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, যাকে একবার স্ত্রী হিসেবে পাওয়া গেছে; তখন সেই স্ত্রী বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। স্ত্রী সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক ভাবনা তার মধ্যে ছিল না। তার পাশের বাড়ি অর্থাৎ গলির মোড়ের পয়লা নম্বর বাড়িতে বাস করতো সুদর্শন ধনী জমিদার সীতাংশুমৌলী। স্বামীর এরূপ অবহেলার মধ্যেই অনিলার জীবনে আবির্ভাব ঘটে সিতাংশুমৌলির। সে অনিলার প্রেমে পড়ে, তাকে একের পর এক চিঠি পাঠায়। কিন্তু অনিলা কোন সাড়া দেয় না। অনিলার একমাত্র ভাই আত্মহত্যা করে। কিন্তু উদাসীন স্বামী সে খবরটুকুও রাখে না।
একদিকে স্বামীর অবহেলা, অন্যদিকে সিতাংশুর প্রেমের উত্তাল আহ্বান। অনিলা এসব থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছে। অনিলা উদাসীন স্বামীর গৃহত্যাগ করেছে, কিন্তু তাঁর স্তব-ধন্য ঐশ্বর্যময় হৃদয়ের অধিকারী সিতাংশুও তার সাক্ষাৎ পায়নি, এমনকি সাড়াও পায়নি। অদ্বৈতচরণ অনিলাকে দেখেছে সাংসারিক সীমারেখায় নিজের প্রয়োজনে। অপরদিকে সিতাংশু তাকে দেখেছে লুব্ধ দৃষ্টিতে। এ বিষয়ে সমালোচকের বিবৃতি: ‘লেখক অনিলাকে এই দ্বন্দ্ব থেকে অকস্মাৎ সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবজীবনে এই দুর্ঘটনা স্ত্রীর প্রতি উদাসীন স্বামীদের সতর্কতা অর্জনের অভিজ্ঞান হয়ে থাকল। দাম্পত্য জীবনে এই বিরোধ ও ব্যর্থতা আমাদের সমাজের চিরন্তন সংস্কারেরই বিষময় ফল।’
অনিলার স্বামী মনে করে সে সীতাংশুর সঙ্গেই চলে গেছে। কিন্তু অনেক বছর পর সে জানতে পারে তার ধারণা সঠিক ছিল না। অনিলা কোনো পুরুষের হাত ধরে ঘর ছাড়েনি। সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সংসার ত্যাগ করেছে। অনিলা যেমন তার স্বামীকে চিঠি লিখে গেছে ‘আমার খোঁজ করো না’; তেমনই সেদিন সীতাংশুকেও জীবনে একটিমাত্র চিঠিতে একই কথা লিখে গেছে। বন্ধনমুক্তির এই আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এক প্রদীপ্ত প্রতিবাদ। অনিলার এই অন্তর্ধান নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তার নীলখামের চিঠি অপরিমেয় যাতনার প্রতীক। এই যাতনা ও বেদনাই স্বামীর উদাসীনতা ও সিতাংশুর ভাবুক রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দুই মেরুর সংকট নিরসনের জন্য সংসার থেকে পালিয়ে অনিলা হয়তোবা আত্মহত্যা করে। মিথ্যার জগৎ থেকে বের হয়ে অনিলা সত্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। পুরুষের লাঞ্ছনা, অপমান আর কামুক নেশা থেকে মুক্তিকামী নারীর চূড়ান্ত প্রতিবাদ অনিলার সাহসিকতার মধ্য দিয়েই গল্পে রূপায়িত হয়েছে।
একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক নারীরা শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, গবেষণা, শিল্প প্রভৃতি জীবনের সর্বত্রই পুরুষের পাশাপাশি জায়গা দখল করছে। আমরা যদি বিশ্বসংসারকে একটি দ্বিচক্র শকটের সাথে তুলনা করি, তাহলে দেখবো সেই শকটের একদিক যেমন পুরুষেরা সামলাচ্ছে তেমনই নারীরাও পিছিয়ে নেই। আত্মসম্মানবোধ, আত্মঅধিকার, ভোটাধিকার, সামাজিক অধিকার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সবদিক থেকেই নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমঅধিকারের জন্য আওয়াজ তুলছে। এলিজা কার্সনের মঙ্গল অভিযাত্রার প্রস্তুতি, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিসনের নির্বাচিত হওয়া, ট্রেন চালক হিসেবে নারীদের নিয়োগ দান কিংবা ঘরে ও বাইরে নারীর দশভুজার মতো দায়িত্ব পালন নারীর কর্মদক্ষতা এবং অগ্রগতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগে বাঙালি নারীর অগ্রগতি কয়েকটি সূচক হলো:
ক. নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি
খ. নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার
গ. নারীর আত্মসম্মানবোধ তথা মানসিক দাসত্ব মোচন
ঘ. নারীর ভয়হীনতা
ঙ. নারী অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আইন ও পদক্ষেপগ্রহণ প্রভৃতি।
রবীন্দ্রনাথের চন্দরা, কল্যাণী, নিরূপমা, অনিলা, মৃণাল সব চরিত্রই একবিংশ শতাব্দীর নারীর মধ্যে সুপ্ত আছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চেয়েছেন এবং পাঠককেও বোঝাতে চেয়েছেন যে, স্বাধীন ও ক্ষমতায়িত জীবনের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত মুক্তি। এক নারীর পাশে দাঁড়াতে হবে অন্য নারীকে। মানুষ হিসেবে আত্মমর্যাদা নিয়ে নারীদের বেঁচে থাকতে হলে এর গত্যান্তর নেই।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজদৃষ্টি সামাজিক জীবনের ব্যাপকতার অনুসন্ধানী। সামাজিক নানা প্রথার বিরুদ্ধে নারীদের নীরব প্রতিবাদী সত্তা, প্রকাশ্য প্রতিবাদ কিংবা তিরস্কারের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিখুঁতভাবেই তাঁর ছোটগল্পের নারী চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন। আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ এসেছে বিচিত্ররূপে, ভিন্ন কারণে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারী প্রতিবাদের যে মিছিল, তার প্রত্যেকটিই নবজীবনের আলোকশিখায় উদ্ভাসিত। নারীর এই প্রতিবাদ সমাজের বিবেককে নাড়া দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দিয়েছে। সমাজে আজ নারী ব্যক্তিত্ব শক্তভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজ প্রোথিত সংস্কার নারীকে আর পঙ্গু বা জব্দ করতে পারবে না। মুক্তির মর্মসুধা পান করে প্রতিবাদী নারীরা মুক্তির পথের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্র ছোটগল্পে নারীরা যথার্থ জীবনবোধের স্বরূপ উন্মোচন করেছে প্রতিবাদের মাধ্যমে। সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ ও নারী মুক্তি আজ একই স্রোতে বহমান। আপন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে গিয়েই নারীরা প্রতিবাদী হয়েছে। করুণার পাত্রী হয়ে নারীদের পুরুষের নিগ্রহ ভোগ করার দিন শেষ হয়ে এসেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের নির্যাতনের মুখে নারীরা আজ সংগ্রামী। রবীন্দ্রনাথের এই নারী চরিত্রেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমাজে তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রয়াস চালিয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা ব্যবহার করে পুরুষ সমাজের নীচতা ও হীনতার প্রতি ধিক্কার জানিয়েছে। প্রতিবাদী নারীরা বুঝিয়ে দিয়েছে এই সমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন নয় বরং সমাজেরই পরিপূরক। মানুষ হিসেবে নারীরা স্বতন্ত্র। প্রতিবাদী নারীদের মূল অনুপ্রেরণাই হলো নারী মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে রূপায়িত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ নারীকে দিয়েছে স্বতন্ত্র ও মুক্ত জীবনের সন্ধান।
তথ্যসূত্র:
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড সংকলন), সাহিত্যকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।
২. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ২০০৭, মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ও অন্যান্য, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা।
৩. মুহম্মদ মজির উদ্দীন, ১৯৭৮, রবীন্দ্র-ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ-চেতনা, সিটি লাইব্রেরি, ঢাকা।
৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০১৪, অশেষ রবীন্দ্রনাথ, নান্দনিক প্রকাশন, ঢাকা।
৫. শিশিরকুমার দাশ, ১৯৮৩ বঙ্গাব্দ, বাংলা ছোটগল্প, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৬. অজিতকুমার চক্রবর্তী, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, গল্পগুচ্ছের পুনর্মূল্যায়ন, আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, কলকাতা।
এসইউ/জিকেএস

 1 month ago
10
1 month ago
10

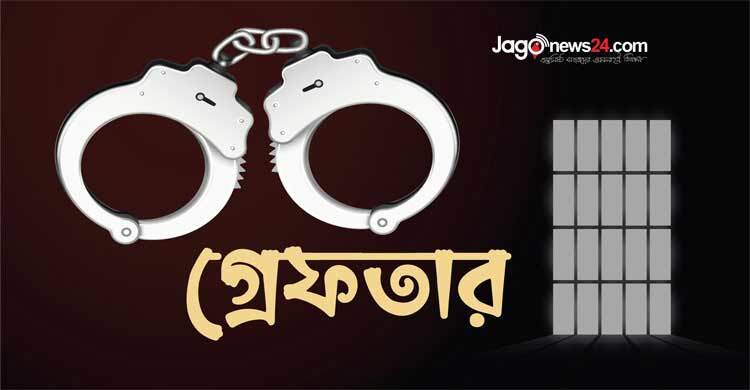




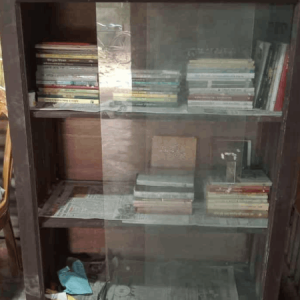


 English (US) ·
English (US) ·