উপদেষ্টা পরিষদ রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত ছাড়াই যে ১২১টি সংস্কার প্রস্তাবকে ‘আশু বাস্তবায়নযোগ্য’ ঘোষণা করেছিল, দীর্ঘ দিনেও সেগুলো বাস্তবায়ন হয়নি। পাঁচটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ থেকে উপদেষ্টা পরিষদ এই সুপারিশগুলো নিজেরা সরাসরি বাস্তবায়নের জন্য বাছাই করে। কিন্তু এ নিয়ে দীর্ঘদিন আর কোনো অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায়নি।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতের সংস্কার। সেজন্য গঠন করা হয়েছে ১১টি সংস্কার কমিশনসহ বিভিন্ন টাস্কফোর্স ও কমিটি। এসব কমিশন, টাস্কফোর্স ও কমিটি তাদের নির্ধারিত মেয়াদ শেষে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনগুলোয় সংস্কারের জন্য নানা সুপারিশ প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পরও কোনো খাতে সংস্কার কার্যক্রমের প্রভাব সেভাবে দৃশ্যমান নয়।
এতে নানা সময়ে সরকারের কার্যক্রম সমালোচিত ও প্রশ্নবিদ্ধও হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের সরকারের কাছে যে বৈষম্যহীন, অন্তর্ভুক্তি ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রের প্রত্যাশা করেছিল জনগণ, সময়ের ব্যবধানে সে প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অন্যদিকে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সে হিসেবে বর্তমান সরকারের মেয়াদ বড় জোর ছয় মাস। বাকি সময়ে সরকার কীভাবে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
জুলাই অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয়েছিল সরকারি চাকরিতে বিদম্যান কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। মূলত শ্রমবাজারে প্রবেশের ন্যায্য সুযোগের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন শিক্ষার্থীরা, যা পরবর্তী সময়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। কিন্তু এ অভ্যুত্থানের এক বছর পর এসেও কর্মসংস্থানের চিত্র একই রয়ে গেছে। বিনিয়োগেও মন্দা ভাব রয়েছে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ৬ শতাংশের ঘরে নেমে এসেছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারের কোনো উদ্যোগ কার্যকর হয়নি।
সম্প্রতি নাগরিক প্লাটফর্ম ‘বাংলাদেশ রিফর্ম ওয়াচ’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা ও নীতিনির্ধারকরাও একই সংশয় প্রকাশ করেছেন। আশঙ্কা প্রকাশের পাশাপাশি বক্তারা সরকারের ইচ্ছা, সক্ষমতা এবং অগ্রাধিকার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে প্রান্তিক, সংখ্যালঘু ও সমাজের নানা স্তরের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বার্থ সংস্কার প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত না হওয়ার কথা তাদের বক্তব্যে উঠে আসে। দেশের বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বক্তাদের কথাগুলো উপক্ষো করার সুযোগ কম।
বিগত সরকারের দেড় দশকের শাসনামলে দেশের রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ প্রায় প্রতিটি খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অতিমাত্রায় রাজনৈতিকীকরণ, অর্থনীতিতে ব্যাপক মাত্রায় দুর্নীতি, লুটপাট, অর্থ পাচার, জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, বিরোধী দল ও মত দমনে গুম-খুন সব মিলিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নাজুক হয়ে উঠেছিল।
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ সরকারের পতন ঘটেছে। এ সরকারের রেখে যাওয়া পরিস্থিতি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। স্বাভাবিকভাবে এক বছরে দীর্ঘ দেড় দশকে সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে পুরোপুরি উত্তরণ সম্ভব নয়। তবে সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে কিছু অগ্রাধিকার ঠিক করতে পারত। অগ্রাধিকার বা সংস্কার কার্যক্রমের পথনকশা নির্ধারণ না করায় কোনো কাজই যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি, যা জুলাই অভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের বড় ব্যর্থতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে না পারা। অভ্যুত্থান চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনমন ঘটেছিল তা সরকার নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। এ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পরবর্তী এক বছরে দেশে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৭৮৮টি মামলা হয়েছে বলে পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩ হাজার ৮৩২টি খুন, ৪ হাজার ১০৫টি ধর্ষণ এবং পুলিশের ওপর হামলার ৫২০টি মামলা।
বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে অন্তত ১৪১টি মবের ঘটনায় ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩৩০টি, যার মধ্যে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ছিল ৬৬টি। এর মধ্যে ২২টি হলো ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা। এছাড়া এ সময় রাজনৈতিক সহিংসতায় মারা গেছে ৪৪ জন।
বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। নানা দাবিতে আন্দোলনরতদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গেও সেনাবাহিনী ও পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে চলেছে। সম্প্রতি একজন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। অথচ গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে জনমনে সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা ছিল পুলিশ সংস্কার নিয়ে। জনগণ চেয়েছিল ‘মানবিক’ পুলিশ। প্রত্যাশা ছিল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে। সংঘাত-সংঘর্ষ কমে আসবে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে সরকার। কিন্তু এর কিছুই হয়নি। বর্তমানে পুলিশ তুলনামূলক সক্রিয় হলেও সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটেনি। নানা মহল থেকে পুলিশকে আবারো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।
অপর দিকে প্রশাসনিক সংস্কার ঘিরেও প্রত্যাশা ছিল। সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরপর যেভাবে রদবদল শুরু করে সে তুলনায় প্রশাসনে গতি ফেরেনি। বরং আগের সরকারের মতোই প্রশাসনে কর্মকর্তাদের পদায়ন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। একটা সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা অন্তর্বর্তী সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু কেবল সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বা নির্বাচিত সরকার শাসনভার নিলে দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটবে এমন নিশ্চয়তা নেই। কারণ অতীতেও নির্বাচিত সরকারকে স্বৈরশাসক হতে দেখা গেছে। আর এর পেছনে অবদান রেখেছিল আমলাতন্ত্র ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাই নির্বাচনের আগে শক্তিশালী আমলাতন্ত্র ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তুলবে সরকার—এমন চাওয়া ছিল, যাতে নির্বাচিত কোনো সরকার ফের পুলিশ-প্রশাসনকে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারের কাজের অগ্রগতি মোটেও সন্তোষজনক নয়।
বিগত সরকারের শাসনামলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের অর্থনীতি। ব্যাংক ও আর্থিক খাতে লুটপাটের কারণে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। দেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচারের তথ্য উঠে এসেছে অর্থনীতির শ্বেতপত্রে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ ৩০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। জনমনে দেশের অর্থনীতির সংস্কার ও পুনরুদ্ধার ঘিরেও প্রত্যাশা ছিল। ব্যাংক খাতের সংস্কারে সরকার বেশ অগ্রগতি দেখিয়েছে। অর্থ পাচার, দুর্নীতি কমিয়ে এনেছে। কিন্তু উচ্চ মূল্যস্ফীতির হার এখনো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনতে পারেনি। কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ পরিস্থিতিতেও কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আসেনি। উল্টো বেকারত্ব, মজুরিবৈষম্য ইত্যাদি বাড়ছে।
অথচ জুলাই অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয়েছিল সরকারি চাকরিতে বিদম্যান কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। মূলত শ্রমবাজারে প্রবেশের ন্যায্য সুযোগের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন শিক্ষার্থীরা, যা পরবর্তী সময়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। কিন্তু এ অভ্যুত্থানের এক বছর পর এসেও কর্মসংস্থানের চিত্র একই রয়ে গেছে। বিনিয়োগেও মন্দা ভাব রয়েছে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ৬ শতাংশের ঘরে নেমে এসেছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারের কোনো উদ্যোগ কার্যকর হয়নি।
অপর দিকে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে শিল্প খাতবান্ধব উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাস্তবে শিল্প খাতে নানা সংকট ও শ্রমিক অসন্তোষ রয়েই গেছে। জ্বালানি খাতে জাতীয় সক্ষমতা বাড়ানোর পরিবর্তে সরকার বিদেশী ঋণ ও কোম্পানিনির্ভর নীতি অব্যাহত রেখেছে। সব মিলিয়ে সরকারের কার্যক্রমে জুলাই-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনমনে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল তার ছাপ পাওয়া যায়নি। সরকারের উচিত ছিল সর্বাগ্রে সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রাধিকার ও ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা। কার্যত এ কারণে সংস্কারকাজের খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি।
প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, সরকার ইচ্ছে করলে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সুপারিশ অধ্যাদেশ জারি করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারে। বিশেষ করে নির্বাচনসহ অতি জরুরি সংস্কার সুপারিশ যেমন– আরপিও এবং আইনবিধি সংশোধন করতে পারে। আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে অধ্যাদেশ জারি করা যায়।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ গণমাধ্যমে বলেছিলেন, ‘এখন আমরা সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে পর্যালোচনার কাজ শুরু করব। এর পর উপদেষ্টা পরিষদের সেগুলো উপস্থাপন করা হবে।’ কবে এ কাজ শেষ হতে পারে– জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বলতে পারছি না। শেষ হলে জানা যাবে। তবে রাজনৈতিক দলের মতামত ছাড়াই স্বল্প সময়ে যেসব সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সে বিষয়ে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।’
লেখক : সাংবাদিক।
এইচআর/এএসএম

 5 hours ago
6
5 hours ago
6








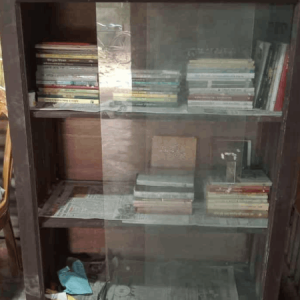
 English (US) ·
English (US) ·