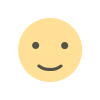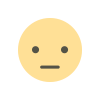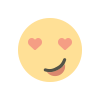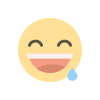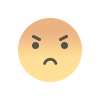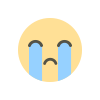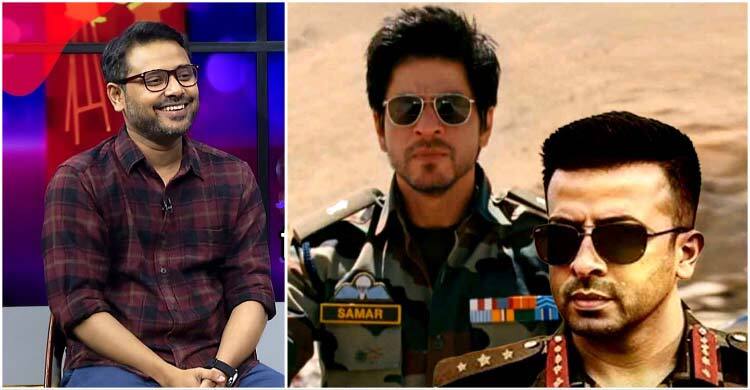বিশ্ব পুরুষ দিবস: একটি মানবিক বিশ্বের দিকে যাত্রা
আজ বিশ্ব পুরুষ দিবস। নানা কারণে দিবসটি গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক চাপ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দিবসটি বিশ্বের অনেকগুলো দেশে পালিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, পুরুষতন্ত্রে চাপ, নির্যাতন, সহিংসতা, পারিবারিক নির্যাতন এগুলো যে শুধু নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে তাই নয়, অনেক পুরুষের জীবনকেও কিন্তু ধ্বংস করে। এই কথায় যাওয়ার আগে ছোট্ট করে একটু পুরোনো কথা মনে করিয়ে দেই। সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য। হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতির নারী ও পুরুষের মধ্যে বায়োলজিক্যালি কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।পুরুষের আছে এক্স ও ওয়াই কক্রোমোজোম। নারীর আছে দুটি এক্স ক্রোমোজোম। নারীর আছে প্রোজেস্টেরন হরমোন বেশি, টেস্টোস্টেরন হরমোন কম। পুরুষের টেস্টোরেন বেশি, প্রজেস্টেরন কম। নারীর প্রজনন অঙ্গ ও পুরুষের প্রজনন অঙ্গ ভিন্ন। ফ্যাট ও পেশীর পরিমাণে কিছু পার্থক্য আছে। সংক্ষেপে বলা যায় নারী ও পুরুষের কিছু বায়োলজিকাল পার্থক্য আছে যেটা প্রাকৃতিক। তাই এই পার্থ্যক্যগুলো মোটের উপর অপরিবর্তনীয়।(আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো পরিবর্তন করতে পারে।) কিন্তু নারী ও পুরুষ বলতে আমরা যে বুঝি ভ

আজ বিশ্ব পুরুষ দিবস। নানা কারণে দিবসটি গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক চাপ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দিবসটি বিশ্বের অনেকগুলো দেশে পালিত হয়।
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, পুরুষতন্ত্রে চাপ, নির্যাতন, সহিংসতা, পারিবারিক নির্যাতন এগুলো যে শুধু নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে তাই নয়, অনেক পুরুষের জীবনকেও কিন্তু ধ্বংস করে।
এই কথায় যাওয়ার আগে ছোট্ট করে একটু পুরোনো কথা মনে করিয়ে দেই। সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য। হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতির নারী ও পুরুষের মধ্যে বায়োলজিক্যালি কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।পুরুষের আছে এক্স ও ওয়াই কক্রোমোজোম। নারীর আছে দুটি এক্স ক্রোমোজোম। নারীর আছে প্রোজেস্টেরন হরমোন বেশি, টেস্টোস্টেরন হরমোন কম। পুরুষের টেস্টোরেন বেশি, প্রজেস্টেরন কম। নারীর প্রজনন অঙ্গ ও পুরুষের প্রজনন অঙ্গ ভিন্ন। ফ্যাট ও পেশীর পরিমাণে কিছু পার্থক্য আছে। সংক্ষেপে বলা যায় নারী ও পুরুষের কিছু বায়োলজিকাল পার্থক্য আছে যেটা প্রাকৃতিক। তাই এই পার্থ্যক্যগুলো মোটের উপর অপরিবর্তনীয়।(আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো পরিবর্তন করতে পারে।)
কিন্তু নারী ও পুরুষ বলতে আমরা যে বুঝি ভিন্ন রকম পোশাক, অলংকার, সাজসজ্জা, ভিন্ন রকম ভূমিকা, অর্থ উপার্জনে ভিন্ন ভূমিকা, চলন বলনে পার্থক্য এর সবটাই সামাজিক। কোনটাই জন্মগত নয়। মোটকথা ‘মেয়েলি’ আর ‘পুরুষালি’ বলতে যা বুঝায় তার অধিকাংশই(বায়োলজিকাল অংশটি বাদ দিলে) সামাজিক।
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার পুরুষ সদসদ্যদের বলে, তোমাকে হতে হবে পুরুষালী। সেটা কেমন? তোমাকে হতে হবে শক্ত সমর্থ, কান্না চলবে না, গৃহস্থালি কাজ তোমার জন্য নয়, সাজসজ্জা তুমি করবে না, সংসারে উপার্জনের দায়িত্বটা পুরোপুরি তোমার কাঁধে ইত্যাদি ইত্যাদি।
ছোটবেলাতেই একটি ছেলে শিশুকে বলা হয়, খবরদার কাঁদবে না। ব্যথা পেলেও না। মনে শত দুঃখ পেলেও কান্না চলবে না। তুমি কি মেয়ে নাকি? তুমি হলে পুরুষ মানুষ। তোমাকে কান্না মানায় না। এই যে তাকে প্রথমেই পুরুষালী শিক্ষা দেয়া এটা কিন্তু অন্তিমকাল পর্যন্ত তার মনের ভিতর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়, আবেগকে অবদমন করে রাখা এটা তার শারিরীক মানসিক অনেক সমস্যারই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বজুড়ে পুরুষের আত্মহত্যার হার নারীর তুলনায় বেশি। এটার অন্যতম কারণও কিন্তু অবরুদ্ধ আবেগ। আমার কথা নয়। এটি মনোবিজ্ঞানীদের কথা।
রবীন্দ্রনাথের গিন্নি গল্পটির কথা মনে পড়ছে। একটি ছোট ছেলে এক বৃষ্টির দিনে তার ছোটবোনের সঙ্গে হাড়িপাতিল দিয়ে রান্নাবাড়ি খেলা খেলছিল। সেই খেলার দৃশ্য দেখে ফেলে স্কুলের পণ্ডিতমশাই। আর যায় কোথায়! ক্লাসের সকলের সামনে ছেলেটিকে ডেকে তাকে চূড়ান্ত উপহাসের পাত্র করে তোলে সেই শিক্ষক। এবং তার নামকরণ করে ‘গিন্নি’। ছেলেটি মনে ভীষণ আঘাত পায়। তার একমাত্র অপরাধ হয়ে দাঁড়ায় এক বৃষ্টির দিনে ছোটবোনের সঙ্গে ‘মেয়েলি’ খেলা। এটি হলো পুরুষতন্ত্রের একটি রূপ যার ভিকটিম একটি পুরুষকেও হতে হচ্ছে। এমন ভিকটিম হওয়ার উদাহরণ আরও দেয়া যায়।
একটি তরুণ যখন বিএ বা এম এ পাস করে তখন অবধারিতভাবে তাকে উপার্জনের জন্য চাকরি খুঁজতে হয় বা ব্যবসা করতে হয়। ‘বেকার’ ছেলের দিকে পুরো সমাজ এমন চোখে তাকায় যেন সে ‘পুরুষ’ হওয়ার অযোগ্য। ঠিক যে চোখে একটি মেয়ের দিকে তাকানো হয় যদি পাত্রপক্ষ তাকে বারে বারে অপছন্দ করে।
সংসারে যে পুরুষ প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারে না আর যে নারী পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে পারে না তাদের দিকে ঘরে বাইরে সকলেই করুণার দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের বিশেষণ হয় ‘অপদার্থ’।
পুরুষ তার স্ত্রীকে বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে এটাই স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। যে পুরুষ নিজের বাবার বাড়িতে নয়, স্ত্রীর বাবার বাড়িতে থাকে তাকে ‘ঘরজামাই’ বলা হয়। ঘরে বাইরে তার লাঞ্ছনার আর শেষ থাকে না।
আর্থিক সাফল্য ও খ্যাতি অর্জনের উচ্চ টার্গেটও পুরুষের জীবনে বড় চাপ সৃষ্টি করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মনে করে যে পুরুষের অর্থ নেই সে ব্যর্থ পুরুষ।
সংসারের অর্থ উপার্জনের পুরো দায় সমাজ চাপিয়ে দেয় পুরুষের উপর। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধগুলো পুরুষকে অর্থ উপার্জক ও নারীকে গৃহকর্মের কুশলী বলে মনে করে। পুরুষের কাজ বাইরে আর নারীর কাজ ঘরে- এটাই সনাতন পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা। আর এরই কারণে কত পুরুষকে যে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে জীবন থেকে বিদায় নিতে হয়। কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ছে। ঢাকাতেই এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যক্তি ব্যবসায় নিঃস্ব হয়ে আত্মহত্যা করেন। তার স্ত্রী ছিলেন গৃহবধূ, সন্তানরা স্কুল পড়ুয়া। বাড়িভাড়া দিতে পারেননি ভদ্রলোক। স্ত্রীও নাকি বলেছিলেন, বউ ছেলেমেয়েকে খাওয়াতে না পারলে, গলায় দড়ি দিতে। অথচ কত সহজ সমাধান ছিল। যদি তার স্ত্রী এবং তিনি দুজনেই অর্থ উপার্জনের দায়িত্বে থাকতেন, তাহলে একজনের আয় বন্ধ হলেও অন্যজনেরটা দিয়ে কোনভাবে সংসারটা চালিয়ে নেয়া যেত। কিন্তু সামাজিক কিছু বস্তাপচা ধারণা পুরুষের নারীর এবং বলতে গেলে সকল মানুষের জীবনকেই কঠিন করে তোলে।
পুরুষতন্ত্রের এসব ক্লিশে ধারণা থেকে বেরিয়ে একটি মানবিক বিশ্ব গঠনে কি এগিয়ে যেতে পারি না আমরা?
লেখক: কবি, সাংবাদিক। চীনে শিক্ষকতা করছেন।
এইচআর/জেআইএম
What's Your Reaction?