চাঁদাবাজি আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। কোনো কোনো ছাত্র সংগঠনের কারো কারো বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ কত ধরনের অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার কত অভিযোগই তো আমরা আগে শুনেছি। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র সংগঠনের একজন নেতা তো গৌরব করে ধর্ষণের সেঞ্চুরি করার কথা দেশবাসীকে জানিয়েও তেমন লজ্জা বোধ করেনি। সেসব ‘নষ্ট’ দিন অবশ্য এখন বাসি হয়েছে। দুঃশাসকের বিদায়ে খারাপ শাসনের ধারারও অবসান হওয়ারই কথা।
হিসাব মতো, একবছর ধরে আমরা এক নতুন বাংলাদেশে আছি। গত বছর জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ থেকে দুঃশাসন, চাঁদাবাজি, লুটপাটের অবসান হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু গত ২৬ জুলাই রাজধানীর অভিজাত গুলশান এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য শাম্মী আহমেদের বাসায় ‘সমন্বয়ক’ পরিচয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে পাঁচ তরুণ আটক হওয়ার পর চাঁদাবাজির বিষয়টি নতুন করে সামনে এসেছে। মানুষের মনে আবার অতৃপ্তি ‘শেষ হইয়াও হইলো না শেষ'। এ কেমন বাংলাদেশ! গুলশানে চাঁদাবাজির ঘটনায় আটক পাঁচজনের মধ্যে চারজন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। এদের কারও বয়স কুড়ি পার হয়নি। সবচেয়ে আশঙ্কাজনক তথ্যটি হলো— এই সংগঠনের একজন সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমার ফেসবুক পোস্ট, যেখানে তিনি জানান, অভিযুক্তদের মধ্যে অন্তত একজনের বিরুদ্ধে এর আগেও ভাঙচুর, হুমকি ও নারীঘটিত অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছিল এবং সেসব অভিযোগ অভ্যন্তরীণভাবে ‘জেনে’ ও ‘দেখেও’ সংগঠনটি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।
এই ছেলেগুলোকে মিছিলে সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে দেখা গেছে, নেতাদের প্রটোকল দিতে দেখা গেছে, এবং কনফারেন্স হল থেকে সচিবালয়ের করিডোর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণ করতে দেখা গেছে। এমনকি উমামার ভাষ্যমতে, গুলশান-বনানীর তথাকথিত গ্যাং কালচারে এই তরুণদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই সংগঠনের ভেতরে অভিযোগ ছিল। তারা মেয়েদের হয়রানি করেছে, সহকর্মীদের হুমকি দিয়েছে এবং প্রয়োজনে পেশিশক্তি ব্যবহার করে চাঁদা আদায়ের কাজ করেছে। এসব অভিযোগের বিপরীতে সংগঠনের আচরণ ছিল পুরোটাই রহস্যঘেরা, দেখেও না দেখার ভানে ভরা। কোনোরকম তদন্ত হয়নি, কোনো সাংগঠনিক জবাবদিহি তৈরি হয়নি। বরং এইসব তরুণ তথাকথিত ‘সমন্বয়ক’ পরিচয়ে অব্যাহতভাবে দাপট দেখিয়ে এসেছে। এ যেন এক নির্মম বিদ্রুপ— যেখানে অপরাধীই হয়ে ওঠে নীতি নির্ধারক।
আজ প্রয়োজন, রাজনীতিকে নতুন করে পড়া, বোঝা এবং রক্ষা করা। যারা সত্য বলে, যারা অন্যায় দেখে প্রশ্ন তোলে, যারা পদ চায় না, ন্যায়ের কথা বলে— তাদের জন্য জায়গা তৈরি করতে হবে। ছাত্র রাজনীতি মানে কেবল পদ-পদবি নয়, বরং একটি আদর্শিক প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হলে, ছাত্র রাজনীতি আবারও হয়ে উঠবে ছদ্মবেশী লুটেরাদের আখড়া। এই সম্ভাব্য পরিণতির আগেই আমাদের সতর্ক হতে হবে, সাহসী হতে হবে এবং নতুন আলো হাতে তুলে নিতে হবে।
এই অবস্থান থেকে যদি আমরা নিজেদের জিজ্ঞেস করি— এই ছেলেগুলো কোথা থেকে এলো? কারা তাদের তৈরি করল? কীভাবে তারা সংগঠনের ভেতরে প্রবেশ করল এবং কীভাবে দিনের পর দিন এমন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই আমাদের চোখ খুলে যাবে। আমরা বুঝতে পারবো রাজনৈতিক সংগঠনের ভেতরে কীভাবে জন্ম নেয় ও বেড়ে ওঠে চাঁদাবাজির এক ভয়াবহ অপসংস্কৃতি। এটি এমন এক সংস্কৃতি, যেখানে আদর্শের চেয়ে সম্পর্ক, নীতির চেয়ে পরিচিতি এবং ন্যায়ের চেয়ে শক্তি বড় হয়ে ওঠে।
যে তরুণটি মিছিলে সামনে থাকে, নেতা তার মাথায় হাত রাখে, সে আজ নয় তো কাল পদ পায়। আর সেই পদ থেকেই তার যাত্রা শুরু হয় নানা অনৈতিকতার দিকে। প্রথমে হালকা ‘সহযোগিতা’, পরে তা হয়ে যায় নিয়মিত ‘তুলে দেওয়া’ এবং শেষে সরাসরি চাঁদাবাজি। এই চক্র ভাঙার জন্য ভেতর থেকে প্রতিরোধ কখনও তৈরি হয়নি। বরং এসব তরুণ সংগঠনের সুবিধাবাদী নেতাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এদের মাধ্যমে তারা ছড়ি ঘোরায়, অনুপস্থিত থেকেও প্রভাব রাখে এবং দিনের শেষে নিজের প্রভাব বিস্তার নিশ্চিত করে।
এই প্রজন্মের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো, তারা রাজনীতিকে দেখে সুবিধা আদায়ের এক পথ হিসেবে। তারা আদর্শ নয়, বরং পরিচয়ের সন্ধানে থাকে। নিজেদের আখের গোছাতে চায়, নিজেকে নেতার ‘ঘনিষ্ঠ’ প্রমাণ করতে চায় এবং প্রভাব খাটাতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষার সুযোগ নিয়েছে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো। তারা নিজেদের স্বার্থে এসব তরুণকে ব্যবহার করেছে, প্রশ্রয় দিয়েছে, আর যখন তারা ধরা খেয়েছে, তখন দায় ঝেড়ে ফেলেছে এক টুকরো বহিষ্কারের বিজ্ঞপ্তিতে। এই ‘বহিষ্কার’ কি যথেষ্ট? এটা কি শুধুই সাংগঠনিক দায়মুক্তির জন্য একটি ফর্মালিটি? নাকি এটি প্রকৃত আত্মসমালোচনার অংশ? আমরা দেখেছি, বহুবার বহিষ্কৃত কর্মী কিছুদিন পর আবার দলে ফিরে আসে— হয়তো ভিন্ন নামে, ভিন্ন পদে। কারণ শিকড় থেকে যদি সংস্কার না হয়, তাহলে ফলাফলও পাল্টায় না।
উমামা ফাতেমার বক্তব্য এখানে একটি বড় ভূমিকা রাখে। একজন সাবেক সংগঠক হিসেবে তিনি কেবল তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেননি, বরং স্পষ্ট করে দিয়েছেন— সংগঠন জানত, অথচ কিছু করেনি। তিনি বলেন, ‘আমি জেনে তখন মোটেও অবাক হইনি, কারণ তত দিনে বৈষম্যবিরোধীতে এই ধরনের মানুষজনের আনাগোনাই সর্বোচ্চ টের পাওয়া যেত।‘ এই কথার ভেতর লুকিয়ে আছে একটি বড় বাস্তবতা— এই ধরনের চরিত্ররা সংগঠনে ঢোকে, মিশে যায়, জায়গা করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত সংগঠনের নামেই অপরাধ করে। উমামা যে ছেলেটির নাম করেছেন— রিয়াদ— সে শুধু তার সামনে মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি, বরং এর আগেও একাধিক অভিযোগের পাত্র ছিল। কিন্তু সংগঠনের পিনড্রপ সাইলেন্স সব কিছু ঢেকে রেখেছিল।
এই পিনড্রপ সাইলেন্সই সবচেয়ে বিপজ্জনক। এটি কেবল চুপ থাকা নয়, এটি সম্মতি দেওয়া। এটি এক ধরনের পরোক্ষ উৎসাহ। আমরা যাদের চুপ থাকতে দেখি, তারা অনেক সময় ভিতরে ভিতরে অপরাধীদের রক্ষা করে। এই সংস্কৃতি যদি না ভাঙে, তাহলে সামনে আরও ভয়াবহ ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আজ যারা ধরা পড়েছে, তারা কেউ একদিনে এই পর্যায়ে আসেনি। এদের তৈরি হতে সময় লেগেছে, পেছনে ছিল প্রশ্রয়, প্রশিক্ষণ এবং প্রণোদনা। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংগঠনিক— সবদিক থেকেই এই প্রশ্রয় এসেছে। আমাদের সমাজে যারা নেতৃত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে, তাদের চারপাশে একটি সুবিধাবাদী বলয় তৈরি হয়। এই বলয়ে যারা ঢোকে, তারা নিজেদের স্থায়ী করার জন্য কোনো নিয়ম মানে না, কোনো আদর্শে স্থির থাকে না। তারা শুধুই সুবিধা চায়। আর এই সুবিধাবাদই শেষ পর্যন্ত চাঁদাবাজিতে রূপ নেয়।
আজ এই ঘটনায় আমরা যারা খুব অবাক হচ্ছি, তারা হয়তো এতদিন দেখেও না দেখার ভান করেছি। অথবা আমরাও সেই 'নিষ্পাপ বিস্ময়'র অভিনয়ে লিপ্ত, যেটিকে উমামা বিদ্রুপ করে বলেছেন— ‘মানুষ কত নিষ্পাপ! সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো তারা আবিষ্কার করেছেন এই ছেলেগুলো আজ কীভাবে চাঁদাবাজি করল?!’ এই কথার ভেতরে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকে না চিহ্নিত করেও পুরো চিত্রটি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। যারা এতদিন দেখে এসেছেন, চুপ থেকেছেন, সহ্য করেছেন— তারাও কি দায়মুক্ত? না কি তাদের ভূমিকা আরও বেশি প্রশ্নবিদ্ধ? আমরা জানি, বহু সময় সংগঠনের ভেতরে কিছু বললেই বলা হয়— 'রাজনীতি বুঝো না', 'এইভাবে বলো না', 'দলকে বদনাম দিয়ো না'। অথচ এইসব চুপ করে থাকার ফলাফলই আজকের এই বিপর্যয়।
একটি ছাত্র সংগঠন যখন তার মূল লক্ষ্যের বাইরে চলে যায়, যখন তা রূপ নেয় সুবিধাবাদীদের দখলে, তখন তার পতন অনিবার্য। ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, শেখ হাসিনার উত্থান-পতন কী আমাদের কিছুই শিখাতে পারেনি? এমন উদাহরণ রয়েছে ইতিহাসে— যে-সব সংগঠন এক সময় জনআন্দোলনের প্রতীক ছিল, সেগুলোই পরে হয়ে উঠেছে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও অস্ত্রবাজির কেন্দ্র। আজ যারা নিজেদের 'বিকল্প' বা 'বিকল্প রাজনীতির প্রতীক' হিসেবে দাবি করে, তাদের মধ্যেও এই একই রোগ ঢুকেছে। ভিন্ন পোশাক, ভিন্ন স্লোগান, কিন্তু একই চেতনার বিকৃতি। কাজেই এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বা কেবল পাঁচজন তরুণের 'ভুল' বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এর ভেতরে রয়েছে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়—একেকটি বড় সংগঠনের কাঠামো আসলে কতোটা দুর্বল, নেতৃত্ব কতোটা অন্ধ এবং মূল্যবোধ কতোটা শূন্য।
সাংগঠনিক স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা পুনর্গঠন ছাড়া এই সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। শুধু বহিষ্কারের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দায় এড়ানো যাবে না। বরং প্রতিটি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, অভিযোগের শুনানি, অপরাধের স্বীকৃতি এবং সর্বোপরি সংগঠনের ভেতরে গণতান্ত্রিক পর্যালোচনার চর্চা আবশ্যক। যে-সব তরুণ আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসে, তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। আর যে-সব অপরাধী সংগঠনের ছত্রছায়ায় কাজ করে, তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে।
এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়— রাজনীতি শুধু ক্ষমতার খেলা নয়; এটি দায়িত্ব, জবাবদিহি ও ন্যায়েরও প্রশ্ন। যারা এই ন্যায়ের পথ হারিয়ে চাঁদাবাজিকে নিজের হাতিয়ার বানায়, তারা আদতে রাজনীতিকে কলঙ্কিত করে। আর যারা তাদের চুপচাপ সহ্য করে, তারা সেই কলঙ্কেরই অংশ। কাজেই আজ প্রয়োজন সত্য বলার সাহস। দরকার সংগঠনের ভিতরে ভিতরে আলো জ্বালানো। দরকার সেইসব মানুষদের যারা সত্য বলার কারণে সংগঠন থেকে ছিটকে পড়েছে, নিঃস্ব হয়েছে, অথচ নিজের বিশ্বাস ধরে রেখেছে। এইসব মানুষই আগামী দিনে নতুন আলোর পথ দেখাতে পারে। কিন্তু তার আগে আমাদের স্বীকার করতে হবে— হ্যাঁ, আমরা ব্যর্থ হয়েছি এবং এই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা না নিলে, সামনে আরও অন্ধকার অপেক্ষা করছে।
সমন্বয়ক পরিচয়ের এই উত্থান হঠাৎ নয়। এটি বহুদিন ধরে গড়ে ওঠা এক সাংগঠনিক প্রবণতার ফল। সংগঠনের কাঠামো দুর্বল হলে, নেতৃত্বের চোখে শুধুই আনুগত্য দেখলেই পদ দেওয়া হলে, তদ্বির ও প্রভাবকে প্রাধান্য দিলে, সেখানে এই ধরনের ব্যক্তি ঘাঁটি গাড়ে। তারা নিজের নামের পাশে 'সমন্বয়ক', 'আহ্বায়ক' বা অন্য পদ-পদবি লিখে নানা স্থানে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি কিংবা উত্তরার কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তারা এমনভাবে কথা বলে যেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেতাদের সঙ্গে ছবি আপলোড করে, মিটিংয়ের ছবি দিয়ে, আরেকটু পরিচিতি আদায়ের চেষ্টা করে। এভাবেই একসময় তারা একটি 'অদৃশ্য ক্ষমতা'র অংশ হয়ে ওঠে। সংগঠনের বাইরে যারা থাকে, তারা ভাবে— এই ছেলে নিশ্চয় বড় নেতা। অথচ বাস্তবে হয়তো সে কেবল নেতা বা নেত্রীর একাধিক মিটিংয়ে গিয়েছে মাত্র। কিন্তু সেটিকে ব্যবহার করে সে হয়ে ওঠে প্রতিনিধি, দায়িত্বপ্রাপ্ত, এবং অবশেষে সমন্বয়ক। এই প্রতীকী পরিচয়টি এক সময় তাকে নানাবিধ লেনদেন ও চাঁদাবাজির সুযোগ এনে দেয়।
এখানে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিও প্রশ্নবিদ্ধ। অনেক প্রতিষ্ঠান এই পরিচয়ের সামনে নমনীয় হয়ে পড়ে। যেহেতু রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে, কেউ বিষয়টি বাড়াতে চায় না। পুলিশ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এমনকি বাড়ির নিরাপত্তারক্ষীরা পর্যন্ত বুঝতে পারে না কে আসল, কে নকল। এই দ্বিধার সুযোগ নিয়েই এই 'সমন্বয়ক'রা মাঠে নামে। তারা চাঁদা দাবি করে, হুমকি দেয়, আবার প্রয়োজনে পরিচিত কারও নাম জুড়ে দেয়— 'ফোন দিলে ভাইই ধরবে'— এই ভয়ের সংস্কৃতি রাজনৈতিক পরিচয়ের শেল্টারে আজ অবাধ।
কিন্তু এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তেমনভাবে কেউ রুখে দাঁড়ায় না। কারণ যারা দাঁড়াতে পারে, তারা হয় সংগঠনের বাইরে চলে যায়, নয়তো ভিতরেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। নতুন যারা আসে, তারা দেখে— আদর্শের চেয়ে সুবিধা বড়। সাহসের চেয়ে ছলনার কদর বেশি। কাজেই প্রতিরোধের পরিবেশ থাকে না। বরং এই সমস্ত 'সমন্বয়ক'রাই হয়ে ওঠে মিটিংয়ের মুখ, আলোচনার প্রতিনিধি। ফলে সংগঠনের অভ্যন্তর থেকে এই সংস্কৃতি দূর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এবং যখন কোনোকিছু ধরা পড়ে, তখন বহিষ্কার বা নিন্দা জানিয়ে দায় শেষ করা হয়। অথচ এই অপরাধীদের তৈরি করতে পেছনে পুরো সংগঠনের পরিবেশ, প্রশ্রয় ও রাজনীতির ধারা কাজ করে।
রাজনীতির মূল চেতনা যদি হয় জনগণের অধিকার ও ন্যায়ের প্রশ্নে সরব হওয়া, তবে এই তথাকথিত 'সমন্বয়ক' সংস্কৃতি রাজনীতির পেছনেই ছুরি চালাচ্ছে। তারা রাজনীতিকে অসৎ লেনদেনের মঞ্চে পরিণত করছে। আর আমরা যারা এই অবক্ষয়ের সাক্ষী, তারা নিরবতা দিয়ে অপরাধকে টিকিয়ে রাখছি। যদি এই নিরবতা না ভাঙে, যদি আমরা নিজেদের দোষ স্বীকার না করি, তাহলে এই চক্র শুধু পাল্টাবে না— বরং আরও গভীরে প্রোথিত হবে।
আজ প্রয়োজন, রাজনীতিকে নতুন করে পড়া, বোঝা এবং রক্ষা করা। যারা সত্য বলে, যারা অন্যায় দেখে প্রশ্ন তোলে, যারা পদ চায় না, ন্যায়ের কথা বলে— তাদের জন্য জায়গা তৈরি করতে হবে। ছাত্র রাজনীতি মানে কেবল পদ-পদবি নয়, বরং একটি আদর্শিক প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হলে, ছাত্র রাজনীতি আবারও হয়ে উঠবে ছদ্মবেশী লুটেরাদের আখড়া। এই সম্ভাব্য পরিণতির আগেই আমাদের সতর্ক হতে হবে, সাহসী হতে হবে এবং নতুন আলো হাতে তুলে নিতে হবে।
লেখক : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, কলামিস্ট।
এইচআর/এএসএম

 1 month ago
18
1 month ago
18





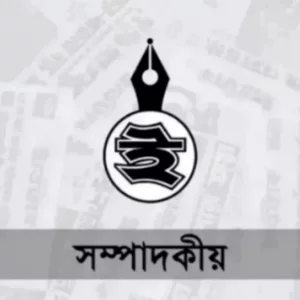



 English (US) ·
English (US) ·