দেশে বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প কারখানা আজ টিকে থাকার লড়াইয়ে নেমেছে। এই লড়াইয়ে কেউ হারছেন, কেউ বা হারতে হারতে টিকে আছেন। এই ধারা যদি চলতে থাকে, তবে জাতীয় অর্থনীতি ভয়াবহ সংকটে পড়বে। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। ক্ষুদ্র শিল্প বাঁচানো মানে কর্মসংস্থানে সুরক্ষা নিশ্চিত করা, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা এবং শিল্পায়নের স্বপ্নপূরণের পথ প্রশস্ত করা। এক্ষেত্রে সরকার, ব্যাংক ও নীতিনির্ধারকদের সমন্বিত উদ্যোগই পারে পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিতে। আমরা মনে করি, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।
অপ্রিয় হলেও সত্য যে, দেশের উন্নয়নশীল অর্থনীতি আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। বিনিয়োগের স্রোত না ফিরলে শিল্প ও কর্মসংস্থান দুই-ই হুমকির মুখে পড়বে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশের অর্থনীতি গত কয়েক দশকে এক উজ্জ্বল পথচলা দেখিয়েছে। তৈরি পোশাক, কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ আমাদের প্রবৃদ্ধিকে করেছে গতিশীল। কিন্তু সাম্প্রতিক বাস্তবতা এক ভিন্ন চিত্র সামনে এনেছে- নতুন বিনিয়োগ কার্যত থেমে গেছে, ছোট-বড় বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর এর অভিঘাত পড়ছে সরাসরি শ্রমজীবী মানুষের ওপর।
অর্থনীতির ভিত শক্তিশালী করার অন্যতম ভিত্তি হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে নগরাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট শিল্প-উদ্যোগ। এ শিল্পগুলোতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ তৈরি হয়, অন্যদিকে জাতীয় উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ নানান প্রতিকূল অবস্থার কারণে এ ধরনের শিল্প একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে শুধু উদ্যোক্তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও হুমকির মুখে পড়ছে।
ক্ষুদ্র শিল্পই আমাদের শিল্পায়নের মেরুদণ্ড। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে, স্থানীয় চাহিদা মেটাতে এবং রপ্তানি খাতের প্রাথমিক ধাপ তৈরি করতে ছোট কারখানার ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু যে পরিবেশে এগুলো টিকে থাকার কথা, সেখানে উল্টো প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্যার মুখে পড়ছেন উদ্যোক্তারা। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহে অস্থিরতা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। অনেক কারখানায় বিদ্যুৎ থাকলেও গ্যাস নেই, আবার কোথাও গ্যাস সংযোগ থাকলেও চাপ কম। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে, আর উৎপাদন কমে আসছে।
আসলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ছোট ব্যবসায়ী ও বড় ব্যবসায়ী উভয়েরই অবদান রয়েছে। তবে ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হারে যে বৈষম্য বিদ্যমান, তা দীর্ঘদিন ধরেই আলোচিত একটি সমস্যা। বড় ব্যবসায়ীরা সহজেই স্বল্পসুদে বিপুল অঙ্কের ঋণ সুবিধা পান, অন্যদিকে ছোট ব্যবসায়ীরা সীমিত অঙ্কের ঋণ নিতে গেলেও উচ্চসুদ এবং নানান শর্তের মুখোমুখি হন। ফলে অর্থনীতির ভেতরে অসম ভারসাম্য তৈরি হয়। এক্ষেত্রে বড় ব্যবসায়ীরা তাদের আর্থিক সক্ষমতা, রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং জামানতের শক্তির কারণে সহজেই ব্যাংকের আস্থা অর্জন করতে পারেন। তাদের জন্য ঋণের সুদের হার তুলনামূলকভাবে কম রাখা হয়, অনেক সময় বিশেষ ছাড়ও দেওয়া হয়। এমনকি খেলাপি ঋণ হলেও পুনঃতফসিল বা ঋণমুক্তির সুবিধা পান। ফলে বড় ব্যবসায়ী মহল ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থায় একটি শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে।
অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা-যাদের বেশিরভাগ এসএমই বা খুচরা ব্যবসায়ী- ঋণ পেতে গিয়ে নানান সমস্যার সম্মুখীন হন। ব্যাংকগুলো তাদের কাছ থেকে বেশি সুদ নেয়, কঠিন জামানত চায় এবং কাগজপত্রে জটিলতা তৈরি করে। বাস্তবে দেখা যায়, বড় ব্যবসায়ীরা ৭-৯ শতাংশ সুদে ঋণ পেলেও ছোট ব্যবসায়ীদের অনেক সময় ১২-১৪ শতাংশ সুদ দিতে হয়। এতে তাদের ব্যবসার খরচ বেড়ে যায় এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।
এই বৈষম্যের প্রভাব অর্থনীতিতে স্পষ্ট। ছোট ব্যবসায়ীরা স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান তৈরি করে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে। কিন্তু উচ্চসুদের কারণে তারা ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারে না। অনেক সময় ঋণের চাপ সামলাতে না পেরে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়। দেখা যায়, বড় ব্যবসায়ীরা সুবিধাজনক ঋণ নিয়ে আরও বড় হয়, ফলে বাজারে এক ধরনের একচেটিয়া ক্ষমতা তৈরি হয়।
বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে ঋণ খাতের বৈষম্য দূর ও বিনিয়োগের গতি ফেরানো ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এখন যদি যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে কর্মসংস্থান সংকট, শিল্পখাতের দুর্বলতা এবং অর্থনীতির স্থবিরতা ক্রমেই তীব্র হবে। তাই সরকার ও নীতিনির্ধারকদের দ্রুত এবং কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে বিনিয়োগকারীরা আবার আস্থা ফিরে পান এবং নতুন বিনিয়োগপ্রবাহ শুরু হয়।
সহজ করে বললে, বড় বড় শিল্প মালিকরা সহজেই ব্যাংক ঋণ পান, এমনকি তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা রাখা হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ব্যাংকের কঠিন শর্ত পূরণ করতে পারেন না। অনেকে আবার উচ্চসুদের চক্রে পড়ে মূলধন হারিয়ে ফেলেন। সরকার যদিও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, কিন্তু বাস্তবে সেই সহায়তা খুব সীমিত সংখ্যক উদ্যোক্তার কাছেই পৌঁছেছে। ফলে অধিকাংশ ছোট শিল্প কারখানা আর্থিক সংকটে পড়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
দৃশ্যমান এসব বৈষম্যের কারণে আর্থিক খাতে আস্থার সংকট দেখা দেয়। আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মনে এই ধারণা জন্ম নিয়েছে যে, ব্যাংক ব্যবস্থা কেবল ধনীদের জন্য কাজ করে, গরিব বা মধ্যবিত্ত উদ্যোক্তাদের জন্য নয়। এর ফলে অনেকেই বিকল্প পথ যেমন এনজিও ঋণ বা অনানুষ্ঠানিক ধারদেনার দিকে ঝুঁকেন, যেখানে সুদের হার আরও বেশি। এ সমস্যার সমাধানে কিছু উদ্যোগ জরুরি।
আরেকটা বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিকক্রমে বলতে হয়, শিল্প কারখানা চালাতে কাঁচামালের প্রাপ্যতা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বৈশ্বিক বাজারে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় কাঁচামাল আমদানি ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। একইসাথে স্থানীয় বাজারেও নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণের দাম লাগামহীন। ছোট উদ্যোক্তারা বড় শিল্পের মতো কাঁচামাল মজুত করে রাখতে পারেন না। ফলে তাদের পণ্যের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে, বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে।
অর্থনীতির প্রাণশক্তি হলো বিনিয়োগ। নতুন শিল্প, নতুন উদ্যোগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি নির্ভর করে বিনিয়োগ প্রবাহের ওপর। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগ তেমন আসছে না- এটি নিঃসন্দেহে দেশের অর্থনীতির জন্য অশনিসঙ্কেত। দীর্ঘমেয়াদে এই স্থবিরতা দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে বড় ধরনের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। ভুলে গেলে চলবে না, দেশের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের প্রধান চালিকাশক্তিও বিনিয়োগ। বিনিয়োগ না হলে নতুন শিল্প গড়ে উঠবে না, কর্মসংস্থান তৈরি হবে না এবং অর্থনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরবে না। বিনিয়োগ স্থবিরতার পেছনে একাধিক কারণ কাজ করছে। ডলারের অস্থিরতা, আমদানি ব্যয়ের চাপ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অনিশ্চয়তা, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার এবং নীতি-নির্ধারণে অস্থিরতা উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও আস্থাহীন হয়ে পড়েছেন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ঝুঁকি দেখে। এর ফলে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না, পুরনো শিল্পও টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত।
এসব সংকটের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো কর্মসংস্থানের সংকোচন। ছোট শিল্পগুলোতে কাজ করা শ্রমিকদের সংখ্যা বিশাল। বিশেষ করে আধা-শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মানুষরা এসব কারখানার ওপর নির্ভর করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। যখন একটি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, তখন ওই শ্রমিকদের অনেকেই নতুন কাজ পান না। পরিবার চালাতে গিয়ে তারা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন, কেউ কেউ আবার বাধ্য হয়ে গ্রামে ফিরে যান। এর ফলে শহরের ওপর চাপ কমলেও গ্রামে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য আরও বেড়ে যায়। এছাড়া সামাজিক অস্থিরতাও তৈরি হয়। চাকরি হারানো তরুণেরা হতাশায় ভোগেন, কেউ কেউ অপরাধ প্রবণতার দিকেও ঝুঁকেন। অর্থনৈতিক মন্দার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা সংকটও প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ছোট শিল্প কারখানা বন্ধ হওয়া কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, বরং এটি একটি গভীর সামাজিক সংকটও বটে।
অন্যদিকে, সরকারের ঘোষিত শিল্পায়নের লক্ষ্যও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ২০২৪ সালের পর বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করছে। এ অবস্থায় যদি ক্ষুদ্র শিল্পগুলো টিকে থাকতে না পারে, তবে বৃহৎ শিল্পায়নের স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হবে না। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ভেঙে পড়া মানে হচ্ছে ভবিষ্যতের বৃহৎ শিল্পপতিদের জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাওয়া। এই ক্ষেত্রে সমাধান কী হতে পারে? প্রথমত, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য আলাদা আর্থিক সহায়তা তহবিল তৈরি করতে হবে, যা সহজ শর্তে দেওয়া হবে। ঋণের সুদের হার কমিয়ে উদ্যোক্তাদের স্বস্তি দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহকে স্থিতিশীল করতে হবে। ছোট শিল্পাঞ্চলগুলোতে আলাদা ব্যবস্থা করে হলেও তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি নিশ্চিত করা জরুরি।
তৃতীয়ত, কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক ও ভ্যাট ছাড় দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে টিকিয়ে রাখতে হবে। চতুর্থত, বিপণন সুবিধা বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ক্ষুদ্র শিল্প মেলা ও ই-কমার্স সুবিধা বাড়ানো উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নীতিনির্ধারণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়া। বড় শিল্পপতিদের স্বার্থে নীতি প্রণয়ন করলে ক্ষুদ্র শিল্প বাঁচবে না। অথচ ক্ষুদ্র শিল্পই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
মনে রাখতে হবে, শিল্প স্থবির হলে সবচেয়ে বড় আঘাত আসে কর্মসংস্থানের ওপর। প্রতিদিন শ্রমজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ছে। শহরের বস্তি থেকে গ্রামীণ পরিবার-সবখানেই এর প্রভাব পড়ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য-সব ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের চক্র আরও বিস্তৃত হচ্ছে। একটি কলকারখানা বন্ধ মানে শুধু একটি ব্যবসার ক্ষতি নয়, বরং শত শত পরিবারের জীবনে অন্ধকার নেমে আসা।
সমাধান খুঁজতে হলে প্রথমেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। নীতিমালায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে, যাতে বিনিয়োগকারীরা আস্থা ফিরে পান। দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে ব্যবসায়িক পরিবেশ সহজতর করা জরুরি। ‘ওয়ান-স্টপ সার্ভিস’ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করলে অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ হবে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা ছাড়া বিকল্প নেই। এছাড়া, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে কর প্রণোদনা, জমি বরাদ্দে স্বচ্ছতা এবং আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। দেশীয় উদ্যোক্তাদেরও উৎসাহিত করতে সাশ্রয়ী ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান জরুরি।
আমরা বলতে চাই, এসএমই খাতে সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। জামানতবিহীন ঋণ, নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় দ্রুত অনুমোদন ছোট উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে পারে। সুদের হার নির্ধারণে ন্যায়সঙ্গত কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে বড় ও ছোট ব্যবসায়ীর মধ্যে এত বৈষম্য না থাকে। রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় ছোট ব্যবসায়ীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার, কারণ তারা কর্মসংস্থান ও স্থানীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। আসলে ব্যাংক ঋণের সুদের হারে বৈষম্য শুধু ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষতিই করছে না, বরং সামগ্রিক অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ ঋণনীতি তৈরি হলে ছোট ব্যবসায়ীরা বিকশিত হবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং অর্থনীতি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে। তাই সময় এসেছে-সুদের হারের বৈষম্য দূর করে ছোট ব্যবসায়ীদের জন্যও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার।
বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে ঋণ খাতের বৈষম্য দূর ও বিনিয়োগের গতি ফেরানো ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এখন যদি যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে কর্মসংস্থান সংকট, শিল্পখাতের দুর্বলতা এবং অর্থনীতির স্থবিরতা ক্রমেই তীব্র হবে। তাই সরকার ও নীতিনির্ধারকদের দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে বিনিয়োগকারীরা আবার আস্থা ফিরে পান এবং নতুন বিনিয়োগ প্রবাহ শুরু হয়।
লেখক : কলাম লেখক ও ক্ষুদ্র শিল্পদ্যোক্তা।
এইচআর/এমএস

 2 hours ago
3
2 hours ago
3




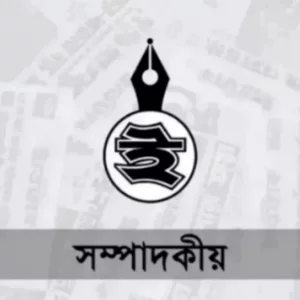




 English (US) ·
English (US) ·