৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্পে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা। এখন পর্যন্ত প্রায় আটশর বেশি নিহত ও আহত হয়েছে প্রায় তিন হাজার মানুষ। আফগানিস্তানের কম্পনে কেঁপে ওঠে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদসহ একাধিক এলাকা।
গত দুই বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও বাংলাদেশে অনেকগুলো ছোট-মাঝারি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ছোট ছোট এসব ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্বব্যাপী ভূমিকম্পের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের মধ্যে রয়েছে ঢাকা। অথচ এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি কমাতে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি কোনো সরকার।
ভূমিকম্পপ্রবণ বাংলাদেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। গত বছরের শেষ দিকে ও চলতি বছরের প্রথমে বাংলাদেশের আশপাশে মৃদু ও তীব্র মাত্রার অর্ধশতাধিক ভূমিকম্প হয়েছে। গত ১৫ বছরে ছোট-বড় ভূমিকম্প হয়েছে দেড় শতাধিক, যা আশঙ্কাজনক। ৬ কিংবা ৭ মাত্রার ভূমিকম্প বাংলাদেশে হলে প্রাণহানি ঘটতে পারে কয়েক লাখ।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাপক ভূমিকম্পের ঝুঁকির মুখোমুখি। বাংলাদেশের ঘনবসতি, পুরোনো অবকাঠামো ও বিল্ডিং কোডের দুর্বল প্রয়োগ এই বিপদগুলো আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অবিলম্বে পদক্ষেপ না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে মিয়ানমার, তুরস্ক, থাইল্যান্ড কিংবা আফগানিস্তানের মতো একটি ভয়াবহ দৃশ্য অপেক্ষা করছে।

ঝুঁকিতে বাংলাদেশ
বেশ কয়েকটি সক্রিয় ফল্ট লাইনসহ টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিতে ফেলেছে। ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চলে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছে ১৮৬৯ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে। পাঁচটি বড় ঘটনা রিখটার স্কেলে ৭ এর ওপরে রেকর্ড করা হয়।
বড় ধরনের ভূমিকম্প ঘটলে দেশে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। প্রস্তুতির অভাবে প্রাণহানির ঝুঁকি অনেক বেশি, বিশেষ করে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোতে। অবকাঠামোগত দিক থেকেও ঝুঁকি প্রবল, কারণ দেশের অনেক ভবন ভূমিকম্প সহনশীল নয় এবং নিম্নমানের নির্মাণশৈলীর কারণে ধসের আশঙ্কা বেশি।- অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান
এরপর থেকে উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প স্তিমিত হয়ে আছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ভূমিকম্পে বিপর্যয়ের আগে এ নীরবতা থাকতে পারে।
- আরও পড়ুন
- বারবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপেছে আফগানিস্তান
- হুহু করে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, প্রাণহানি ৮০০ ছাড়ালো
- ভূমিকম্প নিয়ে ‘ভালো সংবাদ’ নেই বাংলাদেশের
- আবারও ভূমিকম্পের শঙ্কা, ৭ মাত্রার হলে ঢাকায় ‘ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি’
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভূমিকম্পের আঘাত উদ্বেগজনকভাবে বাড়তে দেখা গেছে। ২০২৪ সাল থেকে রেকর্ড করা ৬০টি ভূমিকম্পের মধ্যে তিনটি ৪ মাত্রার ওপরে এবং ৩১টি ৩ থেকে ৪ মাত্রার মধ্যে ছিল। এই ঊর্ধ্বগতি, শহর এলাকায় বিস্তৃত এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত জাতিকে ঝুঁকিপূর্ণভাবে তুলে ধরছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
ভূমিকম্পের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকা
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্যমতে, বাংলাদেশ ভূকম্পনের সক্রিয় এলাকায় অবস্থিত। দুর্যোগ সূচক অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী ভূমিকম্পের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের মধ্যে রয়েছে ঢাকা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছোটোখাটো কম্পন দেশের আরও শক্তিশালী ভূমিকম্পের আশঙ্কা নির্দেশ করে। ১৮৮৫ সালের ভূমিকম্প এবং ১৯১৮ সালের শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্পের প্রতিটিরই কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের মধ্যে এবং যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। এ অঞ্চলে বড় ভূমিকম্প প্রায় ৭৫ বছর ধরে ঘটেনি, তাই শিগগির একটি বড় ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি।
টেকটোনিক প্লেট যেভাবে ভূমিকম্পের অনুঘটক
তিন ধরনের পারস্পরিক প্লেট সীমানার কথা জানা যায়। সমকেন্দ্রাভিমুখী সীমা, অপসারী সীমা ও পরিবর্তক চ্যুতি সীমা। সমকেন্দ্রাভিমুখী সীমা যখন একে অপরের দিকে অগ্রসরমান দুটি প্লেট কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে অবশেষে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন একটি প্লেট অপরটির নিচে চাপা পড়ে। এ ধরনের প্লেট সংঘর্ষের ফলে পর্বতমালার সৃষ্টি হয় এবং প্লেট প্রান্তিকের আশপাশে আগ্নেয়গিরির কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। অপসারী সীমার ক্ষেত্রে দুটি প্লেট একে অপরের কাছ থেকে সরে যেতে থাকে। এ ধরনের প্লেট সীমানার ফলে নতুন সমুদ্র তলদেশের এবং সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।
আশপাশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প বাংলাদেশের জন্য অ্যালার্মিং। ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে কিছু কিছু ভূমিকম্প বেশ কয়েক বছর ধরে হয়েছে। আমাদের দাবি ছিল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী যেন ভবনগুলো বানানো হয়। বিল্ডিং কোড মানার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা ভয়ংকর।- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আদিল মুহাম্মদ খান
আর যখন দুটি প্লেট একে অপরকে অতিক্রম করে যায়, তখন তাকে পরিবর্তক চ্যুতি সীমা বলে। তিন ধরনের প্লেট বিচলনেই ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।
বঙ্গীয় অববাহিকার অধিকাংশই পড়েছে বাংলাদেশে। ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এর উৎপত্তি। ক্রিটেসিয়াস যুগের পূর্বে (সাড়ে ১২ কোটি বছর আগে) বাংলাদেশের অংশবিশেষসহ (বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চল) ভারতীয় প্লেট, অ্যান্টার্কটিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামে একটি বৃহৎ মহাদেশ গড়ে তোলে। বাংলাদেশের অবশিষ্টাংশের তখন অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর গন্ডোয়ানাল্যান্ডে ফাটলের ফলে ভারতীয় প্লেটের উত্তরমুখী সঞ্চরণ ও সবশেষ এশীয় প্লেটের সঙ্গে এর সংঘর্ষের ফলে হিমালয় পর্বতমালা ও বাংলাদেশের ব-দ্বীপীয় সমভূমির সৃষ্টি হয়।
ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেটের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক সংঘর্ষ ইয়োসিন যুগে (পাঁচ কোটি থেকে সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগে) হিমালয়ের প্রারম্ভিক উত্থানের সময় প্রথম সংঘটিত হয়। নবীন ইয়োসিন যুগে (সাড়ে তিন কোটি থেকে চার কোটি) ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেটের মধ্যবর্তী টেথিস সাগরের সবশেষ চিহ্ন সম্ভবত বিলীন হয়ে যায়। এই সময়েই ভারতীয় প্লেটের অভিসরণ দিক দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষসহ উত্তর থেকে উত্তর-পূর্বদিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়।
ওলিগোসিন যুগ থেকে (সাড়ে তিন কোটি বছর আগে) প্লেট সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে এবং বিশাল নদীমালার জলরাশিতে দক্ষিণে আদি বঙ্গীয় অববাহিকা ভরে উঠলে উত্থিত হিমালয়ের অবক্ষেপ নেমে আসতে শুরু করে। মায়োসিন পরবর্তী সময় থেকে (আড়াই কোটি বছর তৎপরবর্তী) অববাহিকায় দ্রুত অবনমনের সঙ্গে হিমালয় পবর্তমালার দ্রুত উত্থানের ফলে বিপুল অবক্ষেপের সুতপের পাশাপাশি বৃহদাকৃতির বদ্বীপ গড়ে ওঠে।
বড় ভূমিকম্পে দেশে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় ঘটতে পারে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন ও ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল, কারণ প্লেট বাউন্ডারি। প্লেট বাউন্ডারি বরাবর এরকম প্রতিদিনই প্রচুর হয়, যেগুলো ছোট ছোট ভূমিকম্প, তবে মাঝে-মধ্যে বড় ভূমিকম্পও হয়। বাংলাদেশে ভূমিকম্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হতে পারে ভয়াবহ। অনেক মানুষ বাস্তুহারা হবে, তাদের জীবিকা ও সামাজিক স্থিতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এখনই প্রস্তুতি ও সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে না।’
সবার আগে ভূমিকম্পে সচেতনতা জরুরি। ঢাকা শহরের বেশিরভাগ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য ভবনগুলো ভূমিকম্প নিরোধক কিংবা মজবুত করা প্রয়োজন। তবে সবচেয়ে বেশি জরুরি জনগণের সচেতন হওয়া। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে উদ্ধারকারী হিসেবে তৈরি করা।- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন্স অ্যান্ড মেনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে প্রধানত এর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে। ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষস্থলে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি নিয়মিত ভূমিকম্পের হুমকির মুখে রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চলগুলো অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত।’
‘বড় ধরনের ভূমিকম্প ঘটলে দেশে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। প্রস্তুতির অভাবে প্রাণহানির ঝুঁকি অনেক বেশি, বিশেষ করে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোতে। অবকাঠামোগত দিক থেকেও ঝুঁকি প্রবল, কারণ দেশের অনেক ভবন ভূমিকম্প সহনশীল নয় এবং নিম্নমানের নির্মাণশৈলীর কারণে ধসের আশঙ্কা বেশি। ফলে পরিবহন ও ইউটিলিটি সেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।’

জিল্লুর রহমান আরও বলেন, ‘অর্থনৈতিক দিক থেকে ভূমিকম্পের প্রভাবও ভয়াবহ। একটি বড় ধরনের ভূমিকম্পের পর পুনরুদ্ধার ব্যয় হাজার হাজার কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবা খাতে স্থবিরতা সৃষ্টি হবে, যার প্রভাব জাতীয় অর্থনীতিতেও পড়বে। জরুরি সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রেও রয়েছে বড় চ্যালেঞ্জ- বিশেষ করে শহরের সরু রাস্তা ও সীমিত চিকিৎসা সুবিধা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যাহত করবে।’
বিল্ডিং কোড মানতে কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবান ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগের অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইপিডি) নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আদিল মুহাম্মদ খান জাগো নিউজকে বলেন, ‘আশপাশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প বাংলাদেশের জন্য অ্যালার্মিং। ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে কিছু কিছু ভূমিকম্প বেশ কয়েক বছর ধরে হয়েছে। আমাদের দাবি ছিল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী যেন ভবনগুলো বানোনো হয়। যে ভবনগুলো বানানো হচ্ছে সেগুলো সঠিক জায়গায় করা। বিল্ডিং কোড মানার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা ভয়ংকর।’
তিনি বলেন, ‘সরেজমিনে তদন্ত করার ক্ষেত্রে দক্ষতা ও আগ্রহ কোনোটাই এখন পর্যন্ত দেখাতে পারেনি তারা। বিপরীতে নিচু ভূমি ও জলাভূমি ভরাট করে বহুতল ভবন বানানোর যে প্রবণতা সেটা ১০ বছরে মহামারি আকারে বেড়েছে।’
আদিল বলেন, ‘জলাভূমি ভরাট করে ভবন হচ্ছে, যা অধিকাংশ আইন অমান্য করে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। কয়েক বছর পরে যখন মাস্টার প্ল্যান সংশোধন হয় তখন বলে যেহেতু হয়ে গেছে তখন অনুমোদন না দিয়ে কী করার...। এই প্রবণতা যদি চলে বড় ভূমিকম্প লাগবে না, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের এলাকায় ৫ কিংবা সাড়ে ৫ মাত্রার হলেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হবে।’
ঢাকা শহরের বেশিরভাগ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন্স অ্যান্ড মেনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী জাগো নিউজকে বলেন, ‘সবার আগে ভূমিকম্পে সচেতনতা জরুরি। ঢাকা শহরের বেশিরভাগ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য ভবনগুলো ভূমিকম্প নিরোধক কিংবা মজবুত করা প্রয়োজন। তবে সবচেয়ে বেশি জরুরি জনগণের সচেতন হওয়া। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে উদ্ধারকারী হিসেবে তৈরি করা।’
টিটি/এএসএ/এমএফএ/এএসএম

 3 hours ago
3
3 hours ago
3







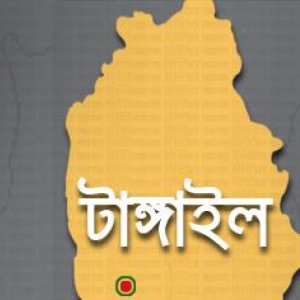

 English (US) ·
English (US) ·