বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় সরকার এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তা ব্যক্তিরা প্রায়ই দেশের সার্বিক উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই আশাবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগায়, মনোবল বাড়ায়, এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ধারায় এক ধরনের ইতিবাচক সুর সৃষ্টি করে। তবে এই আশাবাদের বিপরীতে কিছু উদ্বেগের সুরও শোনা যায়।
যেমন সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এক গভীর সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, সবাই সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে, এবং আপনারা অবশ্যই এটা অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং আমি আশঙ্কা করছি, যদি এটার সঙ্গে ধর্মীয় যে দৃষ্টিকোণ, এটা যদি যুক্ত হয়, তাহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।’ তথ্য উপদেষ্টার এই বক্তব্য বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। এই বক্তব্য কেবল রাজনৈতিক উত্তেজনার ইঙ্গিত নয়; বরং এটি সমাজে ক্রমবর্ধমান বিভাজন ও সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক সঙ্কটেরও প্রতিচ্ছবি।
বাংলাদেশের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তির টানাপোড়েনের মধ্যে বন্দি। তাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস, প্রতিযোগিতা, ও প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক চর্চাকে দুর্বল করেছে, অন্যদিকে সমাজকেও বিভাজিত করেছে নানা উপগোষ্ঠীতে। রাজনীতির এই বিরোধ অনেক সময় এমন জায়গায় পৌঁছায় যেখানে দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থকে ছাপিয়ে যায়। এ অবস্থায় যদি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা অনুভূতি রাজনীতির সঙ্গে মিশে যায়, তবে সংকট আরও গভীর ও বিপজ্জনক রূপ নিতে পারে। ধর্ম বাংলাদেশে মানুষের আবেগের কেন্দ্র, আস্থার প্রতীক। কিন্তু যখন এই আবেগকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন তা সহিংসতা, বিভাজন ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ধর্মের দোহাই দিয়ে সংঘাত উস্কে দেওয়া কখনো সমাজের মঙ্গল বয়ে আনে না; বরং তা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে নষ্ট করে দেয়।
একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জাতির গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। ভোটাররা যদি নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, যদি তারা মনে করেন তাঁদের মতামত সম্মান পাচ্ছে, তবে গণতন্ত্র জীবন্ত থাকে। কিন্তু যদি রাজনৈতিক উত্তেজনা, প্রশাসনিক অনীহা এবং সহিংসতার আশঙ্কা ভোটারদের মনে দানা বাঁধে, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। এই হতাশা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।
এই আশঙ্কার বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় উগ্রতার বিচ্ছিন্ন ঘটনা, মিথ্যা প্রচারণা বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্মীয় উস্কানি সমাজে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের জনপ্রিয়তা বা সমর্থন বৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় আবেগের সুযোগ নিলে সেই আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। এর পরিণতি হবে সমাজে অবিশ্বাস, ভয় ও বৈরিতার বিস্তার। রাজনৈতিক বিভাজন যখন ধর্মীয় রূপ পায়, তখন তা আর কেবল ক্ষমতার লড়াই থাকে না; তা হয়ে ওঠে অস্তিত্বের প্রশ্ন, যা সমাজের মূল কাঠামোকে নাড়া দেয়।
এমন বাস্তবতায় সরকারের কর্তাব্যক্তিদের আশাবাদ যদিও প্রশংসনীয়, তবুও সেই আশাবাদের সঙ্গে বাস্তবতার ভারসাম্য রক্ষা করাটা এখন সময়ের দাবি। উন্নয়নের গতি, অর্থনৈতিক সূচকের বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত সাফল্য—এসব নিঃসন্দেহে ইতিবাচক অর্জন, কিন্তু এগুলোর পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি, রাজনৈতিক স্থিতি এবং মানুষের নিরাপত্তাবোধও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ কেবল উন্নয়নের পরিসংখ্যান দেখে স্বস্তি পায় না; তারা দেখতে চায় একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ। তাই তথ্য উপদেষ্টাদের মতো ব্যক্তিরা যখন সতর্ক করেন, তখন সেটিকে সমালোচনা হিসেবে না দেখে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত।
সংকট থেকে উত্তরণের জন্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও আন্তরিক উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে খোলামেলা সংলাপের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। মুখোমুখি সংঘাত নয়, বরং আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে মতবিরোধ দূর করা সম্ভব। এক্ষেত্রে যত বেশি রাজনৈতিক দলকে পক্ষে টানা যায়, ততই মঙ্গল। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় ধর্মীয় ও জাতিগত সহনশীলতা জোরদার করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধ ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগানোর উদ্যোগ নেওয়া দরকার। তৃতীয়ত, তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি—যাতে মিথ্যা তথ্য বা গুজবের মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কারণ বৈষম্য ও বঞ্চনা অনেক সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দেয়।
তবে সংকটের মূল থেকে উত্তরণের জন্য শুধু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার যথেষ্ট নয়; দরকার মনোভঙ্গির পরিবর্তন। সরকারের নীতিনির্ধারক, প্রশাসন, এবং রাজনৈতিক নেতাদের মানসিকতা হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহনশীল এবং বাস্তববাদী। জনগণের উদ্বেগকে উপেক্ষা না করে, বরং তা শুনে সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টা নিতে হবে। উদ্বেগ প্রকাশ করা দুর্বলতার লক্ষণ নয়; বরং এটি দায়িত্ববোধের পরিচয়। সমস্যার আগাম ইঙ্গিত পাওয়া মানেই তা প্রতিরোধের সুযোগ তৈরি হওয়া।
এখন যখন দেশ নির্বাচনমুখী, তখন এই সংকট ও উদ্বেগের প্রেক্ষাপট আরও তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পরিবেশ গঠন একটি জাতির গণতন্ত্রের মেরুদণ্ডের মতো। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, সেই পরিবেশ সৃষ্টির কার্যকর উদ্যোগ অনুপস্থিত। কিছু রাজনৈতিক দলকে দলকে আলোচনার টেবিল থেকে বাইরে রেখে রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠা কঠিন। যে দলগুলো আলোচনার টেবিলে বসছে, তাদের মধ্যেও মতানৈক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। পারস্পরিক অবিশ্বাস, এবং সংঘর্ষের আশঙ্কা নির্বাচনকে অনিশ্চয়তায় ফেলছে। সরকার ও নির্বাচন কমিশন যদি এখনই দৃঢ় ও আন্তরিক পদক্ষেপ না নেয়, তবে নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জাতির গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। ভোটাররা যদি নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, যদি তারা মনে করেন তাঁদের মতামত সম্মান পাচ্ছে, তবে গণতন্ত্র জীবন্ত থাকে। কিন্তু যদি রাজনৈতিক উত্তেজনা, প্রশাসনিক অনীহা এবং সহিংসতার আশঙ্কা ভোটারদের মনে দানা বাঁধে, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। এই হতাশা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। নির্বাচনের আগে ও পরে সহিংসতা, দমনমূলক আচরণ, বা দলীয় প্রভাবের অভিযোগ থাকলে জনগণের আস্থা নষ্ট হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার জন্য বিপজ্জনক।
এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং সব দলের অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ তৈরি করা—এই তিনটি দিকেই জোর দিতে হবে। পাশাপাশি নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত করতে হবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আস্থা পুনর্গঠনের কাজে। প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন অনলাইন পর্যবেক্ষণ বা ইভিএমের সঠিক প্রয়োগ, স্বচ্ছতা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে, তবে তার আগে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য ও জনগণের আস্থা অর্জন অপরিহার্য।
ভোটাররাই গণতন্ত্রের প্রাণ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তাঁদের মধ্যে যে আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা ও উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে, তা উদ্বেগজনক। তারা চায় একটি নিরাপদ ও নিরপেক্ষ পরিবেশ, যেখানে ভোট দিতে পারা একটি অধিকার নয়, বরং আনন্দের অভিজ্ঞতা। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সহিংসতার ঝুঁকি তাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করেছে। অনেকেই ভোট দিতে আগ্রহ হারাচ্ছেন, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করছে।
এ অবস্থায় ভোটারদেরও তাদের দায়িত্ব বুঝতে হবে। পক্ষপাতহীনভাবে ভোটদান, গুজব থেকে দূরে থাকা, এবং সহিংসতাকে প্রত্যাখ্যান করা প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। একইসাথে সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব হলো এমন পরিবেশ তৈরি করা যেখানে এই দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়। রাজনৈতিক দলগুলোকেও বুঝতে হবে যে, ক্ষমতা নয়, আস্থা সবচেয়ে বড় শক্তি।
বাংলাদেশ আজ এক সংবেদনশীল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে—একদিকে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা, অন্যদিকে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও সামাজিক বিভাজন। তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের উদ্বেগ তাই নিছক সতর্কবার্তা নয়, বরং রাষ্ট্রের জন্য এক আত্মসমালোচনার আহ্বান। আশাবাদ অবশ্যই দরকার, কারণ তা এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়; কিন্তু সেই আশাবাদকে বাস্তবতার আলোয় যাচাই না করলে তা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনায় পরিণত হয়। এখন প্রয়োজন এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান, যেখানে সরকার ও তথ্য উপদেষ্টারা, আশাবাদী ও সমালোচকরা, সবাই একসাথে সংকটের মোকাবিলায় অংশ নেবেন।
রাজনৈতিক সংলাপ, সামাজিক সম্প্রীতি ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার সমন্বয়েই বাংলাদেশ তার বর্তমান অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠতে পারে। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি, ভোটারদের আস্থা পুনর্গঠন, এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভাজনের বিরুদ্ধে সামাজিক ঐক্যই হবে উত্তরণের একমাত্র পথ। আজকের উদ্বেগ যদি আগামী দিনের প্রেরণায় রূপ নেয়, তবে সংকট নয়, আশাবাদই হবে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের মূলমন্ত্র।
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট।
এইচআর/এএসএম

 2 hours ago
4
2 hours ago
4






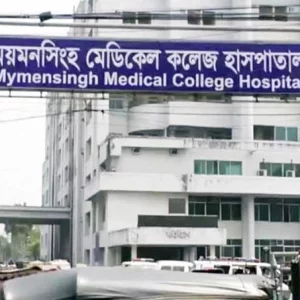


 English (US) ·
English (US) ·